 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
পাঁচুন্দির হাট ও বাংলার গ্রাম
সুদীপ ঘোষাল
রবিবাবু ও গরুর হাটের কথা
গ্রামের নাম পাঁচুন্দি । সামনে একটা গরুর হাট আছে। সেই গরুর হাট কে কেন্দ্র করে এখানে নানা রকমের ব্যবসা গজিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দোকান পাসারি আছে। হাট বসে প্রতি বুধবার। রবিবাবু এখানকার গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। তিনি খুব দয়ালু এবং ভদ্রলোক বলে পরিচিত।
পাঁচুন্দি কাউ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিরু শেখ জানান, গত বছর অনলাইনে ২৭ হাজার গরু বিক্রি হয়েছিল৷ এবার টার্গেট করা হয়েছে এক লাখের মতো৷ তবে পরিস্থিতি দেখে তারা মনে করছেন বিক্রি আরো বেশি হবে৷ করোনা এবং ব্যাপক প্রচারের কারণে অনলাইন হাটের প্রতি আগ্রহ এবার বাড়ছে ৷ অনলাইনে ছবি ও ভিডিও দেখেই গরু কিনতে হবে ৷ তবে খামার বা হাটের পাশে কারো বাড়ি হলে দেখার সুযোগ থাকবে ৷ আর তা না হলে গরুটি সরবরাহের সময়ই দেখা যাবে ৷ তবে অনলাইনে দেখা গরু আর বাস্তবের গরুর মিল না থাকলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গাইড লাইন অনুযায়ী সমাধান হবে ৷ এবার অনলাইনে গরু কিনে কোরবানির দায়িত্বও দেয়া যাবে ৷ অনলাইন হাট থেকে একদম কোরবানি করে বাড়িতে মাংস পৌঁছে দেওয়া হবে।করোনার মধ্যে নির্ধারিত সময়ের আগেই এবার গেরামসহ সারাদেশে কোরবানির গরুর হাট বসেছে ৷ হাটের জন্য রয়েছে কয়েকটি শর্ত ৷ প্রথম শর্ত দুমাসের আগে গরুর হাট বসানো যাবে না৷ কিন্তু হাটে গরু আনা শুরু হয়েছে ১০ দিন আগে৷শর্তে বলা হয়েছে, হাট বসার দু দিনের বেশি আগে গরু আনা যাবে না৷আবাসিক এলাকায় গরুর হাট বসানোতেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে৷ অথচ রেলওয়ে কলোনির আবাসিক এলাকার মাঠ গরুর হাটের জন্য ইজারা দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন নিজেই৷ সারাদেশে নানা জায়গাতেই যেখানেসেখানে বসছে হাট৷ ইজারা দেয়াও শেষ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে গ্রামে এই এলাকায় গরুর হাট বসে গেছে৷ ক্রেতারাও যাচ্ছেন কোরবানির জন্য গবাদি পশু কিনতে৷ এই করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই গরুর হাটের কথা বলছে পঞ্চায়েত৷ তবে পুরোপুরি হাট শুরু হলে বাস্তব অবস্থা আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে৷বিক্রেতা ও ক্রেতাদের জন্য যে অনেকগুলি শর্ত দেয়া হয়েছে তার বড় একটি অংশ করোনায় স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক সংক্রান্ত৷বলা হচ্ছে, গরুর হাটে পুরো স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে ৷ গরুগুলোকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ক্রেতারা নিজেদের মধ্যে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রেখে হাটে অবস্থান করতে পারেন৷ সেভাবেই হাটে গবাদি পশু তুলতে হবে৷ এর বেশি পশু রাখা যাবে না৷হাটে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাইকে মাস্ক পরতে হবে৷ আর গরু কিনতে দুই জনের বেশি হাটে যেতে পারবেন না৷ হাটের আয়তন অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব রেখে যত জন ক্রেতা এক সঙ্গে প্রবেশ করতে পারেন, ততজন প্রবেশ করবেন৷ বাকিরা বাইরে অপেক্ষা করে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করবেন৷হাটে প্রবেশের পথে শরীরের তাপমাত্রা মাপা ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকবে৷ হাটের ভিতরেও হাতধোয়ার ব্যবস্থা৷হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে প্রতিটি হাটে৷ এছাড়া হাটে আইসোলেশন সেন্টার ও মেডিকেল টিম থাকবে৷ তারা প্রয়োজন হলে কাউকে দ্রুত আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে যাবেন৷ থাকবে ভ্রাম্যমাণ আদালত, সিটি কর্পোরেশনের টিম এবং জাল টাকা চিহ্নিত করার বুথ৷ কোনো হাটে জোর করে গরু নেয়া যাবে না৷রবিবাবু সব্জিহাটে গিয়ে শিবপদকে বলেন,কি হে লেখকমশাই কেমন আছো? মুখে মাস্ক পর নাই কেন হে?বিজয় বলেন,পকেটে আছে।পুলিশ দেখলেই পরে নেব।আগে গরুদের মুখে মাস্কের মত জাল পরানো হত আর এখন দেখুন আমরাই গরু হয়ে বসে আছি।
রবিবাবু বললেন,তোমরা লেখক মানুষ। কল্পনাশক্তি বটে।ঠিক বলেছ কথাটা, একদম ঠিক।
বিজয় বলল,করোনার আগে আপনি আর আমি ঘুরে এলাম বেলুন থেকে।আর একবার যাবেন নাকি?
রবিবাবু বললেন,তোমাকে বলা হয় নি। গতকাল ঘুরে এলাম আবার।তুমি তো জানো, আমি দূর দূরান্তে না গিয়ে কাছাকাছি না দেখা গ্রাম দেখতে ভালোবাসি।এবার গেলাম পাশের ইকো ভিলেজ পরিদর্শনে।হাওড়া আজিমগঞ্জ লোকাল ধরে শিবলুন হল্টে নামলাম। সেখান থেকে অম্বলগ্রাম পাশে রেখে দু কিলোমিটার টোটো রিক্সায় গেলে গ্রামটি পাবে। একদম অজ পাড়াগাঁ। মাটির রাস্তা ধরে বাবলার বন পেরিয়ে তন্ময়বাবুর স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করলাম।তন্ময়বাবু ঘুরিয়ে দেখালেন। তার জগৎ।প্রায় একশো প্রজাতির গাছ।পশু,প্রাণীদের উন্মুক্ত অঞ্চল।বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে, সেখানে।তার নিজের হাতে বানানো মা কালীর মূর্তি দেখলাম। কাঁচের ঘরে ইকো সিষ্টেমের জগৎ।কেউটে সাপ, ব্যাঙ থেকে শুরু করে নানারকমের পতঙ্গ যা একটা গ্রামের জমিতে থাকে। বিরাট এক ক্যামেরায় ছবি তুলছেন তন্ময় হয়ে।আমি ঘুরে দেখলাম প্রায় দু কোটি টাকা খরচ করে বানানো রিসর্ট।ওপেন টয়লেট কাম বাথরুম।পাশেই ঈশানী নদী।এই নদীপথে একান্ন সতীপীঠের অন্যতম সতীপীঠ অট্টহাসে যাওয়া যায় নৌকায়। তন্ময়বাবু হাতে সাপ ধরে দেখালেন। শিয়াল,বেজি,সাপ,ভ্যাম আছে। তাছাড়া পাখির প্রজাতি শ খানেক।একটা পুকুর আছে। তার তলায় তৈরি হচ্ছে গ্রন্হাগার।শীতকালে বহু বিদেশী পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। তন্ময়বাবু বললেন,স্নেক বাইটের কথা ভেবে সমস্ত ব্যবস্থা এখানে করা আছে। ঔষধপত্র সবসময় মজুত থাকে।তারপর গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। এখানকার চাষিরা সার,কীটনাশক ব্যবহার করেন না। তারপর বিকেলে নৌকাপথে চলে গেলাম অট্টহাস সতীপীঠ।এখানে মা মহামায়ার ওষ্ঠ পতিত হয়েছিলো। সোনা মহারাজ এই সতীপীঠের প্রধান। তারপর দেখলাম পঞ্চমুন্ডির আসন।ঘন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মন্দিরে মা কালীর মূর্তি। রাতে ওখানেই থাকলাম।রবিবাবু বলেন,তার পরের দিন সকালে হাঁটাপথে চলে এলাম কেতুগ্রাম বাহুলক্ষীতলা। কথিত আছে এখানে মায়ের বাহু পতিত হয়েছিলো। এটিও একান্ন সতীপীঠের এক পীঠ।তীর্থস্থান। সুন্দর মানুষের সুন্দর ব্যবহারে মন ভালো হয়ে যায়।এর পাশেই আছে মরাঘাট। সেখান থেকে বাসে চেপে চলে এলাম উদ্ধারণপুর।এখানে লেখক অবধূতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।গঙ্গার ঘাটে তৈরি হয়েছে গেট,বাথরুম সমস্তকিছু।শ্মশানে পুড়ছে মৃতদেহ।উদ্ধারণপুর থেকে নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে চলে এলাম কাটোয়া। এখানে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেবার পরে মাথা মুন্ডন করেছিলেন। মাধাইতলা গেলাম। বহুবছর ব্যাপি এখানে দিনরাত হরিনাম সংকীর্তন হয় বিরামহীনভাবে। বহু মন্দির,মসজিদ বেষ্টিত কাটোয়া শহর ভালো লাগলো।বিজয় বলল,এবার গেলে আমাকে বলবেন।এখন আসি।
রবিবাবু বললেন,চলো আমিও যাই।স্কুলে যেতে হনে মিড ডে মিল আর সাইকেল দিতে।
আবার পরের সপ্তাহে রবিবাবু ও বিজয় মুখোমুখি হলেন।
রবিবাবুর গ্রামের পুজো আর কদিন পরেই।তাই সকলের মন খুশিতে ভরপুর।লেখক বিজয় বলে এই পুজোর ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন আমাকে।রবিবাবু বলেন,নিশ্চয়ই। তবে তো তুমি লিখতে পারবে।
রবিবাবু বললেন,নদীর ধারে আমাদের গ্রাম।তাই এখানে কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমিরদেবতা কালু রায়ের পুজো করা হয়। তাঁর পোশাক পৌরাণিক যুদ্ধ-দেবতার মতো।আরণ্যক দেবতার প্রাচীন পুজোপদ্ধতি মেনে কালু রায়ের পুজোয় বনঝাউ ফুলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়।ধর্মঠাকুর কেবলমাত্র রাঢের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বান্দরা গ্রামের ধর্মঠাকুর, কালু রায় নামে পরিচিত। বন্ধুর সুবাদেই ঐ গ্রামের ধর্মরাজের পুজো দেখার সুযোগ হয়েছিল। বাহন-সাদা ঘোড়া। জনসাধারণের পূজার পর দুটি পালকিতে সারা গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামে ঘোরানো হয়। কিন্তু কূর্ম মূর্তি যেহেতু গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না, তাই প্রতীকি কালাচাঁদকে পালকি করে অন্যান্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ম হল, যেখানে যেখানে কালাচাঁদের পালকি বাহকরা গ্রামের বাইরে পালকি নামান, সেখানে সেই পালকিকে আটকানো হয়। সেই সব গ্রামের লোকেরা নানারকম প্রশ্ন করেন। এ যেন সেই আদিকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকানো। তখন যুদ্ধ হত, যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারলে ঘোড়া মুক্তি পেত। এখানে হয় প্রশ্নোত্তরের খেলা। যারা দেবতার পালকিকে আটকে দেন তারা প্রশ্ন করেন। আর সন্ন্যাসীরা, যারা সঙ্গে থাকেন তাদের এর উত্তর দিতে হয়। গ্রাম্য জীবনের এও এক আনন্দের উৎস। প্রথাগতভাবে সেগুলি যে খুব উচ্চমানের , তা হয়ত নয়। কিন্তু মন্দ লাগে না। গ্রাম্য জীবন, পুরাণ, ইতিহাস , মহাকাব্য অনেক কিছু মিশে আছে এগুলির সঙ্গে। ধর্মরাজের পূজার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গ্রামের মানুষের গীত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে।স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, দক্ষিণরায়ের রাজত্বের সীমা দক্ষিণে কাকদ্বীপ, উত্তরে ভাগীরথী নদী, পশ্চিমে ঘাটাল ও পূর্বে বাকলা জেলা। প্রত্যেক অমাবস্যায় দক্ষিণরায় মন্দিরে পশুবলি হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে দক্ষিণরায় গানবাজনা পছন্দ করেন। তাই স্থানীয় লোকেরা রাতে তার মন্দিরে নাচগানের আসর বসান। দক্ষিণ রায়ের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে গায়েনরা পালাক্রমে কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত রায়মঙ্গল পরিবেশন করে এবং বাউল্যা, মউল্যা, মলঙ্গি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষেরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এ গান ভক্তিভরে শ্রবণ করেন। সুন্দরবনের অধিবাসীরা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে মাছধরা, কাষ্ঠ বা মধু আহরণের মতো কোনো কাজে যাওয়ার আগে দক্ষিণরায়ের মন্দিরে পূজা দেন। কেউ কেউ মাথার পিছন দিকে দক্ষিণরায়ের মুখোশ পরে জঙ্গলে ঢোকেন যাতে বাঘ সেই মুখোশ দেখে ভয় পেয়ে তার কাছে না আসে।কলকাতার গড়িয়া রেলস্টেশনের কাছে লক্ষ্মীকান্তপুর ও ধপধপির কয়েক মেইল দূরে একটি দক্ষিণরায় মন্দির আছে। এই অঞ্চলটি এক সময়ে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এখনও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দক্ষিণরায় মন্দিরে পূজা দেন। দক্ষিণরায়ের মূর্তিতে একটি বিরাট গোঁফ দেখা যায়। তার শরীর শীর্ণ, চকচকে এবং হলদেটে। গায়ে বাঘের মতো ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। মুখের দুদিক থেকেই লালা ঝরে। তার একটি ছয় মিটার দীর্ঘ লেজও আছে।বারা ঠাকুর হলেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের বাঙালি হিন্দুসমাজে পূজিত এক অশাস্ত্রীয় লৌকিক দেবতা। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলার গ্রামাঞ্চলে এই দেবতার পূজা প্রচলিত; তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এই বারাঠাকুরের পূজার প্রচলন অত্যধিক। 'বারা' শব্দের লোকায়ত অর্থ বাধা দেওয়া বা নিবারণ করা। মূলত ব্যাঘ্র-ভীতি নিবারণ ও সাংসারিক মঙ্গলকামনায় এই দেবতার পূজা করা হয়। ১লা মাঘ বা তার কাছাকাছি সময়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।তাঁর সাথে (বিশেষত মাথার চালির অবয়বে) মিশরের ফারাওদের আঁকা ছবিগুলির (যাদের মাথা অনেক লম্বা — বিশাল দেহ — রাজা বা দেবতা) মিল আছে বলে ধারণা করা হয়।উল্টানো ঘট ও মাথায় লতা-পাতা আঁকা চ্যাপ্টা মুকুট — এটিই বারা ঠাকুরের মূর্তি। ঘটের উপর নানা রঙে আঁকা চোখ, মুখ, গোঁফ অঙ্কিত ধাকে। এই মূর্তিযুগলের গোঁফওয়ালা পুরুষমূর্তিটিকে দক্ষিণরায়-এর কাটা মুণ্ডু বলে মনে করা হয়, অপরটি তার মা নারায়ণী বা কালু রায়।খোলা মাঠে গাছতলায় গাছের গুঁড়ি বা শাখায় মূর্তি স্থাপন করে এঁর পূজা করা হয়। পূজায় বর্ণ ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন; মূর্তির বিসর্জন হয় না। যে গাছে বারা ঠাকুর রাখা হয় তার সবচেয়ে উঁচু শাখায় একটি লালনিশান টাঙিয়ে দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় হিন্দু নিয়ম বহির্ভূতভাবে আগুনে পুড়িয়ে 'বারা' তৈরী হয় এবং পূজার পর সারাবছর খোলা আকাশের নিচে রেখে দেওয়া হয়।বারাঠাকুর পূজায় আদিমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে অশাস্ত্রীয় হলেও ব্রাহ্মণ-শাসিত বর্ণহিন্দু সমাজ এঁকে স্বীকার করে নিয়েছেন।
বিজয় বলে,আমি শুনেছি দাদুর কাছে, নিম্নবর্গ পরিবারের মানুষগুলি দেবতার পূজা,পৌরহিত্য ইত্যাদি থেকে দূরে ছিল বহুদিন, বহুযুগ ধরে। ব্রাহ্মণ্য সংষ্কৃতির চাপে সমাজে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব একরকম ঢাকা ছিল। যখন তারা সেই আস্তরণ সরিয়ে সেই অধিকার আবার ফিরে পেতে শুরু করল, ব্রাহ্মণ্য পূজার রীতিগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করার চেষ্টা করল। কিংবা বলা ভালো, এই রীতিগুলির প্রতি তাদেরও লোভ জন্মাল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অশিক্ষা, ভাষাজ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নানাকারণে তা রপ্ত করতে পারল না। ফলও হল মারাত্মক! এগুলি শুনতে, পড়তে আনন্দদায়ক মনে হলেও অজস্র ভুলভ্রান্তিতে ভরা, অনুকরণের অক্ষম প্রচেষ্টা। ভাষা এবং উচ্চারণ দুয়েরই ভুল। মাঝে মাঝেই মন্ত্র ভুলেগিয়ে দৈনন্দিন যাপনের কথা কখনও বা স্বগতোক্তির মত মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও জনগনকে বোঝানোর জন্য কথ্যভাষার ব্যবহারও করতে হয়েছে পূজার ক্রম ও রীতিগুলি বোঝানোর জন্য। এর পরিণাম হল এই মন্ত্রগুলি।আর একটি কথা মাঝে মাঝে মনে হয় সেটি হল– এই অন্ত্যজ, নিম্নবর্গ মানুষগুলি যার মধ্যে মিশে আছে কিছু জনগোষ্ঠী সমাজের মানুষও যাদের আমরা বলি আদিম অধিবাসী, হয়তো এই পূজাগুলি একদিন ছিল তাদেরই অধিকারে। বহুযুগ পরে তাদের ফিরে পেয়ে আর মনে করতে পারেন না সেই মন্ত্রগুলিকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভুলে থাকা সেই অতীতকে মনে করতে পারে না। কারণ ঘটে গেছে অনেক সংযুক্তি, অনেক বিযুক্তি।
রবিবাবু বলেন,যাইহোক এইসব বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে আছে বাঙালির নিজস্ব কৃষ্টির প্রাণ।
বিজয়েরর লেখক হওয়ার গল্প ও তার আত্মসমালোচনা
আজ কালুরায়ের পুজো কিন্তু বিজয় কোলাহল ছাড়িয়ে সবুজ মাঠে গিয়ে বসে আছে।বাড়ির সকলে পুজোয় ব্যাস্ত।তারা জানে বিজয় অন্য ধরণের ছেলে।পড়াশোনা আর লেখা নিয়েই সে মত্ত।
বিজয় খোলা মাঠে থাকতে ভালোবাসে সবুজের সঙ্গ ভালোবাসে। সে গাছের সঙ্গে কথা বলে। নদীর পাড়ে এসে বসে নদীর সঙ্গে সে আপন মনেই গান করে আর খাতা-কলম নিয়ে লেখে।
স্কুলে যাওয়ার সময় মায়ের কাছে ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। স্কুলে গিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করে। কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে তার ভালো লাগে না।
তবু কষ্ট করে থাকে। স্কুলে সময় কাটিয়ে আবার মাঠে মাঠে হেঁটে বাড়ি ফেরে তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। এইভাবে ছোট থেকে বড় হয় সীমাবদ্ধ হয়ে। ধীরে ধীরে সে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের সেখানেও সেই অন্যমনস্ক ভাবে, আপন মনে সে নিজের খেয়ালে থাকে। একটা ম্যাগাজিন পরিচালনা করে এবং কিছু লিখতেও ভালোবাসে। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর চাকরির পড়া না পড়ে সে উপন্যাস গল্পের বই পড়ে। গল্পের বই পড়ে পড়ে চাকরির কথা ভুলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি বয়সটা চলে যায়। সে কিন্তু আর চাকরি ও পায়না। শিবপদর সব বন্ধুরা খুব চালাক। তারা নিজেরা পড়াশোনা করে চাকরি যোগাড় করে নেয়। কিন্তু শিবপদ সারা জীবন বেকার হয়ে রয়ে যায় , সংসারের মাঝে।তার কোন কদর নেই, তার কোন ভালোবাসা নেই তার কোনো বন্ধু নেই। এভাবেই ধীরে ধীরে সে একা হয়ে যায়। আর একা হতে সে, খাতা পেন নিয়ে বসে। খাতা-কলম নিয়ে বসার পর ধীরে ধীরে মনের কথা লিখতে শুরু করে। কয়েকবছর পরে তার পরিচয় হয় লেখক হিসাবে।সে ভাবে,চারুকলার ক্ষেত্রে, লেখক শব্দটি অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয়, যেমন গীতি লেখক, তবে শুধু লেখক বললে সাধারণত, যিনি লিখিত ভাষা তৈরি করেন, তাঁকে বোঝায়। কিছু লেখক মৌখিক প্রথা থেকে কাজ করেন।
স্কুলে শিক্ষকদের কাছে শুনেছে বিজয়,লেখকরা কাল্পনিক বা বাস্তব বেশ কয়েকটি রীতির উপাদান তৈরি করতে পারেন। অনেক লেখক তাঁদের ধারণাকে সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করেন – উদাহরণস্বরূপ, গ্রাফিক্স বা চিত্রণ। নাগরিক এবং সরকারী পাঠকদের দ্বারা, অ-কাল্পনিক প্রযুক্তিবিদদের কাজের জন্য, সাম্প্রতিক আরেকটি চাহিদা তৈরি হয়েছে, যাদের দক্ষতা ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির বোধগম্য, ব্যাখ্যামূলক দস্তাবেজ তৈরি করে। কিছু লেখক তাঁদের লেখাকে আরও বোধগম্য করার জন্য চিত্র মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে পারেন। বিরল দৃষ্টান্তে, সৃজনশীল লেখকগণ তাঁদের ধারণাগুলি সংগীতের পাশাপাশি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। লেখকের স্ত্রীবাচক শব্দ হচ্ছে লেখিকা। লেখককে অনেকক্ষেত্রে গ্রন্থকারের সমার্থক শব্দরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু লেখক শব্দটি মূলতঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁদের নিজস্ব রচনাগুলি সৃষ্টির পাশাপাশি, লেখকরা প্রায়শই 'কীভাবে' তাঁরা লেখেন সেটাও প্রকাশ করেন (অর্থাৎ, যে প্রক্রিয়াটি তাঁরা লেখার জন্য ব্যবহার করেন) কেন তাঁরা লেখেন (অর্থাৎ তাদের প্রেরণা কি)এবং অন্যান্য লেখকের কাজের বিষয়েও মন্তব্য (সমালোচনা) করেন।
বিজয় প্রশ্ন করেছিল,লেখকরা পেশাদার বা অপেশাদারভাবে কাজ করেন, অর্থাৎ, অর্থের জন্য বা অর্থ ছাড়াই, এছাড়াও অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে, বা কেবল তাঁদের কাজ প্রকাশিত হবার পরে। অর্থ প্রাপ্তি লেখকদের অনেক অনুপ্রেরণার মধ্যে একটি, অনেকে তাঁদের কাজের জন্য কখনও কোন অর্থই পান না।
স্যার বলেছিলেন,সংবিধান রচয়িতা আমাদের প্রণম্য।তিনিও কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই সংবিধান রচনা করেছেন।শুধু অর্থই সব নয়।লেখক শব্দটি প্রায়শই সৃষ্টি মূলক লেখক এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যদিও পরবর্তী শব্দটির কিছুটা বিস্তৃত অর্থ রয়েছে এবং লেখার কোনও অংশের জন্য আইনি দায়িত্ব জানাতে ব্যবহৃত হয়।
বিজয়ের গণিতের শিক্ষকমশাই বলতেন, যোগ,বিয়োগ,গুণ,ভাগ জীবনের ক্ষেত্রেও মেনে চলবি। যত দুঃখ,ব্যথা বিয়োগ করবি। আনন্দ যোগ করে খুশি গুণ করবি। আর খাবার ভাগ করে খাবি। একা খেলে,বেশি খেলে রোগ বেড়ে যাবে। মজার মধ্যেও কতবড় শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছিলেন আজ বুঝতে পারি। আদর্শ শিক্ষক বোধহয় এই রকম হন। ফোচন বললো।ফোচনের বোন ফোড়োনকে মাস্টারমশাই মশলা বলে ডাকতেন। ফোড়োন খুব রেগে যেতো। কারণ বন্ধুরাও তাকে মশলা বলেই ডাকতো। একদিন স্যারের কাছে ফোড়ন বললো,আপনি মশলা নামে ডাকেন বলে সবাই ডাকে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন,আদর করে দেওয়া নাম কোনোদিন ফেলবি না। রাগ করবি না। দেখবি একদিন যখন তোর বন্ধু, বান্ধবীরা দূরে চলে যাবে তখন এই নাম তোর মুখে হাসি ফোটাবে। সংসারের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেবে আদরের পরশে। ফোড়োনের জীবনে সত্য হয়েছিলো এই কথা। একদিন বিয়ের পরে রমেশের সঙ্গে দেখা হলো তার। রমেশ বললো,কেমন আছিস ফোড়োন। ফোড়োন বললো,একবার মশলা বলে ডাক। তা না হলে আমি তোর প্রশ্নের উত্তর দেবো না। রমেশ তারপর ওকে মশলা বলে ডেকেছিলো। মশলা সেবার খুশি হয়ে রমেশকে ফুচকা খাইয়েছিলো। গ্রামে থাকতেই প্রাইমারী স্কুলে যেতাম। মাষ্টারমশাই আমাদের পড়াতেন। পরের দিন আমরা দুই ভাই স্কুলে ভরতি হতে গেলাম। বড়দা গ্রামে কাকার কাছে আর ছোটো ভাই বাবু একদম ছোটো। স্কুলে মীরা দিদিমণি সহজ পাঠের প্রথম পাতা খুলে বললেন,এটা কি? আমি বললাম অ য়ে, অজগর আসছে ধেয়ে।
আবার বই বন্ধ করলেন। তারপর আবার ওই পাতাটা খুলে বললেন,এটা কি?
আমি ভাবলাম,আমি তো বললাম এখনি। চুপ করে আছি। ঘাবড়ে গেছি। দিদি বাবাকে বললেন,এবছর ওকে ভরতি করা যাবে না।
বিজয় ভাবে ছোটবেলার স্মৃতির কথা।ছোড়দা ভরতি হয়ে গেলো। তারপর বাসা বাড়িতে জীবন যাপন। সুবিধা অসুবিধার মাঝে বড়ো হতে লাগলাম। আমাদের খেলার সঙ্গি ছিলো অনেক। ধীরে ধীরে আমরা বড়ো হয়ে টি,আর,জি,আর,খেমকা হাই স্কুলে ভরতি হলাম। তখন লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করার রাস্তা ছিলো না। লাইনের কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতাম। কতজন ট্রেনে কাটা পরে যেতো তার হিসাব নেই। তারপর ওয়াগন ব্রেকাররা মালগাড়ি এলেই চুরি করতো রেলের সম্পত্তি। কঠিন পরিস্থিতি সামলে চলতো আমাদের লেখাপড়া।এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। পাশে রাস্তা আছে। ওয়াগান ব্রেকারদের অত্যাচার নেই।মনে আছে ক্লাস সেভেন অবধি লিলুয়ায় পড়েছি। তারপর গ্রামে কাকাবাবু মরে গেলেন অল্প বয়সে। বাবা অবসর নিলেন চাকরী থেকে। বড়দা ও ছোড়দা রয়ে গেলো লিলুয়ায়। বাবা, মা ও আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে এলেন বড় পুরুলিয়া গ্রামে।গ্রামে কাকীমা ও দুই বোন। রত্না ও স্বপ্না। আমরা চারজন। মোট সাতজন সদস্য। শুরু হলো গ্রামের জীবন।আবার বিল্বেশ্বর হাই স্কুলে ভরতি হতে গেলাম বাবার সঙ্গে। ভরতি র পরীক্ষা হলো। হেড মাষ্টারমশাই বললেন,বাঃ, ভালো পত্রলিখন করেছে। বিজয়া প্রণামের আগে চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে। কজনে জানে।আমি প্রণাম করলাম স্যারকে। ভরতি হয়ে গেলাম।
বিজয় ভাবে অতীতের কথা।স্কুলে আজ বাংলার স্যার দুটো ক্লাস একসঙ্গে নিলেন। কবি বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমার বড়াল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।স্যার সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন তিনি বললেন,কবি বিহারীলাল বাংলা ভাষার কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি হিসেবে তিনি সুপরিচিত। কবিগুরু তাকে বাঙলা গীতি কাব্য-ধারার 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেন। তার সব কাব্যই বিশুদ্ধ গীতিকাব্য। মনোবীণার নিভৃত ঝংকারে তার কাব্যের সৃষ্টি। বাঙালি কবি মানসের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। স্যার বলেন,অতি অল্পকালের ভিতরে তিনি বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিবিড় অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে গীতিকবিতার ধারা চালু করেন। এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিহারীলাল তার কবিতায় ভাবের আধিক্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতি ও প্রেম, সংগীতের উপস্থিতি, সহজ-সরল ভাষা বিহারীলালের কবিতাকে দিয়েছে আলাদাধারার বৈশিষ্ট্য।বিহারীলাল চক্রবর্তী ২১ মে, ১৮৩৫ তারিখে কলকাতার নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। মাত্র চার বছর বয়সে মাতা মারা যান।বিহারীলাল চক্রবর্তী শৈশবে নিজ গৃহে সংস্কৃত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তিন বছর অধ্যয়ন করেন।বিহারীলাল চক্রবর্তী উনিশ বছর বয়সে অভয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্পকাল পরে অভয়া দেবী মারা গেলে কাদম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।তার রচনাবলীর মধ্যে স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), মায়াদেবী, ধুমকেতু, দেবরাণী, বাউলবিংশতি, সাধের আসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ণিমা, সাহিত্য সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু ইত্যাদি তার সম্পাদিত পত্রিকা। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।সারদামঙ্গল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। আখ্যানকাব্য হলেও এর আখ্যানবস্তু সামান্যই। মূলত গীতিকবিতাধর্মী কাব্য এটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, “সূর্যাস্ত কালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয়। কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না। অথচ সুদূর সৌন্দর্য স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ণ পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।”[৫] সমালোচক স্যার বলেন,শিশিরকুমার দাশের মতে, “মহাকাব্যের পরাক্রমধারার পাশে সারদামঙ্গল গীতিকাব্যের আবির্ভাব এবং শেষপর্যন্ত গীতিকাব্যের কাছে মহাকাব্যের পরাজয়ের ইতিহাসে সারদামঙ্গল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কাব্য। বিহারীলালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি নয়, কিন্তু নিজ উদ্যোগে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর পূর্বে বাংলা গীতিকবিতার ধারা প্রচলিত থাকলেও এর যথার্থ রূপায়ণ ঘটে তাঁর হাতেই। তিনি বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারার রদবদল ঘটিয়ে নিবিড় অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব থাকলেও নিজস্ব রীতিই ফুটে উঠেছে। বিহারীলাল বস্ত্ততন্ময়তার পরিবর্তে বাংলা কাব্যে আত্মতন্ময়তা প্রবর্তন করেন। বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম কবির অন্তর্জগতের সুর ধ্বনিত করে তোলেন। তাঁর কবিতায় রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বেশি। প্রকৃতি ও রোম্যান্টিকতা, সঙ্গীতের উপস্থিতি, সহজ-সরল ভাষা এবং তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যুগপৎ ব্যবহার বিহারীলালের কাব্যকে করেছে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাঁর কবিতার বিষয়-ভাবনা, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য প্রকাশের চমৎকারিত্ব, ছন্দ-অলঙ্কারের অভূতপূর্ব ব্যবহার অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পঁয়ত্রিশ বছরের কবিজীবনে বিহারীলাল অনেক গীতিকাব্য ও রূপককাব্য রচনা করেছেন।বিহারীলালের রচনাবলির মধ্যে স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীতশতক (১৮৬২) বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), নিসর্গসঙ্গীত (১৮৮১), মায়াদেবী (১৮৮২), দেবরাণী (১৮৮২), বাউলবিংশতি (১৮৮৭), সাধের আসন (১৮৮৮-৮৯) এবং ধূমকেতু (১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য। নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে বিহারীলাল বঙ্গপ্রকৃতির শোভা অপূর্ব ভাব-ভাষা ও ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কয়েকটি নারী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি গৃহচারিণী বঙ্গনারীকে সুন্দরের প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন। সারদামঙ্গল কাব্য বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি স্তম্ভস্বরূপ। এর মাধ্যমেই তিনি উনিশ শতকের গীতিকবিদের গুরুস্থানীয় হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যটি পড়ে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং বিহারীলালকে আখ্যায়িত করেছেন ‘ভোরের পাখি’ বলে।বিহারীলাল কাব্যচর্চার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা: পূর্ণিমা, সাহিত্য-সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু প্রভৃতি। এসব পত্রিকায় অন্যদের রচনার পাশাপাশি তাঁর নিজের রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ভারতী, সোমপ্রকাশ, কল্পনা প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিহারীলাল ১৮৯৪ সালের ২৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।
বিজয় ভাবে,সংসারে সং সেজে দিবারাতি নিজেকে ঠকিয়ে কোন ঠিকানায় ঠাঁই হবে আমার ।নিজেকে নিজের প্রশ্ন কুরে কুরে কবর দেয় আমার অন্তরের গোপন স্বপ্ন । জানি রাত শেষ হলেই ভোরের পাখিদের আনাগোনা আরম্ভ হয় খোলা আকাশে । আমার টোনা মাসিকে টোন কেটে অনেকে অভিশাপ দিতো । আমি দেখেছি ধৈর্য্য কাকে বলে । আজ কালের কাঠগোড়ায় তিনি রাজলক্ষ্মী প্রমাণিত হয়েছেন । কালের বিচারক কোনোদিন ঘুষ খান না । তাই তাঁর বিচারের আশায় দিন গোনে শিশুর শব, সব অবিচার ,অনাচার কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবে আগামী পৃথিবীর ভাবি শিশু প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি। অপেক্ষায় প্রহর গোনে নিজের অন্তরের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে । সাবধান খুনীর দল ,একবার হলেও অন্তত নিজের সন্তানের জন্য শান্ত পৃথিবী রেখে যা । ঋতু পরিবর্তন কিন্তু তোর হত্যালীলায় বন্ধ হবে না নির্বোধ ।শান্ত হোক হত্যার শাণিত তরবারি ।নেমে আসুক শান্তির অবিরল ধারা। রক্ত রঙের রাত শেষে আলো রঙের নতুন পৃথিবী আগামী অঙ্কুরের অপেক্ষায়। শিউলি শরতের ঘ্রাণে শিহরিত শরীর। শিউলি নামের শিউলি কুড়োনো মেয়েটি আমার শৈশব ফিরিয়ে দেয়।মনে পড়ে পিসির বাড়ির শিউলি গাছটার তলায় অপেক্ষা করতো ঝরা ফুলের দল। সে জানত ফুল ঝরে গেলেও
বিজয় ভাবে,তার কদর হয় ভাবি প্রজন্মের হাতে । সে আমাদের ফুল জীবনের পাঠ শেখায়। মানুষও একদিন ফুলের মত ঝরে যায়। । শুধু সুন্দর হৃদয় ফুলের কদর হয়। বিদেশে ষাট বছরেও মানুষ স্বপ্ন দেখে। নিজেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরখ করার সুযোগ মেলে। কিন্তু আমাদের কয়েকজন বন্ধু লোক ব্যাঙ্গের সুরে বলে, বুড়ো ঢ্যামনার ভিমরতি হয়েচে। সখ দেখো এখনও রঙীন জামা পড়ে। ব্যায়াম করে। মেয়েদের সঙ্গে কতা বলে।একটু হাসি ঠাট্টা করলে বলবে, মিনসে, ঘাটের মরা এখনও দুধ তোলা রোগ গেলো না।সব স্বপ্ন দেখা বন্ধ রেখে বুড়ো সেজে থাকলেই সম্মান পাওয়া যায় বেশি। নিজের মনে গুমরেওঠে যত স্মৃতি। শেয়ার করার কেউ নেই। তারপর মরে যাওয়ার পড়ে অন্তিম কাজ, নির্লজ্জ ভুরিভোজ। তবু সব কিছুর মাঝেই ঋতুজুড়ে আনন্দের পসরা সাজাতে ভোলে না প্রকৃতি। সংসারের মাঝেও সাধু লোকের অভাব নেই। তারা মানুষকে ভালোবাসেন বলেই জগৎ সুন্দর আকাশ মোহময়ী, বলেন আমার মা। সব কিছুর মাঝেও সকলের আনন্দে সকলের মন মেতে ওঠে। সকলকে নিয়ে একসাথে জীবন কাটানোর মহান আদর্শে আমার দেশই আদর্শ।
বিজয় আত্নসমালোচনা করে। সে নিজেকে ভাঙে, গড়ে আবার স্মৃতির বুকে ঝাপিয়ে পড়ে বারবারে।সে আর পাঁচজনের মত নয়। সে ভাবে, সত্য শিব সুন্দরের আলো আমার দেশ থেকেই সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করুক। আমার দুই বোন। তিন ভাইঝি। বোনেদের নাম রত্না স্বপ্না। রত্না হলো কন্যারত্ন। সব অভাব অভিযোগ তার কাছে এসে থমকে পড়ে অনায়াসে। আর অপরের উপকার করতে স্বপ্নার তুলনা মেলা ভার। ভাইঝিরা তানুশ্রী, দেবশ্রী,জয়শ্রী। এরা বড়দার মেয়ে আর মেজদার মেয়ে পৃথা,ছেলে ইন্দ্র। এরা সকলেই আমার খুব প্রিয়। বাবুর মেয়ে তিন্নি আমার ছেলে সৈকত। রূপসী বাংলার রূপে ছুটে যাই। কিন্তু আমার চেনা পৃথিবীর সবটা হয়ে যায় অচেনা বলয়,মাকড়সার জালের মতো জটিল । সবাই এত অচেনা অজানা রহস্য ময় ।বুকটা ধকধক করছে,হয়তো মরে যাবো, যাবো সুন্দরের কাছে,চিন্তার সুতো ছিঁড়ে কবির ফোন এলো । এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে, অভয়বাণী মিলেমিশে সৃষ্টি করলো আশা ।আর আমি একা নই,কবির ছায়া তাঁর মায়া আমাকে পথ দেখায়...আমার মায়ের বাবার নাম ছিলো মন্মথ রায়। মনমতো পছন্দের দাদু আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন। যখন মামার বাড়ি যেতাম মায়ের সঙ্গে তখন দাদু আমাদের দেখেই মামিমাকে মাছ,ডিম,মাংস রান্না করতে বলতেন। কখনও সখনও দেখেছি মামিমা নিজে ডেঙা পাড়া,সাঁওতাল পাড়া থেকে হাঁসের ডিম জোগাড় করে নিয়ে আসতেন। তখন এখনকার মতো ব্রয়লার মুরগি ছিলো না। দেশি মুরগির বদলে চাল,ডাল,মুড়ি নিয়ে যেতো মুরগির মালিক। নগদ টাকর টানাটানি ছিলো। চাষের জমি থেকে চাল,ডাল,গুড় পাওয়া যেতো। মুড়ি নিজেই ভেজে নিতেন মামিমা। আবার কি চাই। সামনেই শালগোরে। সেখানে দাদু নিজেই জাল ফেলে তুলে ফেলতেন বড়ো বড়ো রুই, কাতলা,মৃগেল। তারপর বিরাট গোয়ালে কুড়িটি গাইগরু। গল্প মনে হচ্ছে। মোটেও না। এখনও আমার সঙ্গে গেলে প্রমাণ হিসাবে পুকুর,গোয়াল সব দেখাতে পারি। আহমদপুর স্টেশনে নেমে জুঁইতা গ্রাম। লাল মাটি। উঁচু উঁচু ঢিবি। আমি পূর্ব বর্ধমানের ছেলে। সমতলের বাসিন্দা। আর বীরভূমে লাল উঁচু নিচু ঢিবি দেখে ভালো লাগতো।আমাদের মাটি লাল নয়। কি বৈচিত্র্য। ভূগোল জানতাম না। জানতাম শুধু মামার বাড়ি। মজার সারি। দুপুর বেলা ঘুম বাদ দিয় শুধু খেলা। আর ওই সময়ে দাদু শুয়ে থাকতেন। ডিসটার্ব হতো।একদিন ভয় দেখানোর জন্যে বাড়ির মুনিষকে মজার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ছেলেধরার গুজব উঠেছিলো। আমরা দুপুরে খেলছি। দাদু বার বার বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,আজ কিন্তু ছেলেধরা আসতে পারে। আমি খুব ভিতু ছিলাম। আমার মামার ছেলে বাঁটুলদা,হোবলো,ক্যাবলা,লেবু। সবাইকে বললাম। তখন বারো থেকে পনেরো বছরের পালোয়ান আমরা। সকলের ভয় হলো। দাদু কোনোদিন মিথ্যা বলেন না। কথার মধ্যে কনফিডেন্স না থাকলে তিনি রাগ করতেন। একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,এই অঙ্কটা পারবি। পড়ে দেখ। আমি বললাম,বোধহয় পারবো। তিনি রেগে বললেন, বোধহয় কি? হয় বল না, কিংবা হ্যাঁ। নো অর ইয়েস। ধমকের চোটে কেঁদে ফেলেছিলাম। এই সেই দাদু বলেছেন, আজ ছেলেধরা আসবে। সাবধান। সবাই ঘুমোবি। দুপুরের রোদে বেরোবি না। বাধ্য হয়ে শুলাম। দাদুর নাক ডাকা শুরু হলেই সবাই দে ছুট। একেবারে বাদাম তলায়। চিনে বাদামের একটা গাছ ছিলো। ঢিল মেরে পারছি। এমন সময়ে মুখ বেঁধে ছেলেধরা হাজির। হাতে বস্তা। বস্তা ছুড়ে ঢাকা দিতে চাইছে আমাদের । আমরা সকলেই প্রাণপণে বক্রেশ্বর নদীর ধারে ধারে গিয়ে মাঝিপাড়ায় গিয়ে বলতেই বিষ মাখানো তীর আর ধনুক কাঁধে বেড়িয়ে পড়লো। বীর মুর্মু। সাঁওতাল বন্ধু। ছেলেধরা তখন পগাড় পাড়। আর দেখা নেই। বড়ো হয়ে সত্য কথাগুলি জানতে পেরেছি। দাদু ওই সাঁওতাল বন্ধুকে বকেছিলেন,ছেলেগুলোকে ভয় দেখাতে নাটক করছিলাম। আর তুই এক নম্বরের বোঙা। একবারে অস্ত্র হাতে। যদি মরে যেতো ছেলেটো। বন্ধু বললো,আমাকে অত বোঙা ভাবিস নি। তোর মুনিষটো আমাকে আগেই বলেছে তোর লাটকের কথা। আমি অভিনয়টো কেমন করেছিলাম বল একবার। দাদু ওদের খুব ভালোবাসতেন। ওদের অসময়ের বন্ধু ছিলেন দাদু। দাদুকে আমরা বলতাম টাইগার বাম বা বিপদের বন্ধু। ওষুধ মলমের স্পর্শে যেমন ফোড়া ভালো হয়ে যায়। তেমনি বিপদের সময় দাদুর উপস্থিতি সকল সমস্যার সমাধান করে দিতো। একবার ডেঙা পাড়ায় ডাকাত পরেছিলো। জমিদার বাড়িতে। তখন ফোন ছিলো না। জানাবার উপায় নেই। পাশের বাড়ির একজন দাদুকে ডাকতেএসেছিলো। দাদু ঘুম থেকে উঠেই লাঠি হাতে লোকজন ডেকে সিধে চলে গিয়েছিলেন। তখন লাঠিই প্রধান অস্ত্র। লাঠিখেলায় দাদুর সমকক্ষ কেউ ছিলো না। চারজন বাছা বাছা তরুণকে বললেন,আমার মাথায় লাঠি মারতে দিবি না। তারপর শুরু হলো লড়াই। পঁচিশজন ডাকাত সবকিছু ফেলে লাগালো ছুট। জমিদার দাদুকে বললেন,আপনার জন্যই আজকে বাঁচলাম। ভগবান আপনার ভালো করবেন। বাড়ির মহিলারা দাদুকে মিষ্টিজল খাইয়ে তবে ছাড়লেন। বাকি লোকেরাও খেলেন। দাদুর লাঠি খেলার দলের কথা আশেপাশে সবাই জানতো। দাদুর মুখেই শুনেছি হাটবারে ডাকাত সর্দার হাটে এসেছিলো। বলেছিলো,আপনার মায়ের দুধের জোর বটে। আপনাকে পেন্নাম।সাহসকে বলিহারি জানাই। আপনি ওই গ্রামে থাকতে আর কোনোদিন ডাকাতি করবো না। দাদু বলেছিলে, ছেড়ে দে ডাকাতি। তোকে জমিদার বাড়িতে ভালো কাজ দেবো। শেষে ওই ডাকাতদল জমিদারের লাঠিয়াল হয়েছিলো। ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছিলো। এখন চোর ডাকাতগুলো চরিত্রহীন, দুর্বল,নির্গুণ। সেই ডাকাত সর্দার সন্ধ্যা হলেই দাদু আর জমিদারকে শ্যামাংগীত শোনাতো। সম্পর্কে দাদু হলেই তো আর বুড়ো হয়ে যায় না। দাদুর যখন চল্লিশ বছরের তখন মায়ের বিয়ে হয়েছিলো। দাদু আঠারো বছরেই মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের মুখ থেকে শোনা কথা। বিয়ের পরেও আমার মা তালবোনা পুকুরে তাল পরলেই সাঁতার কেটে সবার আগে তাল কুড়িয়ে আনতেন। দাদু আমার মা,বড়মা সবাইকে সব বিষয়ে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। আর আমার মামা শান্ত লোক।গাঁয়ের মাসি বলতেন, একটা ব্যাটা। দুটি বিটি। তাই ঠাকুমার আদরে দাদা ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে থাকতেন। জুঁইতা গ্রামটা ছিলো একটা ঘরের মতো। গ্রামের বাসিন্দারা সেই ঘরের লোক। কোনোদিন বুঝতে পারিনি, কে আপন, কেই বা পর। গ্রাম না দেখলে ভারতবর্ষকে চেনা অসম্ভব। মামার বাড়ি গেলেই গ্রামে ঢুকতেই স্কুল। তারপর মামার বাড়ি আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। আমার বড়দাকে ওখানে সবাই মিনু বলে ডাকতো। মাকে বলতো গীতু। হাঁটছি হঠাৎ এক মামা বললেন, কিরে গীতু ভালো আছিস,আই মিনে আয়। সুদপে,রিলপে আয়। আমাদের নাম ওখানে আদরের আতিশয্যে বিকৃত হয়ে যেতো।আবার কোনো মাসি বলতেন,আয় গীতু কতদিন পরে এলি, একটু মিষ্টিমুখ করে যা,জল খা। কোন পাষন্ড এই আদরের ডাক উপেক্ষা করবে। কার সাধ্য আছে। ফলে দেরি হতো অনেক। ইতিমধ্যে গীতু,মিনে দের দলবেঁধে আসার খবর রানার পৌঁছে দিয়েছে আগেই। তাই দেখা হয়ে যেতো মামির সঙ্গে কোনো এক বাড়িতে।আঁচলে ডিম আর হাতে মাছ নিয়ে হাসিমুখে হাজির। আরও অনেক কথা হারিয়ে গেছে স্মৃতির গভীরে।
বিজয় ভেবে চলে,কিশোরবেলার কথা।সে ভাবে,তারপর সংসারের টানা পোড়েন।রাগ,হিংসা,ক্রোধের সংমিশ্রণে সংসার স্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবন প্রবাহ এগিয়ে চলে। হয়তো এর ফলেই দাদুর শেষজীবনে সেবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। আমি নিয়ম করে দাদুকে গীতাপাঠ করে শোনাতাম। দাদু কত গল্প বলতেন। কোনোদিন হা পিত্যেশ করতে দেখিনি। আমার সময় কাটতো দাদুর কাছেই বেশি। পড়াশোনার ফাঁকে চলতো গীতাপাঠ। আমি জিজ্ঞেস করতাম,দাদু মরণের পরে আমরা কোথায় যাই? দাদু বলতরন,জানি না ভাই। তবে।।মরণের পরে যদি যোগাযোগ করা যায়,তাহলে আমি তোকে নিশ্চয় জানাবো। দাদু বলতেন, আমি যখন শেষ বিছানায় শোবো,তখন আমি ঈশারা করবো হাত নেড়ে। তখন তুই গীতার কর্মযোগ অধ্যায় পড়ে শোনাবি। তোর মঙ্গল হবে। আমিও শান্তিতে যেতে পারবো। হয়েছিলো তাই। কর্মযোগ পাঠ করা শেষ হতেই দাদুর হাত মাটিতে ধপাস করে পরে গেলো। দাদু ওপাড়ে চলে গেলেন হেলতে দুলতে চারজনের কাঁধে চেপে। মাথাটা দুই বাঁশের ফাঁক গলে বেরিয়ে ঝুলছিলো। আমি বলে উঠলাম, ওগো দাঁড়াও দাদুর লাগবে। মাথাটা ঠিক কর বালিশে দি। কেঁধো বললেন,মরে গেয়েচে। ছেড়ে দে। আমি বললাম, না ঠিক করো। তারপর ঠিক করলো দাদাভাই,দাদুর মাথাটা বালিশে দিয়ে। অনেক বছর অপেক্ষা করেছি,দাদুর কথা শুনবো ওপাড় থেকে। যোগাযোগের উপায় থাকলে নিশ্চয় করতেন। কিন্তু কোনোদিন স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। কথা শোনা তো দূর অস্ত। আমরা ছোটোবেলায় মোবাইল পাই নি। কিন্তু আমরা যেসব আনন্দের অংশিদার ছিলাম সেসব আনন্দ এখনকার ছেলেরা আর পায় না। ইতিহাসের বাইরে চলে গেছে ভুলোলাগা বামুন।তিনি ঝোলা হাতে মাথায় গামছা জড়িয়ে আসতেন শিল্পকর্ম দেখিয়ে রোজগার করতে। তিনি আমাদের বাড়িতে এসে শুরু করতেন নিজের কথা বা শিল্পকর্ম। নাটকের অভিনয়ের ভঙ্গিমায় বলতেন, আর বলো না বাবা। তোমাদের গ্রামে আসতে গিয়ে চলে গেলাম ভুলকুড়ি ভুল করে। তারপর মেলে, কোপা, বিল্বেশ্বর, চুরপুনি, সুড্ডো ঘুরে কোমডাঙ্গা। তারপর কেতুগ্রাম, কেউগুঁড়ি হয়ে গুড়ি গুড়ি পায়ে হেঁটে পোশলা, নঁগা, খাটুন্দি, পাঁচুন্দি হয়ে তৈপুর, পাড়গাঁ, বাকলসা, পাঁচুন্দি, মুরুন্দি, সেরান্দি,খাটুন্দি পার করে কাঁদরের গাবায় গাবায় হেঁটে এই তোমাদের গ্রামে। আমরা জিজ্ঞেস করতাম, এতটা পথ হাঁটলে কি করে দাদু। তিনি বলতেন, সব ভূতের কারসাজি। তেনারা ভুলো লাগিয়ে দেন। ভর করে দেহে। তাই এতটা পথ হাঁটতে পারি। তারপর চালটা, কলাটা, মুলোটা দিতেন তার ঝোলায় আমার মা বা পিসি। ভুলোলাগা বামুন এলেই সেই দিনটা আমাদের খুব ভালো লাগতো। তার পিছু পিছু মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘুরে বেড়াতাম ভুলো লাগা বালক হয়ে। বৃষ্টির পরেই রাম ধনু দেখা যায় । দুঃখ শেষে আনন্দ । আমার পাগলামি যে ভালোবাসে সেই শোভন ।দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে মানুষকে ভালোবাসা র নামই জীবন । নর জীবনে নারী ছাড়া জীবন অচল । তবু কেন এত অন্যায় অত্যাচার নারীর উপর । সাধুবেশে নারীদের বিশ্বাস অর্জন করে ন্যায় অন্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেন তাদের বিশ্বাস হত্যা করা হয় । তারা যে মায়ের ,মাসির আদরের আঁচল । তাদের রক্ষা করার জন্য তৈরি হোক সমস্ত মানবহৃদয় ।যতবার আমি বিপদে পড়েছি রক্ষা পেয়েছি নারী হৃদয়ের কমনীয়তার গুণে ।ভীষণ বন্যায় ভেসে চলেছিলাম স্রোতের তোড়ে । রক্ষা পেয়েছি সর্দার দিদির বলিষ্ঠ হাতের আশ্রয়ে । জীবনে জ্বর হয় বারে বারে । সেবা পেয়েছি স্বপ্না বোনের শাসনে । বারে বারে জীবনযুদ্ধে যখন হেরে যাই ভালোবাসা র আড়ালে মায়াচাদর জড়িয়ে রাখেন আমার বড় সাধের সহধর্মিণী ।আর আমার মা সুখে দুখে শোকের নিত্যদিনের সঙ্গী । পুরো জীবনটাই ঘিরে থাকে নারীরূপী দেবির রক্ষাকবচ । সমগ্র পুরুষ সমাজ আমার মতোই নারীর কাছে ঋণী । তবে কোন লজ্জায় পুরুষ কেড়ে নেয় নারীর লজ্জাভূষণ । পুরুষদের মধ্যেই অনেকে আছেন তাদের শ্রদ্ধা করেন । তাদের রক্ষায় জীবন দান করেন । তারা অবশ্যই প্রণম্য । তাদের জীবন সার্থক ।এই পৃথিবী সকলের স্বাধীন ভাবে বিচরণের স্থান হোক । হিংসা ভুলে পৃথিবীর বাতাস ভালোবাসা ভরুক দুর্বল মানসিআমরা চার বন্ধু। রমেন, জীবন, বিশু আর আমি। যেখানেই যেতাম একসাথে থাকতাম। বিশু ছিলো আমাদের দলের অলিখিত নেতা। নেতা তো এমনি এমনি হয় না। তার কাজ,দল চালানোর কৌশল তাকে নেতা বানিয়েছিলো। একদিন দুপুর বেলায় সে আমাদের ডাক দিলো তার বাঁশি বাজিয়ে। বাঁশির ডাক শুনেই মন চঞ্চল হয়ে উঠতো। ঠিক যেনো রাধার পোড়া বাঁশির ডাক। চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে বটতলায়। আমাদের মিলন অফিস ছিলো এই বটতলা। চারজন ছুটে চলে যেতাম মাঠে। সেখানে বিশুবলতো, দাড়া কয়েকটা তাল কাঁকড়া ধরি । ভেজে খাওয়া যাবে।
বলেই হাত ভরে দিলো সোজা ধানের জমির গর্তে। একটা মাগুর ধরেছি, বলেই মাথা টিপে হাত বের করতেই দেখা গেলো মাছ নয়একটা বড় কালো কেউটে সাপ। বিশু সাপটাকে সাঁ সাঁ করে ঘুরিয়ে সহজেই ছুঁড়ে দিলো দূরে। তারপর তাল কাঁকড়া ধরে ভেজে খাওয়া হলো মাঠে। ভাজার সমস্ত সরঞ্জাম বিশু লুকিয়ে রাখতো একটা পোড়ো বাড়িতে। সাঁতার কাটতে যেতাম নতুন পুকুরে। একবার ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম তার প্রখর বুদ্ধির জোরে। মাথার চুল ধরে টেনে তুলেছিলো ডাঙায়।গ্রীষ্ম অবকাশে বট গাছের ডালে পা ভাঁজ করে বাদুড়ঝোলা খেলতাম বিশুর নেতৃত্বে।তারপর ঝোল ঝাপটি। উঁচু ডাল থেকে লাফিয়ে পড়তাম খড়ের গাদায়। এসব খেলা বিশুর আবিষ্কার। তারপর সন্ধ্যা হলেই গ্রামের বদমাশ লোকটিকে ভয় দেখাত বিশু। সুদখোর সুরেশ মহাজন বটগাছের ডাল থেকে শুনলো, কি রে বেটা খুব তো চলেছিস হনহনিয়ে। আয় তোকে গাছে ঝোলাই। সুদখোর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো। তারপর থেকে ও পথে যেত না মহাজন। সাদা চুলো গান্ধিবুড়িকে রোজ সন্ধ্যাবেলা নিজের মুড়ি খাইয়ে আসতো অতি আদরে। বিশু বলতো, আমি তো রাতে খাবো। বুড়ির কেউ নেই, আমি আছি তো। শ্রদ্ধায় মাথা নত হত নেতার হাসিতে। একবার বন্যার সময় স্কুল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের নেতা। কোথাও সাঁতার জল কোথাও বুক অবধি জল। একটা সাপ বিশুর হাতে জড়িয়ে ধরেছে। বিশু এক ঝটকায় ঝেরে ফেলে দিলো সাপটা। স্কুল আমাদের যেতেই হবে। সাঁতার কাটতে কাটতে আমাদের সে কি উল্লাস। যে কোনো কঠিন কাজের সামনাসামনি বুক চিতিয়ে সমাধান করার মতো মানসিকতা বিশুর ছিলো। সে সামনে আর আমরা চলেছি তার পিছুপিছু। শেষ অবধি পৌঁছে গেলাম স্কুল। হেড মাষ্টারমশাই খুব বাহবা দিলেন স্কুলে আসার জন্য। তিনি বললেন, ইচ্ছা থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।টিফিনের সময় ছুটি হয়ে গেলো। আসার সময় একটা নৌকো পাওয়া গেলো। মাঝি বললেন, আমার বয়স হয়েছে আমি একা অতদূর নৌকা বাইতে পারবো নি বাবু। তাছাড়া আমার এখনও খাওয়া হয় নি।বিশু সঙ্গে সঙ্গে নিজের টিফিন বের করে দিলো। আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো টিফিন বের করে দিলাম। মাঝি ভাই বললেন, এসো সবাই এক হয়ে খেয়ে লি। তারপর নৌকার কান্ডারি হলো বিশু। আর আমরা সবাই মুড়ি মাখিয়ে খেতে শুরু করলাম। মাঝি ভাই ও বিশু খেলো। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম গ্রামে। মাঝি ভাইকে পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় জানালাম।পরের দিন রবিবার। রঙিন সকাল। আকাশে মেঘের আনাগোনা। কাশের কারসাজি নদীর তীর জুড়ে। বন্যার জল নেমে গিয়েছে। পুজো পুজো ভাব। বিশু কাশফুলের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কয়েকদিন হলো তাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি ঘুরতে ঘুরতে পুজো বাড়ির ঠাকুর দেখতে গেলাম। সেখানে দেখি বিশু হাতে কাদা মেখে শিল্পীকে সাহায্য করছে। তিন দিন ধরে এখানেই তার ডেরা। এখন তার মনে বাজছে ঢাকের ঢ্যামকুড়াকুড়। মন মন্দিরে তার দুর্গা গ্রামদেশ ছাড়িয়ে অভাবি বাতাসে বাতাসে। পুজো বাড়িতে আমাকে দেখেও কোনো কথা না বলে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে চলে গেলো।আমি জানি সে এখন চাল, ডাল নিয়ে সর্দার বুড়িকে রেঁধে খাওয়াবে। সে বলে, ওর যে কেউ নেই। ও খাবে কি? বিশুর বাবা বছরে একবার বাড়ি আসেন। তিনি ভারতীয় সৈন্য বিভাগে কাজ করেন। বাড়িতে এলেই বিশুর হাতে হাতখরচ বাবদ তিনি বেশ কিছু টাকা দিয়ে যান। সেই টাকা বিশু লোকের উপকারে কাজে লাগায়।বড়ো অবাক হয়ে ভাবি, ছোটো বয়সে এতবড় মন সে পেল কোথা থেকে?
স্কুলের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় আমাদের চার বন্ধুর বাড়ির গার্জেনরা শলা পরামর্শ করে হোষ্টেলে থাকার কথা বললেন। দায়িত্ব নিলো বিশু। কিন্তু হেড মাষ্টারমশাই বললেন, সেশনের মাঝে হোষ্টেল পাবি না। ঘর ভাড়া নিয়ে চারজনে থাক। পরীক্ষা এসে গেছে। কাছাকাছি থাকিস তিনটি মাস। রেজাল্ট ভালো হবে।ঘুরে ঘুরে অবশেষে ভাড়া ঘর পেলাম। কিন্তু বাড়িওয়ালার পাশের প্রতিবেশি বললেন, সাবধান ওই বাড়িতে ভূত আছে। আমরা ভয় পেয়ে তিনজনে বলেুু উঠলাম, তাহলে অন্য ঘর দেখি চল।বিশু বললো, টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। ভূতের বাড়িতেই থাকবো। বিশু যখন সঙ্গে আছে, ভয় কি তোদের।তার অভয় বাণী ভরসা করে আমরা মাল পত্তর নিয়ে ঢুকে পড়লাম লড়াইয়ের কোর্টে। ক্যাপটেন বিশু বাড়িটা এক চক্কর পাক দিয়ে হাতে একটা লাঠি নিয়ে বললো, চলে আয় ভূতের বাচ্চা। আমরা ওর সাহস দেখে অবাক হতাম। রমেন বলে উঠলো, ভূতের শেষ দেখে ছাড়বো। জীবনের মরণের ভয় একটু বেশি। সে কাঁপা গলায় বলে উঠলো, যদি গলা টিপে ধরে ভূত। বিশু বললো, ভয় নেই, আমি একাই একশো। তোর কিছু হবে না। হলে আমার হবে।
এই বাড়ির নিচু তলায় কিছু অসামাজিক লোকের কাজকর্ম বিশু এক সপ্তাহের মধ্যেই টের পেয়ে গেলো। তারাই এই ভূতের ভয় দেখায়। একদিন জীবন বাথরুম গেছে এমন সময় নাকি সুরে একজন বলে উঠলো, এঁখান থেকে পাঁলা। ঘাড় মটকে দেবো। আবার একদিন রমেন ভয় পেলো। ঠিক সেই বাথরুমে। বিশু তদন্ত করে দেখলো বাথরুমের ভেন্টিলেটার ভেঙ্গে একটা সরু দড়ি ঢোকানো হয়েছে। বাইরে গিয়ে দেখলো দড়িটা নিচের ঘরের বারান্দায় শেষ হয়েছে। বাথরুমে ভাঙ্গা কাঁচে টান পরলে বিকট আওয়াজ হয়। আর মুখ বাড়িয়ে মুখোশ পড়ে নাকি সুরের কথায় সকলেই ভয় পাবে। বিশু বললো সবাই তৈরি থাকিস। আজ রাতেই ভূত ধরবো।আজ আর কেউ স্কুল গেলাম না। একটা উত্তেজনা রাতে জাগিয়ে রেখেছে। এবার সেই বিকট শব্দ। বিশু বাঘের মতো লাফিয়ে লাঠি হাতে নিচের তলায় গিয়ে জলজ্যান্ত ভূতের পাছায় লাঠির আঘাতে ভূতকে কাবু করে ফেললো। ভূত বাবাজি জোড় হাতে বলছে, ছেড়ে দাও বাবা আমি আর ওসব করবো না। ভূতের সঙ্গিরা সব পালিয়েছে, আমাদের হাতে লাঠি দেখে। বিশু বললো, যাও, যেখানে বিশু আছে সেখানে চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। বিপদে পড়বে।তারপর থেকে আর কোনোদিন ভূতের উপদ্রব হয়নি সেই বাড়িতে।বিশুর বাহাদুরি দেখেই আমরা সাহসী হয়ে উঠেছিলাম। বিশুর সঙ্গে আমরা বেরোলে সকলের চোখেমুখে একটা সাহসের,শান্তির ছাপ ফুটে উঠতো। পাড়ার কোনো মানুষ বিপদে পরলে বিপদের বন্ধু এই টাইগার বিশুকেই স্মরণ করতো। তার সঙ্গে আমরা তো থাকতাম অবশ্যই। রমেন, জীবন,বিশু,আমি একবার বন্যার সময় নৌকা করে মানুষের খাবার জোগাড় করতে চড়খী গ্রামে গিয়েছিলাম। হেলিকপ্টার থেকে চিড়ের বস্তা,গুড়ের বস্তা ফেলছে চড়খীর ব্রীজে যার আসল নাম কাশীরাম দাস সেতু। সেখান থেকে আমরা চিড়ে, গুড়ের পাটালি নৌকায় তুললাম। রমেন পেটুক। বললো, একটু টেষ্ট করলে হয় না। বিশু বললো, এখন এটা সকলের সম্পত্তি। যা হবে সকলের সামনে হবে। কেউ হাত দিবি না। এখন তাড়াতাড়ি চল। বান বাড়ছে। বিশু দাঁড় টানেআর আমরা সবাই সাহায্য করে নৌ্কা ও খাবার নিয়ে চলে এলাম নতুন পুকুরের পাড়ে। সেখানে বাড়ি বাড়ি সকলকে সমানভাবে খাবার ভাগ করে দিলো বিশু। তারপর আমরা বাড়ি এসে জীবনের মায়ের হাতের রান্না, গরম খিচুড়ি আর পেঁপের তরকারি খেলাম। অমৃতের স্বাদ। বিশু বললো, কাকীমা অনেক পেঁপে গাছ পড়ে গেছে বন্যার স্রোতে। আমরা আপনাকে অনেক পেঁপে এনে দেবো। সেবার বন্যায় পেঁপে, গ্রামের লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। আমাদের গ্রাম অজয় নদীর ধারে। গ্রামগুলিও খুব নীচুস্থানে অবস্থিত। নদীর নাব্যতা বা গভীরতা অল্প। ফলে বন্যা প্রায় প্রতি বছর দেখা দিয়ে যেতো। জল যখন কমে যেতো তখন তোতনের মা ও পাড়ার মা বোনেরা মাঠে মাছ ধরার জন্য যেতো। নানারকমের শাক, ঢোল কলমি, শুশুনি তুলতো। খুব ভালো লাগতো নানারকমের মাছ ভাজা খেতে। আমি দেখলাম, তোতনের মা মাঠ থেকে দুই তিন রকমের শাক তুলেছে। ওরা ভিটামিন বোঝে না, শরীরচর্চ্চাও বোঝে না। ওরা জানে খাটবো, রোজগার করবো আর খাবো পেট ভরে। মাঠেই পাওয়া যেতো বেশির ভাগ শাক, সব্জী। , খলসে, ওআরও নানারকমের মাছ মাঠের জলে সাঁতার কেটে বেড়াতো। বেলে, তে চোখো,চ্যাঙ,ছিঙুরি,গচিমাছ ছাড়াও ছোটো কাঁকড়া তাল কাঁকড়া পাওয়া যেতো। গর্তে হাত ঢুকিয়ে বিশু অনরকবার তআল কাঁকড়া বের করে আমাদের দেখিয়েছে। পাঁকাল,গুঁতে,কৈ,মাগুর,ল্যাটা প্রভৃতি অসংখ্য মাছ। বিত্তি পেতে দিতো স্রোতের মুখে।বিশু বলছে, খাল কেটে মাঝখানে বিত্তি পেতে জল যাওয়ার নালা কেটে দিতো। মাছ লাফিয়ে ওই গর্তে পড়তো। টানা জাল,পাতা জাল দিয়ে মাছ ধরতো। এখন তোতনের মায়ের জায়গায বৌমা মাঠে যায়। কিন্তু কৃষিকাজে সার, ওষুধ প্রয়োগ করার ফলে সেইসব মাছ ইতিহাসের পাতায় চলে গেছে। শাকপাতাও পায় না মা বোনেরা। এখন সব বাজারমুখী।। তখন শাক আঁচলে করে নিয়ে গিয়ে বাউরীবউ মুড়ি নিয় আসতো চাষি বাড়ি থেকে। মাঠের টাটকা শাক সবাই নিতো জলের দরে। আজ আর টাটকা কিছু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুর কথা একশো শতাংশ সত্য। এখন আমরা বড় হয়ে গেছি। কিন্তু, স্বর্ণ যুগের সেইসব স্মৃতি মনের মণিকোঠায়চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমার মা বলতেন,ছোটো থাকাই ভালো রে,সংসার অসার। মা বলতেন,এখন সংসাররূপ চিতায় জ্বলে মরছি মরণের পরে প্রকৃত চিতায় পুড়ে যাবে আদরের দেহ...স্বজন বন্ধুরা বলবে. আর কত সময় লাগবে শেষ হতে...একটু দ্রুত করো ভাই...তবে কিসের এত অহংকার...কেন এত লোভ ... ভালোবাসায় কৃপণতা। কে ধনী... টাকায় চিতা সাজালেও পরিণতি একই..।কৃষ্ণধনে ধনী যেজন
নিজ ধামে ফেরে সেজন..।লক্ষ্মীপুজো এলেই মা বলতেন কোজাগরির অর্থ।
তিনি বলতেন, কোজাগরি লক্ষীপুজোয় পুজো করার পরে যে গৃহস্থ রাত্রি জাগরণ করে রাত কাটাবে তার ঘরে লক্ষী স্বয়ং বিরাজ করেন। কোনো অভাব, অনটন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। স্বার্থ নিয়েই মানুষ পুজো করে। কারণ সে সংসারী। ছেলে, মেয়ে, বাবা,মা, ঠাকুমা, দাদু সকলকে নিয়ে এই সংসার। তাদের মঙ্গল কামনা করেই মানুষের এই পুজো পার্বণ। বাজারে দরদাম করে ঠাকুর কেনার পরে পুজোর ফলমূল, দশকর্মার জিনিসপত্র কিনে বাড়িতে আলপনা এঁকে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর পুরোহিতের পৌরোহিত্যে গৃহস্থের মঙ্গলসাধন। লৌকিক আচার, আচরণে বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে। আর বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। পুজোর প্রতিটি পর্যায়ে শিল্প ভাবনা বিরাজ করে। তারফলে পুজো আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দুর্গাপুজোয় ঢাক বাজে। প্যান্ডেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোনো কিছুর আদলে মন্দির বানানো হয়। যেমন, তাজমহল, খাজুরাহো, কোনারক প্রভৃতি। নানারকম বাদ্যযন্ত্র পুজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। মা আমাদের নিয়ে,কাটোয়ার কার্তিক লড়াই, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রি পুজো, কাগ্রামের জগদ্ধাত্রি পুজো,শিবলুনের মেলা,উদ্ধারণেরপুরের মেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন। পুজো এলেই মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপি উন্মুক্ত হয়ে যেতো। কোজাগরীর রাতে মা কম করে তিনশো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। মাজা নীচু করে আসনে বসা মানুষদের প্রসাদ বিতরণ করতাম আমরা ভাই বোনেরা। পরের দিনও খিচুড়ির ব্যবস্থা থাকতো। ডোমপাড়ার সকলে এসে নিয়ে যেতো আনন্দে। সর্দার বুড়ি বেসকা দি, মঙ্গলীদি সবাই আসতো। ছোটো পিসি, মানা, বড়পিসী, সন্ধ্যা,রুনু, শংকরী সকলে আসতো। মায়ের ঘর পূর্ণ হয়ে উঠতো অতিথি সমাগমে। গম্,গম্ করতো বাড়ি। মানুষই যে লক্ষ্মী তা আবার প্রমাণ হয়ে যেতো চিরকালের সত্য সুরে।পুজোর বেশ কিছুদিন পরে মেয়েরা সকলে এক হয়ে মাংস, ভাতের ফিষ্টি করতো। মনেআছে আমার, খেতে এসে বিশাখাদি বলেছিলো, আমি বিধবা মাংস খবো কি করে? আমার মাসতুতো দিদি বলেছিলো, বিধবা আবার কি কথা? তোর স্বামী মরে গেছে। দুঃখের কথা। তার সঙ্গে মাংসের কি সম্পর্ক। আচ্ছা কেউ মনে কর মাংস খেলো না। আর মনে মনে স্বামীকে দোষ দিলো। সমাজপতিরা, সমাজের সেনাপতিরা মনের নাগাল কি করে পাবে? ওদের হাত ওই মাংস অবধি। অতএব, নো চিন্তা, ডু ফুর্তি।বিশাখাদি আনন্দে মাংস খেয়েছিলো। সমস্ত কিছুতেই চিরকাল কিছু মহিলার সংস্কারমুক্ত মনের জন্য পৃথিবী এত সুন্দর। উন্মুক্ত সমাজ আমাদের সর্দার পাড়ার। সেখানে সমাজের কোনো সেনাপতি বিধি আরোপ করে না। যে যারইচ্ছেমতো খেটে খায়। কেউ মুনিষ খাটে, কেউ মাছ ধরে, কেউ কেরালা সোনার দেকানে কাজ করে। বুড়ো বয়সে তারা ছেলে মেয়েদের রোজগারে খায়। ওদের কাউকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হয় না। কার কৃপায় ওরা বুড়ো বুড়ি হয় না? শক্ত সমর্থ থাকতেই পরকালের ডাকে ওপাড়ে চলে যায়। কাজই হলো আসল লক্ষ্মী। কদতলার মাঠে এসে ঢিল মেরে পেরে নিতাম কাঁচা কদবেল। কামড়ে কচ কচ শব্দে সাবাড় করতাম কদ। বুড়ো বলতো, কদ খেয়ছিস। আর খাবি। কই তখন তো গলা জ্বলতো না। এখন শুধু ওষুধ। ভক্ত,ভব,ভম্বল,বাবু বুলা, রিলীফ সবাই তখন আমরা আমড়া তলায় গিয়ে পাকা আমড়া খেতাম। জাম, তাল,বেল, কুল,শসা, কলা, নারকেল কিছুই বাদ রাখতাম না। নারকেল গাছে উঠতে পারতো গজানন। শুধু দুহাতের একটা দড়ি। তাকে পায়ের সঙ্গে ফাঁদের মতো পরে নিতো গজানন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নারকেল গাছের পাতা সরিয়ে ধপাধপ নিচে ফেলতো। আমরা কুড়িয়ে বস্তায় ভরে সোজা মাঠে। বাবা দেখলেই বকবেন। তারপর দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে মাঠেই খেয়ে নিতাম নারকেল। একদম বাস্তব। মনগড়া গল্প নয়। তারপর গাজনের রাতে স্বাধীন আমরা। সারা রাত বোলান গান শুনতাম। সারা রাত নাচতাম বাজনার তালে তালে।শীতকালে খেজুর গাছের রস। গাছের কামান হতো হেঁসো দিয়ে। মাথার মেথি বার করে কাঠি পুঁতে দিতো গুড় ব্যাবসায়ী। আমাদের ভয় দেখাতো, ধুতরা ফুলের বীজ দিয়ে রাকবো। রস খেলেই মরবে সে। চুরি করা কাকে বলে জানতাম না। একরাতে বাহাদুর বিশুর পাল্লায় পরে রাতে রস খেতে গেছিলাম। বিশু বললো, তোরা বসে থাক। কেউএলে বলবি। আমি গাছে উঠে রস পেরে আনি। তারপর গাছে উঠে হাত ডুবিয়ে ধুতরো ফুলের বীজ আছে কিনা দেখতো। পেরে আনতো নিচে। তারপর মাটির হাঁড়ি থেকে রস ঢেলে নিতাম আমাদের ঘটিতে। গাছেউঠে আবার হাঁড়ি টাঙিয়ে দিয়ে আসতো বিশু। সকালে হাড়ি রসে ভরে যেতো। ভোরবেলা ব্যাবসায়ির কাছে গিয়ে বলতাম, রস দাও, বাড়ির সবাইকে দোবো। বুক ঢিপঢিপ চাঁদের গর্ত। দেবে কি দেবে না, জানিনা। অবশেষে প্রাপ্তিযোগ। যেদিন রস পেতাম না তখন মাথায় কুবুদ্ধির পোকা নড়তো। তাতে ক্ষতি কারো হতো না। বিশু ভালো মিষ্টি রস হলে বলতো, এটা জিরেন কাঠের রস। মানে চারদিন হাড়ি না বাঁধলে রস মিষ্টি হতো। জানি না। আমরা গাছে নিচে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। রস পরতো জিভে টুপ টাপ। কতদিন ঘনটার পর ঘনটা কেটে গেছে রসাস্বাদনে। মোবাইল ছিলো ন।,ফেসবুক ছিলো না। কোনো পাকামি ছিলো না।সহজ সরল হাওয়া ছিলো। ভালোবাসা ছিলো। আনন্দ ছিলো জীবনে। ব্লু হোয়েলের বাপ পর্যন্ত আমাদের সমীহ করে চলতো। কোনোদিন বাল্যকালে আত্মহত্যার খবর শুনিনি। সময় কোথায় তখন ছেলেপিলের। যম পর্যন্ত চিন্তায় পরে যেতো বালকদের আচরণে, কর্ম দক্ষতায়। আমাদের একটা বন্ধু দল ছিলো । পুজোর সময় রাত জেগে ঘুরতুম কোলকাতার অলিগলি । হাওড়া ব্রিজ থেকে শিয়ালদহ । পায়ে হেঁটে । গোল হয়ে প্রাচী পেরিয়ে হাঁটার নেশায় চলে আসতাম আবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে সোজা কলেজ স্কয়ার । জীবনের তিরিশটা বছর তিল তিল করে খরচ করেছি আনন্দের খোঁজে। অসীম বলে সীমাহীন আনন্দের ছেলেটা গান গাইতো সুন্দর । বিচ্ছু বলে বন্ধুটা ভালোবাসতো অপলক মায়া জড়ানো চোখের সুন্দরী কে । তাকে দেখলেই বিচ্ছু ওথেলো হয়ে যেতো ।অমিত রান্না করতো খুব ভালো । পুরী আর দীঘাতে ওর হাতের রান্না খেয়ে আনন্দিত আমরা ওকে একটা জামা উপহার দিয়েছিলাম । ও শেফ হতে চেয়েছিলো । অনিন্দিতা বলে বান্ধবী টা আমাদের মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো । কিন্তু সব স্বপ্ন গুলো বিস্ফারিত চোখের কাছে থমকে গিয়েছিলো ।অই বন্ধুরা একত্রে সমাজ সেবার প্রচেষ্টায় আছে । রাস্তার অভুক্ত মানুষের মুখে একটু নুনভাত জোগানোর জন্য ওরা ভিক্ষা করে, জীবনমুখী গান শুনিয়ে । অসীম গান করে,বিচ্ছু একতারা বাজায় । অমিত আর অনিন্দিতা সুরে সুর মিলিয়ে স্বপ্ন দেখে । ওরা এখনও স্বপ্ন দেখে । হয়তো চিরকাল দেখে যাবে থমকা লাগা স্ট্যাচুর পলক..ছোটোবেলার রায়পুকুরের রাধা চূড়ার ডালটা আজও আমায় আহ্বান করে হাত বাড়িয়ে । এই ডাল ধরেই এলোপাথারি হাত পা ছুড়তে ছুড়তে সাঁতার শিখেছি আদরের পরশে । ডুবন্ত জলে যখন জল খেয়ে ফেলতাম আনাড়ি চুমুকে, দম শেষ হয়ে আসতো তখন এই ডাল তার শক্তি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরতো অক্লেশে । হয়তো পূর্ব জন্মে আমার দিদি হয়ে যত্ন আদর করতো এই ডালটা । কোনোদিন তাকে গাছ মনে করিনি আমি ।এখনও জল ছুঁয়ে আদরের ডাক শুনতে পাই পুকুরের ধারে গেলে । রাধা নামের মায়াচাদর জড়ানো তার সবুজ অঙ্গে ।ভালো থেকো বাল্য অনুভব । চিরন্তন প্রকৃতির শিক্ষা অঙ্গনে নাম লিখে যাক নব নবীন শিক্ষার্থী প্রবাহ ।আমার স্বপ্নের সুন্দর গ্রামের রাস্তা বাস থেকে নেমেই লাল মোড়াম দিয়ে শুরু ।দুদিকে বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস রাস্তায় পরম আদরে ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে । কত রকমের পাখি স্বাগত জানাচ্ছে পথিককে । রাস্তা পারাপারে ব্যস্ত বেজি , শেয়াল আরও অনেক রকমের জীবজন্তু।.চেনা আত্মীয় র মতো অতিথির কাছাকাছি তাদের আনাগোনা । হাঁটতে হাঁটতে এসে যাবে কদতলার মাঠ। তারপর গোকুল পুকুরের জমি, চাঁপপুকুর, সর্দার পাড়া,বেনেপুকুর । ক্রমশ চলে আসবে নতুন পুকুর, ডেঙাপাড়া ,পুজোবাড়ি, দরজা ঘাট, কালী তলা । এখানেই আমার চোদ্দপুরুষের ভিটে । তারপর ষষ্টিতলা ,মঙ্গল চন্ডীর উঠোন , দুর্গা তলার নাটমন্দির । এদিকে গোপালের মন্দির, মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, তামালের দোকান, সুব্রতর দোকান পেরিয়ে ষষ্ঠী গোরে, রাধা মাধবতলা । গোস্বামী বাড়ি পেরিয়ে মন্ডপতলা । এই মন্ডপতলায় ছোটোবেলায় গাজনের সময় রাক্ষস দেখে ভয় পেয়েছিলাম । সেইসব হারিয়ে যাওয়া রাক্ষস আর ফিরে আসবে না ।কেঁয়াপুকুর,কেষ্টপুকুরের পাড় । তারপর বাজারে পাড়া ,শিব তলা,পেরিয়ে নাপিত পাড়া । এখন নাপিত পাড়াগুলো সেলুনে চলে গেছে । সাতন জেঠু দুপায়ের ফাঁকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরতেন মাথা ,তারপর চুল বাটি ছাঁটে ফাঁকা । কত আদর আর আব্দারে ভরা থাকতো চুল কাটার বেলা ।এখন সব কিছুই যান্ত্রিক । মাঝে মাঝে কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়েকে রোবোট মনে হয় । মুখে হাসি নেই । বেশ জেঠু জেঠু ভাব ।সর্বশেষে বড়পুকুর পেরিয়ে পাকা রাস্তা ধরে ভুলকুড়ি । আর মন্ডপতলার পর রাস্তা চলে গেছে খাঁ পাড়া , কাঁদরের ধার ধরে রায়পাড়া । সেখানেও আছে চন্ডীমন্ডপতলা , কলা বা গান, দুর্গা তলার নাটমন্দির সব কিছুই । পুজোবাড়িতে গোলা পায়রা দেখতে গেলে হাততালি দিই ।শয়ে শয়ে দেশি পায়রার দল উড়ে এসে উৎসব লাগিয়ে দেয়। পুরোনো দিনের বাড়িগুলি এই গ্রামের প্রাণ ।এই গ্রামে ই আমার সবকিছু , আমার ভালোবাসা, আমার গান।ছোটোবেলার সরস্বতী পুজো বেশ ঘটা করেই ঘটতো । পুজোর দুদিন আগে থেকেই প্রতিমার বায়নাস্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে আসা হত শিল্পী কে ।তারপর প্যান্ডেলের জোগাড় । বন্ধুদের সকলের বাড়ি থেকে মা ও দিদিদের কাপড় জোগাড় করে বানানো হত স্বপ্নের সুন্দর প্যান্ডেল । তার একপাশে
বানানো হত আমাদের বসার ঘর । পুজোর আগের রাত আমরা জেগেই কাটাতাম কয়েকজন বন্ধু মিলে । কোনো কাজ বাকি নেই তবু সবাই খুব ব্যস্ত । একটা ভীষণ সিরিয়াস মনোভাব । তারপর সেই ছোট্ট কাপড়ের পাখির নিড়ে কে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা কেউ জানতে পারতাম না । মশার কামড়ও সেই নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভাঙাতে পাড়তো না ।তবু সকালে উঠেই মচকানো বাঁশের মত ব্যস্ততার আনন্দ । মা বাবার সাবধান বাণী ,ডেঙ্গু জ্বরের ভয় কোনো কিছুই আমাদের আনন্দের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি । হড়কা বানে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে , আমাদের আনন্দ ঠিক আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত মহানন্দের জগতে । এরপরে সকাল সকাল স্নান সেরে ফলমূল কাটতে বসে পড়তাম বাড়ি থেকে নিরামিষ বঁটি এনে । পুরোহিত এসে পড়তেন ইতিমধ্যে । মন্ত্র তন্ত্র কিছুই বুঝতাম না । শুধুমাত্র বুঝতাম মায়ের কাছে চাইলে মা না করতে পারেন না । পুষ্পাঞ্জলি দিতাম একসঙ্গে সবাই । জোরে জোরে পুরোহিত মন্ত্র বলতেন । মন্ত্র বলা ফাঁকি দিয়ে ফুল দিতাম মায়ের চরণে ভক্তিভরে । তারপরে প্রসাদ বিতরণের চরম পুলকে আমরা বন্ধুরা সকলেই পুলকিত হতাম । প্রসাদ খেতাম সকলকে বিতরণ করার পরে ।আমাদের সবার প্রসাদে ভক্তি বেশি হয়ে যেত ,ফলে দুপুরে বাড়িতে ভাত খেতাম কম । সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ ,ধূপ জ্বেলে প্যান্ডেলের ঘরে সময় কাটাতাম । পরের দিন দধিকর্মা । খই আর দই । পুজো হওয়ার অপেক্ষায় জিভে জল । তারপর প্রসাদ বিতরণ করে নিজেদের পেটপুজো সাঙ্গ হত সাড়ম্বরে ।এরপরের দৃশ্য প্রতিমা বিসর্জন । কাছেই একটা পুকুর । রাত হলে সিদ্ধিলাভে(দামীটা না) আনন্দিত হয়ে নাচ তে নাচতে অবশেষে শেষের বাজনা বেজে উঠতো । মা তুই থাকবি কতক্ষণ, তুই যাবি বিসর্জন ।
তার সাথে আমাদের মনটাও বিসর্জনের বাজনা শুনত দুদিন ধরে।সুমন্ত ভট্টাচার্য শুধু একজন যোগ্য বিজ্ঞানী নন। তিনি একাধারে চিকিৎসক, সন্ধানী গোয়েন্দা আবার কিশোর মনো বিজ্ঞান পত্রিকার সহ সম্পাদক । তিনি এক বনেদী পরিবারের সন্তান । পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্ব পুরুষ রা বাস করতেন । অই বংশের একাংশ আবার জলপাইগুড়ি তে বাস করতেন । কিন্তু কালের প্রবাহে কোনো কিছুই স্থির নয় । এখন কে কোথায় ছিটকে পৃথিবীর কোন জায়গায় আছেন তার সন্ধান করা সহজ কাজ নয় । জয়ন্ত দা বসে বসে এইসব ভাবছেন আর মনে মনে প্রার্থনা করছেন, যে যেখানেই থাকুন, তারা যেনো সবাই সুখে শান্তিতে থাকেন ।
হঠাৎ রত্না দি র ডাকে সুমন্ন্ত দার লুপ্ত চেতনা ফিরে এলো । দাদা বললেন , বসো বসো আমি একটু আসছি ।তারপর দুই কাপ চা এনে বললেন, দিদি চা খাও ।দাদা চা খুব ভালো করেন ।দিদি বললেন, দাদা চা খুব ভালো হয়েছে ।দাদা বললেন, ধন্যবাদ। তার পর কি খবর বলো ।দিদি বললেন, গতকাল এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন বেড়াতে যাওয়ার জন্য।কোথায় ?বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া র কাছে মথুরাপুর গ্রামে । দাদা নতুন জায়গা দেখতে ভালোবাসেন । ব্যাগ পত্তর গুছিয়ে পরের দিন দুজনে হাওড়া রামপুর হাট এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে বস লেন ।ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাওয়া অন্তরে এক অদ্ভূত অনুভূতির সৃষ্টি করে । এ রসে যে বঞ্চিত তাকে বোঝানো কঠিন । দাদা ও দিদিকে এই কথা গুলি বলছিলেন ।দিদি বললেন, সত্য কথা । ট্রেন জার্নির স্বাদ আলাদা ।তারপর বারোটার সময় ওনারা মথুরাপুর গ্রামে এসে গেলেন । পরেশবাবু ফোনে খবর পেয়ে আগে থেকেই তৈরি ছিলেন ।জলটল খাওয়ার পর পরেশবাবু দাদাও দিদিকে নিয়ে ময়ুরাক্ষী নদী দেখাতে নিয়ে গেলেন । নদীতে এখন বেশি জল নেই ।পায়ে হেঁটে ওনারা নদীর ওপাড়ে গেলেন ।পরেশবাবুর ব্যবহার দেখে দাদা ও দিদি খুব মুগ্ধ হলেন ।তারপর খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকালে গ্রাম ঘোরার পালা । কত কিছু দেখার আছে আমাদের দেশের গ্রামে । গাছপালা নদীনালা এই নিয়েই আমাদের গ্রাম । কবিগুরু তাই বলেছিলেন, " দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ... একটি ঘাসের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু "।আমরা আজীবন ঘুরে বেড়াই, আনন্দের খোঁজে । আর এই আনন্দ হলো জীবনের আসল খোঁজ । কথা গুলি জয়ন্ত দা বললেন ।দিদি পরেশ বাবু কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন । পরেশ বাবুও কথা বলে খুব আনন্দ পেলেন ।তার পর রাতে খাওয়া বেশ ভালোই হলো । পরেশ বাবুর বিরাট জায়গা জুড়ে বাগান ।অনেক হিম সাগর আম । গাছের টাটকা আম । আর সাঁকিরের পাড় থেকে আনা দৈ আর রসগোল্লা । রসিক মানুষ জয়ন্ত দা । বললেন, পরেশবাবু কব্জি ডুবিয়ে ভালোই খেলাম ।পরেশবাবু বললেন, আপনাদের খাওয়াতে পেরে আমি খুব খুশি ।ভোরবেলা তখন চারটে বাজে । জয়ন্ত দার ঘুম ভেঙ্গে গেলো । পরেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার এত কল রব কেন ?পরেশবাবু বললেন, আর বলবেন না । আমার বাগানে অনেক জবা গাছ আছে নানা জাতের । কোনোটা লঙ্কা জবা, পঞ্চ মুখী , গণেশ জবা , সাদা জবা, ঝুমকো জবা ,খয়েরী জবা , লাল, ঘিয়ে জবা প্রভৃতি।এখন একটা লাল জবা গাছে ঘিয়ে জবা হয়েছে । সবাই তাই ভোরবেলা পুজো দেয় । বলে , ঠাকুরের দয়া । তাই এক গাছে দুই রকমের ফুল ।দিদি দেখছেন প্রচুর মহিলা চান করে কাচা কাপড় পড়ে পুজো দিতে এসেছেন ।দাদা বললেন , এদের বোঝাতে হবে ।এটা বিজ্ঞান নির্ভর ব্যাপার ।দিদি বললেন , আপনারা শুনুন, এটা বিজ্ঞানের ব্যাপার ।তখন মহিলাদের একজন বললেন, একথা বলবেন না দিদি । পাপ হবে ।দিদি বললেন , পরাগ মিলনের ফলে লাল গাছের পরাগ রেণু ঘিয়ে গাছের পরাগ রেণুর সঙ্গে মিলিত হয় । এই কাজটি করে পতঙ্গ রা ।সংকারয়নের ফলে জটিল পদ্ধতি পার করে এইসব ব্যাপারগুলো হয় । সেসব বুঝতে গেলে আরও পড়াশুনা করতে হবে ।আরেকজন মহিলা বললেন, কই আর কোনো গাছে তো হয় নি ।দিদি বললেন, এত বড় বাগান ঘুরে দেখুন। নিশ্চিত দেখা যাবে ।দাদা জানেন সবাই প্রমাণ চায় । প্রমাণ ছাড়া এদের কুসংস্কার মন থেকে যাবে না ।দাদা ডাক লেন, আপনারা এদিকে আসুন । দেখুন এখানেও দুটি গাছে অই একই ঘটনা ঘটেছে।সবাই ওখানে গিয়ে দেখলেন, সত্য কথা তাই হয়েছে । লাল গাছে ঘিয়ে জবা ।দাদা বললেন ,মনে রাখবেন বিজ্ঞান অসম্ভব কে সম্ভব করে । বিজ্ঞান এর দৃষ্টি দিয়েই আমাদের সবকিছু বিচার করতে হবে ।সবাই বুঝতে পারলেন এবং খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলেন ।পরেশবাবু বললেন, এবার আপনাদের জন্য কফি নিয়ে আসি বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে কবি কাশীরাম দাসের জন্ম স্থান ।অই গ্রামে আমার এক আত্মীয় বাড়িতে ক্ষেত্রপাল পুজোর সময় বেড়াতে গেছিলাম ।এই পুজোর সময় এই গ্রামে খুব ধূমধাম হয় ।রতন আমার থেকে বয়সে একটু ছোটো হলেও বন্ধু র মতোই ভালোবাসি । যেখানে যাই আমরা দুজন একসাথে যাই ।আমার অনেক দিনের ইচ্ছা কিশোর মনোবিজ্ঞানের সহ সম্পাদক সুমন্ত ভট্টাচার্য ও সহ সম্পাদনা সচিব রত্না রায় কে এই সিঙ্গিগ্রামের পুজো দেখাবো । রতন কে আগেই বলে রেখেছি । দাদা ও দিদিকেও একমাস আগে বলে রেখেছি ।আজ তাঁরা আসবেন ।আমরা ক্ষেত্র পাল তলায় ঢাকের তালে মত্ত । হঠাৎ একটি ছোট ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে সবাই কে বলছে, সবাই দেখে এসো মিত্র বাড়িতে ঠাকুর এসেছে ।আমরা ছেলেটির কথা শুনে কৌতূহল বশত মিত্র বাড়িতে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য ।
-কি হয়েছে রে,একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম । মেয়েটি বললো, জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর স্বয়ং জগন্নাথ ঠাকুর এসেছেন ।ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম , একটি বড় পোকা ঠিক জগন্নাথ ঠাকুরের মত সব কিছু ।খুব আশ্চর্য হওয়ার কথা ।এদিকে দাদা ও দিদি এসে গেছেন । ওনাদের বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গোলাম । কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হলে গ্রামের সবকিছু ঘুরে দেখলেন । পাশের গ্রামে অনেক ভেড়া ,ছাগল জাতীয় পশু দের বলি দেওয়া হচ্ছে দেখে দাদা ও দিদির খুব রাগ হলো ।ওনারা বললেন, এই সুযোগে বলি প্রথা বন্ধ করতে পারলে ভালো হয় । দেখা যাক এই নিরীহ পশু দের যদি বাঁচানো যায়। তার জন্য একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলে নিতে হবে ।
যাইহোক গ্রাম ঘুরে বেশ ভালো লাগলো ওনাদের ।রাত্রিবেলা সোরগোল । জগন্নাথ ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে অনেকেই অসুস্থ । তারা সবাই কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ।দাদা মন্দিরের ভিতর ঢুকে বললেন, এত পশুর বলি দান দেওয়া হচ্ছে এই বিপদ অই কারণেই হয়েছে । গ্রামের সবাই যদি প্রতিজ্ঞা করে , বলি প্রথা বন্ধ করবে, তাহলে সবাই সুস্থ হবে । সবাই ঠাকুরের সামনে তাই বললো । আর কিছু করার নেই । বলি বন্ধ হলেই হবে ।অনেক কিশোর কিশোরী ,বুড়ো বুড়ি এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি । গ্রামের বেশির ভাগ লোক পশু বলি চায় না ।কিন্তু অভিশাপের ভয়ে কেউ মুখ খোলে না ।হাসপাতাল থেকে সবাই সুস্থ হয়ে ফিরে এলে দিদি বললেন, এই পোকা টি জগন্নাথ ঠাকুরের মত দেখতে । কিন্তু এটি একটি বিষাক্ত পোকা । গভীর জঙ্গলে ওরা থাকে । রাতে প্রাসাদের আঢাকা থালার মধ্যে যাওয়া আসা করার ফলে বিষাক্ত ফ্লুয়িড খাবারে লেগে যায় । সেই প্রসাদ সকালে খাওয়া হয়,আবার তারপরে বলিপ্রথার পাপের ফল ।এই দুয়ে মিশে আমাদের গ্রামের অনেকেই অসুস্থ ।
বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায় জলের মতো ।দাদা বললেন, মনে রাখতে হবে , আমরা মানুষ ,পশু নই । তাই আমরা নিজেরা বাঁচার পাশাপাশি আর বাকি সবাইকে বাঁচতো দেবো । তবেই আমরা সুন্দর এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারবো। কেতুগ্রাম থানার ভুলকুড়ি গ্রামে সন্ধ্যা ছ'টার পর আর কেউ বাইরে বেরোয় না ।একমাস যাবৎ এই অন্ঞ্চলে ভূতের অত্যাচার খুব বেড়ে গেছে ।
গ্রামের শিক্ষিত ছেলে বাবু ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বললো, জানো দাদা জবা দের দোতলা ঘরে জবা শুয়েছিলো । ঠিক বারোটার সময় জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে জবার মাথার চুল ছিঁড়ে নিয়েছে ।
-----কবে রে বাবু
------ গতকাল রাতে
------এখন কেমন আছে
-----এখনি ডাক্তার খানা নিয়ে যাবে বলছে
আমি কয়েকদিন ধরে এইরকম কথা শুনছি ।ভাবছি কি করা যায় ।আমার বাড়িতেও তো এইরকম আক্রমণ হতে পারে ।
আজকে রাতে রাস্তায় কেউ নেই । আমি দোতলার বারান্দায় রাত বারো টা অবধি জেগে থাকলাম । কিন্তু ,কাকস্য পরিবেদনা । কেউ নেই । একটু ভয় ভয় লাগছে ।তারপর রাত্রি র অপরূপ রূপে মগ্ন হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ।সকাল বেলা পেপার আর চা নিয়ে কোকিলের ডাক শুনছিলাম ।
হঠাৎ মন্ডল পাড়ার স্বদেশ এসে আমেজ টা নষ্ট করে দিলো ।
-----দাদা,কালকে আমাদের পাড়ায় ভূতটা ঘুরছিলো ।প্রায় দশ ফুট লম্বা ,বড়ো হাত আর কালো রঙ ।ভয়ে আমার বাবা অজ্ঞা ন হয়ে গিয়েছিলো ।
____এখন ভালো আছেন ?
_____না না ,এখনও বু বু করছে ।
আমি আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলাম ।কি করা যায়,এই সমস্যা সহজে সমাধান করা খুব কঠিন ।প্রকৃতির নিয়মে আবার রাত হলো ।গ্রামের সহজ সরল মানুষ এই সব বিপদের দিন অসহায় হয়ে যায় ।রাতে শুয়ে চিন্তা করলাম মুস্কিল আসান করার জন্য কিশোর মনোবিজ্ঞানের সুমন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে খবর দিতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে চড়খীর অমল কে ফোন করলাম । আমার মনে আছে অদৃশ্য নাথ সেই ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলো জয়ন্ত দা ও হৈমন্তী দি র জন্য।
অমল ফোন করে সুমন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের আসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলো ।সঙ্গে আসছেন কিশোর মনো বিজ্ঞানের সহ সম্পাদনা সচিব রত্না দিদি । তিনি বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী । আমার একটু সাহস বাড়লো । ওদের সাথে আমার বন্ধু অমল কেও আসতে বললাম ।
সেই রাত কাটলো ভয়ে ভয়ে ।সকালে উঠে শুনলাম ব্রাহ্মণ পাড়ার দীপক বাইরে বসে গান করছিলো আর ভূতে তাকে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছো । শুনে আমার খুব রাগ হলো ।ভাবলাম, দাঁড়া আজকের রাতে তোদের ব্যবস্থা হচ্ছে।
দাদা ও দিদি ঠিক বারোটার মধ্যে অমল কে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এলেন ।তাদের দেখে আমার বুকের ছাতি চল্লিশ ইঞ্চি হয়ে গেলো মনে হচ্ছে।
ঠিক চারটের সময় মঙ্গল চন্ডীর উঠোনে গ্রামবাসীরা হাজির হয়ে গেলো । জয়ন্ত দা বলতে শুরু করলেন, আজ আমরা সবাই রাতে জেগে থাকব । কে বা কারা এই কুকর্ম করছে আমাদের জানা দরকার ।
একজন বলে উঠলেন, ভূতের সঙ্গে লড়াই করে কি পারা যাবে ।
দিদি বললেন, ভূত বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই । তারপর তিনি আরও কিছু কথা বললেন গ্রামবাসীদের সাহসী করার জন্য ।
আবার একজন বললেন, তাহলে আগুন জ্বলে উঠছে কেমন করে ।
দাদা বললেন, এসব কিছু বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যাপার ।আগে ধরা হোক অপরাধী কে তারপর সব বোঝা যাবে ।
এখন রাত দশটা বাজে । গ্রামের সবাই জেগে আছে ।ঠিক রাত বারোটার সময় একটা দশ ফুটের লোক হেঁটে আসছে গ্রামের দিকে । দাদা থানায় ফোন করে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ আনিয়েছেন ।সাধারণ লোকের বুদ্ধির সঙ্গে এখানে ই দাদার পার্থক্য । কখন যে সমস্ত ব্যাবস্থা করে রেখেছেন কেউ জানি না । ভূত কাছাকাছি আসা মাত্র পুলিশ দু রাউন্ড গুলি চালালো ফাঁকা আকাশে । গুলির আওয়াজ শোনা মাত্র ভূত টি ভয়ে মাটিতে পড়ে গেলো । সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সাহসী ছেলেরা বিকট চিৎকার করে ধরে ফেললো ভূত বাবাজিকে । বেচারা তখন জোড়া হাতে ক্ষমা চাইছে ।তাকে বিচারের জন্য ফাঁকা জায়গায় আনা হলো ।সবাই বসে পড়লেন । এবার দাদা বলতে শুরু করলেন,দেখুন সবাই এই চোরটি রণ পা ব্যবহার করেছে লম্বা হওয়ার জন্য । রণ পা টি বাঁশের তৈরী নয় ।একজন বললো,তাহলে ও ছোটো বড় কি করে হতো ।
দিদি বললেন, রণ পা টি বিশেষ ধরণের । এর মাঝে একটি শক্ত স্প্রিং আছে। যার ফলে এ যখন লাফ দি তো তখন এটি ছোটো বড়ো হতো ।
আর একজন বললো, তাহলে মুখ দিয়ে আগুন বেরোতো কি করে।
দিদি বললেন, এটা তো সহজ ব্যাপার । সার্কাসে আপনারা দেখে থাকবেন মুখের মধ্যে পেট্রোলিয়াম বা কেরোসিন জাতীয় দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে এরা মানুষকে অবাক করে দেন । এই চোরটিও তাই করেছে ।
দাদা এবার চোরটিকে ধমক দিয়ে বললেন,তুমি জঘন্য অপরাধ কেন করছো জবাব দাও ।এবার চোরটি উঠে জোড় হাতে বললো,আমরা মাদক দ্রব্য চোরাপথে চালান করি । তাই ভূতের ভয় দেখিয়ে আমরা মানুষকে বাড়িতে ঢুকিয়ে রাখি ।এর ফলে আমাদের চোরা চালানে সুবিধা হয় ।তারপর থেকে আর ভূূতের উপদ্রব হয় নি।
রবিবাবুর বিবাহ ও তার জীবনের কথা
রবিবাবু স্কুলের কাছে বিবেকানন্দ আশ্রমে যেতেন মাঝে মাঝে।সেখানে শুনতেন মহারাজের কথা।তিনি বলতেন,রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন "তোদের চৈতন্য হোক" । আবার শ্রীচৈতন্য দেব ভক্ত দের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নিজের ভক্তির অর্ঘ্য শ্রীহরির চরণে নিবেদন করতে বলেছেন । সহজ পথ তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন । তাঁদের দেখানো পথে যেতে পারলেই মন নিয়ন্ত্রিত হয়ে মৃত্যু ভয় দূর হয় ।জয় শ্রী গৌরাঙ্গ বলে ঝাঁপিয়ে পর মন , বাড়ির কাছেই পাবে শ্রী বৃন্দাবন । তবু বিষয় বিষে জর্জরিত মানুষ পার্থিব সুখ কে আঁকড়ে বাঁচতে চায় ।
মানুষের মন ও মৃত্যুচেতনা বিষয়ে অনেক বিচিত্র ধারণা প্রাচীন কাল থেকে মায়ার চাদরে আচ্ছাদিত ।আইনস্টাইন থ্রি ডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশনে সময় যোগ করেছিলেন ।আমার মতো অর্বাচীন মন নিয়ে আপনাদের কতটুকু ধারণা দিতে পারি বন্ধু । তবু আমার মনে হয় ফাইভ ডাইমেনশনে মন যুক্ত হবে ।শিশুর সারল্যে মন যখন কোনো কিছু ভালোবাসে সেই ভালোবাসা স্থায়ী হয়ে মনের মণিকোঠায় আজীবন আনন্দের দামামা বাজিয়ে চলে । সাধক মানুষ সিদ্ধিলাভের পরে জীবনের পার্থিব চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে থাকে । কবিতা গান নাটক উপন্যাস সবকিছু এই বিচিত্র মনের সৃষ্টি ।বন পুড়লে দাবানল সৃষ্টি করে আর মন পুড়ে সৃষ্টি করে গান কবিতা ছবি । একটা কবিতা বা গান সুর তোলে মনের মণিকোঠায় । সকল দুঃখ বেদনা সারিয়ে তুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায় ।মন আজীবন মানুষের অভিভাবক হয়ে নির্দেশ দেয় সু পথে চলার ।
মন বলবেই মৃত্যু কে সহজেই স্বীকার করার কথা । মৃত্যু কে রোধ করার চেষ্টা করলে জীবনের গতিপথ যে বন্ধ হয়ে যাবে ।মৃত্যু ই তো জীবনের স্বাদ অমৃতময় করে তোলে ।অতএব সুখ দুঃখ আলো অন্ধকার সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হোক ।
মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব সন্তান হারা মাতাকে মৃত্যু প্রবেশ করেনি এমন বাড়ি থেকে একমুঠো সরিষা আনতে বলেছিলেন ।তিনি কি আনতে পেরেছিলেন । তাই বন্ধুদের কবি অসীম সরকারের একটা গানের লাইন শোনাই, " ও মন সওদাগর বিদেশে বাণিজ্যে এসে কেন বাঁধলি বসতঘর ;দেশের মানুষ দেশেই ফিরে চল"...আপন দেশ শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পিত হোক আমাদের জীবন । শ্রীহরি আমার অন্তরে চৈতন্যের জাগরণ করে দাও, আমার অহংকার কেড়ে নাও ,আমাকে তোমার চরণে ঠাঁই দাও, এই হোক আমাদের প্রার্থনা ।
রবিবাবু মন দিয়ে কথাগুলো শোনেন।তার খুব ভাল লাগে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে। সন্ধে হলে তিনি বাড়ি ফিরলেন,দেখলেন কয়েকজন অপরিচিত লোক এসেছেন।রবিবাবুর বাবা বললেন,তাহলে আমরা আগামীকাল মেয়ে দেখে আসব।ফাইনাল কথা কালকেই বলব।
রবিবাবুও সম্মত হলেন।মেয়ে পছন্দ হলে তিনমাস পরে বিয়ে হয়ে গেল।এখন রবিবাবু বিবাহিত।
রবিবাবুর স্ত্রী র নাম আলো।আলো পাশের বাড়ির বৌটার সঙ্গে মেশে।তার বরের নাম অভয়।
অনেকগুলো ছেলে মেয়ে জন্মের পর মরে যাওয়ায় অভয় এবারের ছেলের নাম রাখলো গু,য়ে। ভালো নাম রাকবো না রে। আবার যদি মরে যায়। পরের বছর যে হবে তার নাম রাকবো আকু। বললো,অভয়। গ্রামের পুরোহিত বললো,ঠিক করেছো। এইবার তোমার ছেলে,মেয়ে বাঁচবে।
ছেলে দুটো বাঁচার পরে আরও দুটো মেয়ে হলো। আর সন্তান নিলো না অভয়। অনেকে বললো,সংসার ছোটো রাকো,তাহলে অভাব হবে না। অভয় বললো,আমার বন্ধু রামুর তো নয়টা ছেলে আর দুটো মেয়ে। আছে তো দু বিঘে জমি। ওরা বুঝলো,তর্ক করে লাভ নেই। যে বোঝার নিজে থেকেই বোঝে।
তারপর বড় হয়ে স্কুলে ভরতি হওয়ার সময় আকুর নাম হলো সমর আর গুয়ের নাম হলো অমর। আর ভয় নেই। শিব ঠাকুরের কাছে মানত করে অভয়,ছেলেদের বললো,বছরে একবার গাজনের সময় ভক্ত হবি। তাহলে সব বিপদ কেটে যাবে। অভয় ভাবে,মেয়েরা তো তাড়াতাড়ি বাড়ে। বিয়ে দিতে হবে। অভাবের জন্য ওরা বেশিদূর পড়তে পারলো না। সমর মুদিখানার দোকানে কাজ নিলো। আর মেয়েরা বাড়ির কাজ করে। অমর পড়াশোনায় ভালো বলে স্কুল ছড়লো না। হেড মাষ্টার নিজে খরচ দিয়ে অমরকে পড়াতেন স্কুলে। তখনকার দিনে স্কুলে পড়তে গেলে টাকা,পয়সা লাগতো।কাদা, মাটির রাস্তা গ্রামে। বর্ষাকালে মুদিখানার মাল রেলস্টেশন থেকে সমর মাথায় করে নিয়ে আসতো। নুনের বস্তাও মাথায় করে আনতো। লোকে বলতো অভয়কে,অত খাটাস না ছেলেটাকে। চোখে, কোমরে রোগ ধরে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।
মেয়ে দুটোর একই দিনে বিয়ের ব্যবস্থা করলো অভয়। বড়ো মেয়ের বয়স সতেরো। আর ছোটো মেয়ের বয়স ষোলো। বেশ ধুমধাম হলো। কলা পাতা দিয়ে গেট বানানো হলো। সতরঞ্জি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। গরীব মানুষ। তবু বাড়ির সকলে খুব আনন্দ করলো।বিয়ের দিনে বর পথে দুর্ঘটনায় মারা গেল। কপাল পুড়ল মেয়েটার।
তারপর চলে এল জগদ্ধাত্রী পুজো।এই গ্রামে ধূমধাম করে মশাল জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের পুজো হয়। গ্রামের বাজারে বহু বছর যাবৎ এই পুজো হয়ে আসছে। পাটকাঠির মশাল জ্বালিয়ে এই পুজো মহা সমারোহে পালন করা হয়। কথিত আছে জ্ঞানের আলো এই দেবি জগতে ছড়িয়ে দেন। তাই আলোময় মশাল জ্বালিয়ে দেবির পুজো করা হয়। ভিন্ন মতও অনেক আছে।
তবে মতবাদের ককচকচানির উর্ধ্বে উঠে সকল গ্রামবাসী এক হয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হন এই কটা দিন।পাটকাঠির বোঝা বেঁধে বড় বড় মশাল তৈরি হয়। মশালে আগুন ধরিয়ে ঢাক ঢোলের তালে তালে নাচতে থাকে ভক্তের দল। চারদিকে আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে পুজোমন্ডপ। মশাল জ্বালিয়ে গ্রাম ঘোরে প্রতিমাসহ মশালবাহির দল। বড় সুন্দর এই দৃশ্য। সব মানুষ ভেদাভেদ ভুলে মেতে যান এই উৎসবে।আর কোথাও এই পুজো আছে কি না জানা নেই রবিবাবুর।তবে তিনি বলেন,এই পুজোয় গ্রামবাসীর আনন্দ তাকেও আনন্দিত করে তোলে।
লেখক বিজয়ের কিশোর জীবনের কথা
বিজয় এম এ, বি এড পাশ।বিজয় প্রাইভেট স্কুলে পড়ায় আর টিউশন পড়ায় কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের ।তাদের সে বলে তার আত্মকথা, নদীর ধার দিয়ে নিত্য আমার আনাগোনা । গ্রীষ্মে দেখি শুকনো বালির বৈশাখী কালো রূপে আলো ঘেরা অভয় বাণী ।বর্ষায় পরিপূর্ণ গর্ভবতী নারীরূপ । এই রূপে জলবতী নদীতে অতি বড় সাঁতারু ভুলে যায় কৌশল । আমি তখন নদীর বুকে দুধসাদা ফেনা হয়ে ভাসতে ভাসতে চলি বাক্যহারা হয়ে ।
একজন বলে ওঠে, স্যার,এবার শরতে কাশ ফুলের কারসাজি । তার মাথা দোলানো দেখে আমিও দুর্গা পুজোর ঢাকী হয়ে যাই । আমার অন্তর নাচতে থাকে তালে তালে । মা তুই আসবি কবে আর, নতুন জামায় নাচে মন সবার ।
বিজয় বলে, বাহ, ভালো বলেছিস। এবার শোন, নদী এরপরে হেমন্তের বুকে ছবি এঁকে এগিয়ে যায় শীত ঋতুর আহ্বানে । লোটা কম্বল বগলে আমি রাজস্থানী সাজি । কখনও ধূতি পাঞ্জাবি পরিহিত শাল জড়ানো খাঁটি বাঙালি । মাঝে মাঝে কোট প্যান্ট পরিহিত বিদেশী সাহেবের সুন্দর সাজ । আমি সারা পৃথিবীর সাজে সজ্জিত হতে চাই শীতের আদরে ।শীতল আড়মোড়া ভাঙতেই বসন্তের বাসন্তী রঙের তালে তালে আমি রঙের ফেরিওয়ালা হয়ে যাই । সকলের অন্তরের গোপন রঙ ছড়িয়ে দেয় প্রকৃতি । এই সময়ে আমার রাধাভাব ছড়িয়ে পড়ে স্বচ্ছ অজয়ের মদনমোহনের রূপে ।তখন আমার সমস্ত শরীর মন ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মনোদেবতার মহান চরণে .।..
বিজয় বলে চলে গল্পের মত জীবনের কথা, দূর থেকে ভেসে আসছে ভাদুগানের সুর । ছুটে গিয়ে দেখলাম জ্যোৎস্না রঙের শাড়ি জড়ানো বালিকা ভাদু বসে আছে । আর একটি পুরুষ মেয়ের সাজে ঘুরে ঘুরে কোমর নাচিয়ে গান করছে , "ভাদু আমার ছোটো ছেলে কাপড়় পর়তে জানে না" ।অবাক হয়ে গিলে যায় এই নাচের দৃশ্য অসংখ্য অপু দুর্গার বিস্মিত চোখ । ঝাপানের সময় ঝাঁপি থেকে ফণা তোলা সাপ নাচিয়ে যায় চিরকালের চেনা সুরে ঝাপান দাদা ।ঝাপান দাদা ঝাপান এলেই গান ধরতো,"আলে আলে যায় রে কেলে , জলকে করে ঘোলা । কি ক্ষণে কালিনাগ বাসরেতে ঢোকে রে, লখিন্দরের বিধি হলো বাম " । আর একজন ছাত্র বলে,গ্রামের পুরোনো পুজোবাড়ি গাজনের সময় নতুন সাজে সজ্জিত হতো । বাবা শিবের ভক্তরা ভক্তি ভরে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে দোল পুজো বাড়িতে নামাতেন । অসংখ্য লোকের নতুন জামা কাপড়ের গন্ধে মৌ মৌ করে উঠতো সারা বাড়ি । তারপর পুজো হওয়ার পরে দোল চলে যেতো উদ্ধারণপুরের গঙ্গা য় স্নানের উদ্দেশ্যে । কিন্তু আমার মন ফাঁকা হয়ে একা হয়ে পড়তো । এই তো কিছুক্ষণ আগেই ছিলো আনন্দ ঘ্রাণ । তবু দোল চলে গেলেই মন খারাপের দল পালা করে শুনিয়ে যেতো অন্যমনস্ক কবির ট্রাম চাপা পড়ার করুণ কাহিনী । ঠিক এই সময়ে কানে ভাসতো অভুক্ত জনের কান্নার সুর । আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি বারংবার, সকলের অনুভূতি কি আমার মতো হয় ?
একজন ছাত্রী বলে,স্যার রাতে শোয়ার পরে বোলান দলের নুপুরের ঝুম ঝুম শব্দ কানে বাজতো বেশ কিছুদিন ধরে । ফাল্গুনে হোলিকার কুশ পুত্তলিকায় আগুন ধরিয়ে কি নাচ । নাচতে নাচতেই সবাই সমস্বরে বলতাম, ধূ ধূ নেড়া পোড়া, হোলিকার দেহ পোড়া ।
বিজয় বললেন,ঠিক। অশুভ শক্তিকে পুড়িয়ে শুভ শক্তির উন্মেষ । পরের দিনে রং আর আবিরে ভরে যেত আকাশের নরম গা । বাতাসের অদৃশ্য গায়ে আবিরের আনাগোনা । সে এক অনির্বচনিয় আনন্দের প্রকাশে রাধা কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের আকুতি ।আশ্বিনের আকাশে বাতাসে বেলুনের অনিল পাঠকের রঙের খেলা । শিল্পী একমাটি, দুমাটি করে শেষে চোখ আঁকতেন পর্দার আড়ালে । আগে থেকে চোখ দেখতে নেই । আর আমার চোখ দেখার জন্য চাতুর্যের সীমা থাকতো না ।বিজয় বলে,পাঠক মশাইয়ের ফাই ফরমাশ খেটে সবার অলক্ষ্যে চোখ দেখে নিতাম একবার । সেই চোখ আজও আমার মনে এঁকে যায় জলছবি । কি যেন বলেছিলো সেই চোখ । আশ্বিন এলেই আমি প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখে বেড়াই মায়ের চোখ দেখার বাসনায় । ছোটোবেলার দেখা চোখ কোথায় কোন গভীর জলে ডুব দিয়েছে কে জানে ।দরজা পুকুরের সবুজ সর সরিয়ে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে খুঁজে চলে আজও আমার মায়ের চোখ ।হাঁসগুলিও আমাকে সান্ত্বনা জুগিয়ে চলে জলে ডুবে ডুবে । হয়তো আমার জন্য ই ওরা অভয় নাচ দেখিয়ে চলে মনদেবতার ঈশারায় । কাশের কুঁড়ি রসদ মজুদ করছে ফোটা ফুলের সৌরভ বিতরণের । এরপরেই শুরু আনন্দে মাথা দোলানোর উৎসব । মননদীর গভীরে প্রোথিত তার আগমনী সংগীত । হাত নেড়ে বলছে, আসছে আসছে । দেবী কাশ রঙের সংকেতে তাঁর আগমনী বার্তা পাঠান যুগ যুগ ধরে ।
বিজয় বলে,আমাদের শোভন কাকা কাশ ফুল দেখলেই কারণে অকারণে গলা ছেড়ে গান গাইতেন । সেই মধুর সুরেই শোভন কাকা কাশ ফুলের শোভা বাড়িয়ে সকলের মনের সংকীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে দিতেন ।আমরা সকলেই প্রিয়জন মরে গেলে দুঃখ পাই । কিন্তু নিজের মরণ বুঝতে পারলেও দুঃখ প্রকাশের সুযোগ পাই কি ? সেই শোভন কাকা গানে গানে কিন্তু নিজের মরণের আগেই পরিণতির কথা শোনাতেন । অঘোষিত উঁচু পর্বে নাম খোদাই হয়ে গিয়েছিলো তার । মৃৎশিল্পেও তার দক্ষতা ছিলো দেখার মতো । প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব তার উপরেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতো পূজা কমিটি ।শোভন কাকা এলেই আমাদের পুজোর গন্ধ গ্রাম জুড়ে গানের সুরের সঙ্গে ভেসে বেড়াতো । তিনি ছিলেন প্রাণজুড়ানো শান্ত পালক নরম আনন্দের ফেরিওয়ালা ।তিনি মাটি হাতে মায়ের সঙ্গে মন মাতানো মন্দাক্রান্তা গাইতেন ।তার চলন বলন দেখে ভালোবেসে তাকে শোভনানন্দ বলতেন তথাকথিত গুরুবৃন্দ । তারপর ছাত্র ছাত্রী রা চলে গেল।এবার ঘরে ঢুকলো বিজয়ের বন্ধু রমেন। রমেন চা বিস্কুট খায় আর বিজয় বলে চলে গল্পকথা,তার জীবনের কথা।শিবপদ বলে, তিরিশ বছর পরে আমার মনে পড়ছে খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল ভেদ করে সে এসেছিলো জ্যোৎস্না রঙের ফ্রকে । হাত দিতেই একরাশ মুক্ত ঝরে পরে ছিলো তার রক্ত রাঙা দেহ মাটিতে ।
আমাকে বলেছিলো সে, _পলাশ তোমার পরশ থেকে আমাকে ছিন্ন কোরোনা, আমি মরে যাবো ।
আমি বলেছিলাম আবেগে, __এসো আমার আনন্দ জীবন, আমার করবী ।
রমেন বলে,কে যে মরে আর হা পিত্যেশ করে বোঝা যায় না এই পৃথিবীতে ।
বিজয় বলে,ঠিক বলেছিস।তারপর সেদিন খড়ের চাল ফুঁড়ে জ্যোৎস্না আমার উপর উঠে বিপরীত ক্রিয়াতে হেসেছিলো নেশাতে । আমি শুধু অবাক হয়েছিলাম প্রথম সমুদ্র দেখার মতো ।তারপর জয় পরাজয়, উত্থান পতনের ঢেউ আছাড় মেরেছে জীবন সৈকতে । কোনোদিন ভেঙ্গে পরে নি মন । হঠাৎ পাওয়া জ্যোৎস্না বিয়ে করে আমেরিকা চলে গেলো । না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বয়ে বেড়ালাম তিরিশ বছর ।এখন প্রকৃতির সঙ্গে ভাব জমিয়েছি খুব ।
রমেন বলে, আমি কাউকে ভালোবাসি না। আমার এক স্প্যানিয়াল কুকুর বন্ধুকে নিয়ে ঘর করি । কোনো কথা নেই , কোনো ঝগড়া নেই । ভালোবাসার চোখে দেখি একে অপরকে ।আপন মনে থাকতে থাকতে মনে চলে আসে মায়ের কথা । আমার মা আর নেই।
বিজয় বলে,খুব কষ্ট মা না থাকলে। তারপর শোন রমেন আমার কাহিনী। বৃষ্টির এক দুপুরে আমার প্রেমিকার চিঠির কথা আজও মনে পড়ে । প্রেমিকা লিখেছিলো ,ধনী পিতার একমাত্র সুন্দর ছেলেকে পরিবার যেমন নজর বন্দী করে রাখে পাছে ছেলে ভালোবাসা র খপ্পরে পরে পর হয়ে না যায় । ঠিক তেমনিভাবেই রেনকোট, ছাতার আড়াল করে আমরা নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করেও বৃষ্টির ভালোবাসা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি না ।বৃষ্টি বলে সুন্দরী যেমন একমাত্র সুন্দর ছেলেকে পরিবারের নজর থেকে নিজের করে নেয় ,ঠিক একইভাবে বৃষ্টি আমাদের. একমাত্র সুন্দর দেহ জামার কলারের ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে অন্দরমহলে । তারপর হাঁটা পথে চলার রাস্তায় জল পরম মমতায় পায়ে জলের শে কল পরিয়ে রাখতে চায় । বৃষ্টির সময় চোখে মুখে জল আদরের প্রলেপ লাগায় । ঠোঁট চুম্বন করে শীতল স্পর্শকাতর জল । তার আদরে প্রেমজ্বরে পড়তে হয় মাঝে মাঝে । আমি ভালোবেসে তাকে বলছি, তুমি আমার জ্বরের মাঝে ঝরঝর ঝাঁপিয়ে পড়ো । আমিও বৃষ্টি হয়ে যাই ।তারপর জানতে চেয়েছিলো কেমন হয়েছে তার চিঠি । তখনও আমি কিছুই বলতে পারি নি ।রমেন বলে,তুই খুব বোকা চিরকাল।তুই ও জ্যোৎস্না যে গ্রামে ভালোবাসা র বয়সটা কাটিয়েছি তার কথা আজ মনে সবুজ সর ফেলছে । শুধু মনে পড়ছে,আমার স্বপ্নের সুন্দর গ্রামের রাস্তা বাস থেকে নেমেই লাল মোড়াম দিয়ে শুরু ।দুদিকে বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস রাস্তায় পরম আদরে ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে । কত রকমের পাখি স্বাগত জানাচ্ছে পথিককে । রাস্তা পারাপারে ব্যস্ত বেজি , শেয়াল আরও অনেক রকমের জীবজন্তু।.চেনা আত্মীয় র মতো অতিথির কাছাকাছি তাদের আনাগোনা । হাঁটতে হাঁটতে এসে যাবে কদতলার মাঠ। তারপর গোকুল পুকুরের জমি, চাঁপপুকুর, সর্দার পাড়া,বেনেপুকুর । ক্রমশ চলে আসবে নতুন পুকুর, ডেঙাপাড়া ,পুজোবাড়ি, দরজা ঘাট, কালী তলা । এখানেই আমার চোদ্দপুরুষের ভিটে । তারপর ষষ্টিতলা ,মঙ্গল চন্ডীর উঠোন , দুর্গা তলার নাটমন্দির । এদিকে গোপালের মন্দির, মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, তামালের দোকান, সুব্রতর দোকান পেরিয়ে ষষ্ঠী গোরে, রাধা মাধবতলা । গোস্বামী বাড়ি পেরিয়ে মন্ডপতলা । এই মন্ডপতলায় ছোটোবেলায় গাজনের সময় রাক্ষস দেখে ভয় পেয়েছিলাম । সেইসব হারিয়ে যাওয়া রাক্ষস আর ফিরে আসবে না ।কেঁয়াপুকুর,কেষ্টপুকুরের পাড় । তারপর বাজারে পাড়া ,শিব তলা,পেরিয়ে নাপিত পাড়া । এখন নাপিত পাড়াগুলো সেলুনে চলে গেছে । সাতন জেঠু দুপায়ের ফাঁকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরতেন মাথা ,তারপর চুল বাটি ছাঁটে ফাঁকা । কত আদর আর আব্দারে ভরা থাকতো চুল কাটার বেলা ।এখন সব কিছুই যান্ত্রিক । মাঝে মাঝে কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়েকে রোবোট মনে হয় । মুখে হাসি নেই । বেশ জেঠু জেঠু ভাব ।সর্বশেষে বড়পুকুর পেরিয়ে পাকা রাস্তা ধরে ভুলকুড়ি । আর মন্ডপতলার পর রাস্তা চলে গেছে খাঁ পাড়া , কাঁদরের ধার ধরে রায়পাড়া । সেখানেও আছে চন্ডীমন্ডপতলা , কলা বা গান, দুর্গা তলার নাটমন্দির সব কিছুই । পুজোবাড়িতে গোলা পায়রা দেখতে গেলে হাততালি দিই ।শয়ে শয়ে দেশি পায়রার দল উড়ে এসে উৎসব লাগিয়ে দেয়। পুরোনো দিনের বাড়িগুলি এই গ্রামের প্রাণ ।এই গ্রামে ই আমার সবকিছু , আমার ভালোবাসা, আমার গান ।
বিজয় বলে,শোন, চারদিন আগে, জ্যোৎস্না খোঁজ নিয়ে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে ।এসেই নিজের ঘরের মতো এলোমেলো জীবন সাজাতে চাইছে । আর কথা বলে চলেছো অনবরত । ভালো করে তৈরি হয়ে এসে বিছানায় বসে শরীর টা এলিয়ে দিলো । তারপর শুরু করলো, মনে আছে তোমার সব ঘটনা । জানো আমি সুখী নই । কথাটা শুনে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো । আবার আমার দুর্বল জায়গা জাগিয়ে তোলার জন্য পুরোনো কথা শুরু করলো ।ও জানে না আমি স্মৃতি জড়িয়ে ধরে বেঁচে আছি ।আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনাতে লাগলাম পুরোনো বাল্য ভারত, তুমি শোনো জ্যোৎস্না,ছোটোবেলার সরস্বতী পুজো বেশ ঘটা করেই ঘটতো । পুজোর দুদিন আগে থেকেই প্রতিমার বায়নাস্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে আসা হত শিল্পী কে ।তারপর প্যান্ডেলের জোগাড় । বন্ধুদের সকলের বাড়ি থেকে মা ও দিদিদের কাপড় জোগাড় করে বানানো হত স্বপ্নের সুন্দর প্যান্ডেল । তার একপাশে
রমেন বলে,দারুণ কথা বলিস তুই।তুই একদিন বিখ্যাত লেখক হবি দেখিস।আমাদের ঘর বানানো হত আমাদের বসার ঘর । পুজোর আগের রাত আমরা জেগেই কাটাতাম কয়েকজন বন্ধু মিলে । কোনো কাজ বাকি নেই তবু সবাই খুব ব্যস্ত । একটা ভীষণ সিরিয়াস মনোভাব । তারপর সেই ছোট্ট কাপড়ের পাখির নিড়ে কে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা কেউ জানতে পারতাম না । মশার কামড়ও সেই নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভাঙাতে পাড়তো না ।তবু সকালে উঠেই মচকানো বাঁশের মত ব্যস্ততার আনন্দ । মা বাবার সাবধান বাণী ,ডেঙ্গু জ্বরের ভয় কোনো কিছুই আমাদের আনন্দের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি । হড়কা বানে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে , আমাদের আনন্দ ঠিক আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত মহানন্দের জগতে । এরপরে সকাল সকাল স্নান সেরে ফলমূল কাটতে বসে পড়তাম বাড়ি থেকে নিরামিষ বঁটি এনে । পুরোহিত এসে পড়তেন ইতিমধ্যে । মন্ত্র তন্ত্র কিছুই বুঝতাম না । শুধুমাত্র বুঝতাম মায়ের কাছে চাইলে মা না করতে পারেন না । পুষ্পাঞ্জলি দিতাম একসঙ্গে সবাই । জোরে জোরে পুরোহিত মন্ত্র বলতেন । মন্ত্র বলা ফাঁকি দিয়ে ফুল দিতাম মায়ের চরণে ভক্তিভরে । তারপরে প্রসাদ বিতরণের চরম পুলকে আমরা বন্ধুরা সকলেই পুলকিত হতাম । প্রসাদ খেতাম সকলকে বিতরণ করার পরে ।আমাদের সবার প্রসাদে ভক্তি বেশি হয়ে যেত ,ফলে দুপুরে বাড়িতে ভাত খেতাম কম । সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ ,ধূপ জ্বেলে প্যান্ডেলের ঘরে সময় কাটাতাম । পরের দিন দধিকর্মা । খই আর দই । পুজো হওয়ার অপেক্ষায় জিভে জল । তারপর প্রসাদ বিতরণ করে নিজেদের পেটপুজো সাঙ্গ হত সাড়ম্বরে ।
তারপর বিজয় বলে,এরপরের দৃশ্য প্রতিমা বিসর্জন । কাছেই একটা পুকুর । রাত হলে সিদ্ধিলাভে(দামীটা না) আনন্দিত হয়ে নাচ তে নাচতে অবশেষে শেষের বাজনা বেজে উঠতো । মা তুই থাকবি কতক্ষণ, তুই যাবি বিসর্জন ।তার সাথে আমাদের মনটাও বিসর্জনের বাজনা শুনতো পড়ার ঘরে বেশ কিছুদিন ধরে...কথা শুনতে শুনতে জ্যোৎস্না আমাকে জড়িয়ে ধরেছে । আমার প্রবল কামনাকে কামড়ে ধরে নীলকন্ঠ হয়ে আছি । জ্যোৎস্না বললো, জানো বিদেশে এটা কোনো ব্যাপার নয় । এসো আমরা এক হই পরম সুখে । আমি হাত ছাড়িয়ে বাইরে এলাম ।জ্যোৎস্না কি ভুলে গেছে মনে ভাসা সবুজ সর নিয়ে ,দুঃখ কে জয় করার মানসিকতায় এক ভারতবর্ষীয় যাপনে আমি ডুব দিয়েছি জীবন সমুদ্রে....। তারপর কেটে গেছে অনেকটা সময়। আমি একা থাকতেই ভালোবাসি। মাছ ছিপ দিয়ে ধরতে ভালোবাসি।
বিজয় বলে,এবার শোন ভূতের গল্প।
রমেন বলে,ছেলেমানুষী শুধু তোর। আবার ভূত দেখার বাল্যসখও আছে। অনেকে হয়তো আড়ালে হাসবেন।
রবিবাবুর শহরে আগমন ও তার বাকি জীবনের কথা
রবিবাবু গ্রামের বাড়ি থেকে শহরে চলে এলেন সাংসারিক বিভিন্ন চাপে।তখন তার বড় ছেলে সেভেনে পড়ে আর ছোটছেলে পড়ে ক্লাস ফোরে।শহরে এসে বাসাবাড়ি ভাড়া করলেন।স্ত্রী আলো খুব খুশি।আলাদা সংসার তিনি মন দিয়ে সাজালেন দশবছর পরে রবিবাবু শহরে জায়গা কিনে বাড়ি করলেন।ছেলেরা তখন লাভপুর কলেজে বড়ছেলে হোষ্টেলে থাকে আর ছোটছেলে কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।
তারপর ছেলেরা দুজনেই চাকরি পেল। রবিবাবু রিটায়ার্ড করলেন স্কুল থেকে।আলো দেবি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। রবিবাবু আলোকে দেখেন আর চুপ করে থাকেন।রবিবাবু চুপ মেরে গেলেন।ডাক্তার বলছে, মনরোগ। বাড়ির বড় ছেলে বাবাকে গল্পের বই কিনে দেন নিয়মিত।ছোটোছেলে গানের ক্যাসেট এনে দিলো। কিন্তু রবিবাবুর কোনো পরিবর্তন নেই। গল্পের বই পড়েন না। গান শোনেন না। অথচ এই রবিবাবু চিত্তরঞ্জনে একটা উচ্চ বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি জীবন তার। এই সময়ে তিনি স্কুলে যেতেন সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে। নিজের হাতে রান্না করে খেতে ভালোবাসতেন। ভোটের কাজে তিনি ছিলেন বিজ্ঞ। সকলে তার কাছেই পরামর্শ নিতে আসতেন। মহুকুমার মধ্যে তার মত গণিতজ্ঞ ছিলো না বললেই চলে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করতো। আর বিস্মিত হতো তার কর্মজীবনের সাফল্য দেখে।
একদিন বাড়িতে তার বড় ছেলে বললো, বাবা আজ আমরা বিরিয়ানী খাবো। তুমি রান্না করো। রবিবাবু বাজার থেকে সমস্ত কিছু জোগাড় করে এনে রান্না করে পরিবারের সকলকে বিরিয়ানী খাওয়ালেন।তিনি ছেলেদেরকে বলতেন, রান্না করা শিখে রাখবি। আগামী দিনে রান্নার লোক পাবি না। এখন হোম ডেলিভারির যুগ। ফলে পেটের সমস্যা বাড়বে। রান্না করা শিখতে পারলে খেতে পাবি নিজের মত। তা না হলে যা জুটবে তাই খেতে হবে। ছেলেরা বাবার কথামত রান্না করা শিখেছে।রবিবাবু সফলভাবে চাকরি জীবন সমাপ্ত করে যেদিন বাড়িতে এলেন বিরাট টাটা সুমো গাড়িতে চেপে,সেদিন তার উপহার রাখার জায়গা ছিলো না। বেছে বেছে তিনি একটা বিভূতিভূষণের বই রেখে দিয়েছিলেন যত্ন করে।
তার কিছুদিনের মধ্যে একটা স্কুলের পার্ট টাইম টিচারের পদে যোগদানের জন্য অনুরোধ এলো। তারা বললেন,আপনি এই এলাকার অঙ্কের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আপনি আসুন। অনেকে উপকৃত হবে। সাম্মানিক বেশ ভালো।
রবিবাবু বললেন, এত দিন তো এইসব করেই কাটালাম। এখন বড়ছেলে শিক্ষক হয়েছে। আর আমি শিক্ষকতা করবো না। ছেলেদের বারণ আছে।
এখন রবিবাবুর বড় ছেলে রতন ভাবেন , বাবা চাকরিটা করলে বোধহয় ভালো থাকতেন। চলাফেরা হতো। শরীর ভালো থাকতো।
কিন্তু তা তো হোলো না। বাবা এখন চুপচাপ থাকেন। কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। মন গুমরে আজ তার শরীরটা পাটকাঠির মত হয়েছে।
তারপর বিপদ তো একা আসে না। সুখের সংসারে অভিশাপ হয়ে প্রবেশ করলো কর্কট রোগ। রতনের মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়লো। রবিবাবু সেদিন স্ত্রীকে বলে ফেললে, আর নয়। বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।
স্ত্রী আলো সব জেনে শুনেও রবিবাবুকে ধমক দিলেন, ছেলেরা থাকলো। তোমাকে দেখতে হবে। আমি তো এখন দুদিনের অতিথি।
রবিবাবু ভাবলেন, একটু কাঁদতে পারলে ভালো হতো। কিন্ত ছেলে বৌমা, নাতি নাতনিরা আছে। তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই কান্নাকে ব্যাথার বিপুল পাথরে চাপা দিয়ে রাখলেন।
রবিবাবুর স্ত্রী আলো ভাবেন, এই তো কয়েকদিন আগে কলেজে রবির সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দেখাতেই ভালোলাগা। আর এই ভালোলাগা টেনে নিয়ে গেছিলো তাদের কলকাতা চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া,বইমেলা, মিনার্ভা, কফি হাউস। তাদের দুজনের কবিতার বই আছে। কত আকুতি মেশানো প্রেমের কবিতা। তখন কি আর মনে ছিলো কর্কট রোগে কবিতা আবার নতুন করে জন্ম দেবে।
আজ আলো খোলা চুলে ছাদে গিয়ে রোদে বসে খাতা কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসেছে। রবিবাবু আড়াল থেকে দেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপন মনে বলে উঠলো, আমি যেন তোমার আগে মরতে পারি রত্না। তোমার কবিতা শোনার পরে তৃপ্ত হৃদয়ে আমি মরতে চাই।
নিচে বড়ছেলের চিৎকার শোনা গেলো, মা গো তুমি কোথায়? একবার নিচে এসো। এখনি আমরা কলকাতা নার্সিং হোমে যাবো। আজ ফার্স্ট কেমো নেওয়ার দিন.।তারপর চলল,বিরাট ল
আলো দেবি মারা গেলেন। রবিবাবু আলোছাড়া বাঁচতে চান না।
একদিন তিনিও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।
প্রবাহ চলছে।বড়ছেলে ও ছোটছেলের বিয়ে হল।তাদের পুত্র, কন্যা হল।আবার শুরু হল নব প্রজন্মের নবপ্রবাহ।
লেখক বিজয়ের জীবনপ্রবাহ ও সন্তানলাভ
বিজয় লেখক।চাকরী করে একটা প্রাইভেট ফার্মে। যখনই তার লেখা কোনো ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় সে রেলওয়ে স্টেশনের স্টলে গিয়ে ম্যাগাজিনটি কিনে বাড়ি ফেরে।কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনে ঢুৃকতে গেলে প্ল্যাটফরম টিকিট কেটে ঢুকতে হয়।এখন দশ টাকা লাগে একটা প্ল্যাটফরম টিকিটে।খুব গায়ে লাগে বিজয়ের।কিন্তু কিছু করার নেই। টিকিট না থাকলে আবার টিকিট চেকার ফাইন করতে পারেন। অতএব টিকিট নিয়ে স্টেশনে ঢোকাই উচিত বলে মনে করলো বিজয়।আজ থার্ড আই পত্রিকায় বিজয়ের একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে।খুব আনন্দিত হয়ে সে তার বন্ধু সুমনকে বললো,তুই একটু দাঁড়া, আমি প্ল্যাটফরম টিকিট কেটে বইটা নিয়ে আসি।
শুনে সুমন বললো,আরে প্ল্যাটফরম টিকিটের দাম দশটাকা। তুই দাঁইহাটের টিকিট নিলে পাঁচ টাকায় পাবি। একটা টিকিট থাকলেই হলো।
বিজয় বললো,এটা তো জানা ছিলো না। তাহলে এত দিন ধরে আমার অনেক টাকা সেভ হতো।
ঠিক আছে তাই হবে।তোকে অনেক ধন্যবাদ।
----বন্ধুকে, শালা ধন্যবাদ জানানোর কি আছে?যা, তাড়াতাড়ি যা।একসঙ্গে বাড়ি যাবো।
তারপর বিজয় একটা দাঁইহাটের টিকিট কেটে ম্যাগাজিন কিনে মহানন্দে বাড়ি চলে এলো। বন্ধুও তার বাড়ি চলে গেলো।
বাড়িতে এসেই বিজয় বৌকে বললো,বেশ ভালো করে আদা দিয়ে চা করো তো। একটু রসিয়ে সব গল্পগুলো পড়বো।বিজয় ভালো করে বিছানায় বসলো।
বিজয়ের বৌ মুন চা করে কাপ দুটি টেবিলে রাখলো।তারপর বসলো বিজয়ের পাশে। গল্পে ডুব দিয়েছে বিজয়।
মুনের মন ফিরে গেলো, পাঁচ বছর আগে কলেজ জীবনে।তখন ওরা দুজনে দুজনকে চিনত না। একদিন কলেজের কমন রুমে বিজয় বসে আছে। এমন সময় মুন গিয়ে বসলো তার পাশে। একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বিজয় আবার নিজের কাজ করতে লাগলো।মুন বললো,আপনি কোন ইয়ার?
------ থার্ড ইয়ার, বাংলা।
------আমারও বাংলা। ফার্ষ্ট ইয়ার।
-----ও তাই। কোথা থেকে আসেন।
------টিকিয়াপাড়া।
------ও আমি পটুয়া পাড়া থেকে।
-----তাহলে তো একই দিকে। খুব ভালো হলো একসঙ্গে যাওয়া আসা করা যাবে।
-----অবশ্যই।
তারপর থেকে ওরা একসাথে ওঠাবসা করতো।ভালোলাগা ক্রমশ ভালোবাসায় পরিণত হলো। তারপর বিয়ের। বিয়ের পরেই একটা ফার্মে চাকরী।এখন ওরা ঘর ভাড়া নিয়ে সুখে আছে।
মুন একটা গান গাইছিলো। বিজয়ের জামাটা আলনা থেকে টেনে গন্ধ শুঁকে দেখলো কাচতে হবে কি না। কাচতে হবে, তাই পকেট হাতড়ে টাকা পয়সা কাগজ বের করে টেবিলে রাখলো।মুন দেখলো,কাগজের সঙ্গে একটা রেলের টিকিট। মুন ভাবলো,অফিস তো সাইকেলে যায় তাহলে দাঁইহাটের টিকিট কেন? দাঁইহাটে আমাদের সাতকুলে কেউ থাকে না। তাহলে ওখানে কেন? কই বিজয় তো বলে নি, সে ওখানে গিয়েছিলো? তাহলে কি বিষয়টা বলার মত নয় বলে এড়িয়ে গেছে। সন্দেহ দানা বাঁধলো মুনের মনে। গান থেমে গেছে। অকারণে থালা, বাটি, গ্লাস ফেলে আওয়াজ করছে। বিজয় বললো,আস্তে কাজ করো।গল্প পড়ছি।
----আমি খেটে মরবো আর তুমি বাবুমশাই বসে গল্পের বই পড়বে?
---- কি হলো, অইভাবে কথা বলছো কেন?
----না বলবে না। আমি একা একা বাড়িতে থাকি আর উনি হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন।
-----কি বলছো,বুঝতে পারছি না। পরিষ্কার করে বলো।
-----দাঁইহাট কেন গেছিলে।কার কাছে। নিশ্চয় প্রেমিকার কাছে। আমাকে তবে বিয়ে করলে কেন?
----আরে দাঁইহাটে কেন যাবো?
-----আবার মিথ্যে কথা। আমার কাছে প্রমাণ আছে।
----কি প্রমাণ। কই দেখাও।
মুন দাঁইহাটের টিকিট এনে খাটে ফেলে দিলো।বিজয় হেসে উঠলো জোরে। বললো,আজ বই কিনতে প্ল্যাটফরমে গেছিলাম।প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম দশ টাকা। আর দাঁইহাটের টিকিট পাঁচ টাকা। টিকিট একটা থাকলেই হলো। তাই পাঁচ টাকা বাঁচাতে দাঁইহাটের টিকিট কাটলাম।
সুমন আমার সঙ্গে ছিলো। ওকেই জিজ্ঞাসা করো।
তারপর মোবাইলে সুমনকে ধরে ফোনটা দিতে গেলো বিজয়। মুন ফোনটা কেটে দিয়ে হাসিমুখে বললো,আমার বুঝতে ভুল হয়েছে। তারপর বিজয়ের গলা পেঁচিয়ে ধরে বললো,তুমি এমনি করেই শুধু আমার হয়ে থেকো চিরকাল।
বিজয় মুনকে আদর করার সময় শুনতে পেলো ভবিষ্যতের পদধ্বনি।
পাশাপাশি দুজনেই শুয়ে আছে বিছানায়। মুনকে বললো,আজ আমি তোমাকে আমার ছোটোবেলার গল্প শোনাই শোনো।
জানো মুন,ছোটোবেলার রায়পুকুরের রাধা চূড়ার ডালটা আজও আমায় আহ্বান করে হাত বাড়িয়ে । এই ডাল ধরেই এলোপাথারি হাত পা ছুড়তে ছুড়তে সাঁতার শিখেছি আদরের পরশে । ডুবন্ত জলে যখন জল খেয়ে ফেলতাম আনাড়ি চুমুকে, দম শেষ হয়ে আসতো তখন এই ডাল তার শক্তি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরতো অক্লেশে । হয়তো পূর্ব জন্মে আমার দিদি হয়ে যত্ন আদর করতো এই ডালটা । কোনোদিন তাকে গাছ মনে করিনি আমি ।এখনও জল ছুঁয়ে আদরের ডাক শুনতে পাই পুকুরের ধারে গেলে । রাধা নামের মায়াচাদর জড়ানো তার সবুজ অঙ্গে ।ভালো থেকো বাল্য অনুভব । চিরন্তন প্রকৃতির শিক্ষা অঙ্গনে নাম লিখে যাক নব নবীন শিক্ষার্থী প্রবাহ ।আমি এইসব ভাবছি। এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা বড় পাঁঠা আমাকে গুঁতিয়ে জলে ফেলে দিলো। খুব রাগ হলো কিন্তু পাঁঠার সঙ্গে লড়াই করতে লজ্জা হলো। যদি কেউ দেখে ফেলে।তুমি শুনছো মুন।মুন বললো,লেখক মশাই শুনছি। এইসব আবেগের কথাও লিখে ফেলো গল্পে।ভালো লাগবে।
তারপর শোনো মুন, কদতলার মাঠে এসে ঢিল মেরে পেরে নিতাম কাঁচা কদবেল। কামড়ে কচ কচ শব্দে সাবাড় করতাম কদ। বুড়ো বলতো, কদ খেয়ছিস। আর খাবি। কই তখন তো গলা জ্বলতো না। এখন শুধু ওষুধ। ভক্ত,ভব,ভম্বল,বাবু বুলা, রিলীফ সবাই তখন আমরা আমড়া তলায় গিয়ে পাকা আমড়া খেতাম। জাম, তাল,বেল, কুল,শসা, কলা, নারকেল কিছুই বাদ রাখতাম না। নারকেল গাছে উঠতে পারতো গজানন। শুধু দুহাতের একটা দড়ি। তাকে পায়ের সঙ্গে ফাঁদের মতো পরে নিতো গজানন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নারকেল গাছের পাতা সরিয়ে ধপাধপ নিচে ফেলতো। আমরা কুড়িয়ে বস্তায় ভরে সোজা মাঠে। বাবা দেখলেই বকবেন। তারপর দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে মাঠেই খেয়ে নিতাম নারকেল। একদম বাস্তব। মনগড়া গল্প নয়। তারপর গাজনের রাতে স্বাধীন আমরা। সারা রাত বোলান গান শুনতাম। সারা রাত নাচতাম বাজনার তালে তালে। সবাই মনে করতো, ব্যাটারা গাঁজার ভক্ত নাকি। গাজনে একজন হনুমান সেজেছিলো। আমরা তার লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পরে দেখলাম লোকটা রাগ করে নি। বলছে,লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো।
আর হনুমান লাফিয়ে শেষে জলে ঝাঁপ দিলো।
চারদিকে প্রচুর লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।
শীতকালে খেজুর গাছের রস। গাছের কামান হতো হেঁসো দিয়ে। মাথার মেথি বার করে কাঠি পুঁতে দিতো গুড় ব্যাবসায়ী। আমাদের ভয় দেখাতো, ধুতরা ফুলের বীজ দিয়ে রাকবো। রস খেলেই মরবে সে। চুরি করা কাকে বলে জানতাম না। একরাতে বাহাদুর বিশুর পাল্লায় পরে রাতে রস খেতে গেছিলাম। বিশু বললো, তোরা বসে থাক। কেউএলে বলবি। আমি গাছে উঠে রস পেরে আনি। তারপর গাছে উঠে হাত ডুবিয়ে ধুতরো ফুলের বীজ আছে কিনা দেখতো। পেরে আনতো নিচে। তারপর মাটির হাঁড়ি থেকে রস ঢেলে নিতাম আমাদের ঘটিতে। গাছেউঠে আবার হাঁড়ি টাঙিয়ে দিয়ে আসতো বিশু। সকালে হাড়ি রসে ভরে যেতো। ভোরবেলা ব্যাবসায়ির কাছে গিয়ে বলতাম, রস দাও, বাড়ির সবাইকে দোবো। বুক ঢিপঢিপ চাঁদের গর্ত। দেবে কি দেবে না, জানিনা। অবশেষে প্রাপ্তিযোগ। যেদিন রস পেতাম না তখন মাথায় কুবুদ্ধির পোকা নড়তো। তাতে ক্ষতি কারো হতো না। বিশু ভালো মিষ্টি রস হলে বলতো, এটা জিরেন কাঠের রস। মানে চারদিন হাড়ি না বাঁধলে রস মিষ্টি হতো। জানি না। আমরা গাছে নিচে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। রস পরতো জিভে টুপ টাপ। কতদিন ঘনটার পর ঘনটা কেটে গেছে রসাস্বাদনে। মোবাইল ছিলো না,ফেসবুক ছিলো না। কোনো পাকামি ছিলো না।সহজ সরল হাওয়া ছিলো। ভালোবাসা ছিলো। আনন্দ ছিলো জীবনে। ব্লু হোয়েলের বাপ পর্যন্ত আমাদের সমীহ করে চলতো। কোনোদিন বাল্যকালে আত্মহত্যার খবর শুনিনি। সময় কোথায় তখন ছেলেপিলের। যম পর্যন্ত চিন্তায় পরে যেতো বালকদের আচরণে, কর্ম দক্ষতায়। হাসি,খুশি সহজ সরল জীবন।
ছোটোবেলার সরস্বতী পুজো বেশ ঘটা করেই ঘটতো । পুজোর দুদিন আগে থেকেই প্রতিমার বায়নাস্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে আসা হত শিল্পী কে ।তারপর প্যান্ডেলের জোগাড় । বন্ধুদের সকলের বাড়ি থেকে মা ও দিদিদের কাপড় জোগাড় করে বানানো হত স্বপ্নের সুন্দর প্যান্ডেল । তার একপাশে বানানো হত আমাদের বসার ঘর । সেই ঘরে থেকেই আমরা ভয় দেখাতাম সুদখোর মহাজনকে।সুদখোর ভূতের ভয়ে চাঁদা দিতো বেশি করে। বলতো, তোরা পাহারা দিবি। তাহলে চাঁদা বেশি দেবো।
পুজোর আগের রাত আমরা জেগেই কাটাতাম কয়েকজন বন্ধু মিলে । কোনো কাজ বাকি নেই তবু সবাই খুব ব্যস্ত । একটা ভীষণ সিরিয়াস মনোভাব । তারপর সেই ছোট্ট কাপড়ের পাখির নিড়ে কে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা কেউ জানতে পারতাম না । মশার কামড়ও সেই নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভাঙাতে পাড়তো না ।তবু সকালে উঠেই মচকানো বাঁশের মত ব্যস্ততার আনন্দ । মা বাবার সাবধান বাণী ,ডেঙ্গু জ্বরের ভয় কোনো কিছুই আমাদের আনন্দের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি । হড়কা বানে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে , আমাদের আনন্দ ঠিক আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত মহানন্দের জগতে । এরপরে সকাল সকাল স্নান সেরে ফলমূল কাটতে বসে পড়তাম বাড়ি থেকে নিরামিষ বঁটি এনে । পুরোহিত এসে পড়তেন ইতিমধ্যে । মন্ত্র তন্ত্র কিছুই বুঝতাম না । শুধুমাত্র বুঝতাম মায়ের কাছে চাইলে মা না করতে পারেন না । পুষ্পাঞ্জলি দিতাম একসঙ্গে সবাই । জোরে জোরে পুরোহিত মন্ত্র বলতেন । মন্ত্র বলা ফাঁকি দিয়ে ফুল দিতাম মায়ের চরণে ভক্তিভরে । তারপরে প্রসাদ বিতরণের চরম পুলকে আমরা বন্ধুরা সকলেই পুলকিত হতাম । প্রসাদ খেতাম সকলকে বিতরণ করার পরে ।আমাদের সবার প্রসাদে ভক্তি বেশি হয়ে যেত ,ফলে দুপুরে বাড়িতে ভাত খেতাম কম । সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ ,ধূপ জ্বেলে প্যান্ডেলের ঘরে সময় কাটাতাম । পরের দিন দধিকর্মা । খই আর দই । পুজো হওয়ার অপেক্ষায় জিভে জল । তারপর প্রসাদ বিতরণ করে নিজেদের পেটপুজো সাঙ্গ হত সাড়ম্বরে ।
বিজয় এবার থামলো। মুন গল্প শুনে খুব খুশি। স্বামী তার লেখক। এই গরবে মুনের গরবিনী হৃদয় দুলে উঠলো।সমস্ত অভাব, না পাওয়ার দুঃখ নিমেষে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুন পরম আনন্দময় চাঁদের পদধ্বনি শুনতে পেলো তার অনুভবে।
মুন বলল,তুমি বাবা হতে চলেছ।
বিজয় বলল,কী আনন্দের কথা। কই একবার তার পদধ্বনি শুনি।বিজয় মুনের ভরাপেটে কান দিয়ে শুনল আগমনী সংগীত।হবু সন্তান পেটের ভিতরে পা ছুঁড়ছে। বিজয় মুনকে বলে,জীবনের প্রবাহ থেমে থাকে না।
সভ্য হওয়ার আগে মানুষ বনে বনে ঘুরে বেড়াতো ।তখন এত হিংসা ছিলো না । বনে পশু পাখি ঘুরে বেড়াত। সবুজ গাছ মানুষের মন জুড়িয়ে দিত । তখন এত গরম আবহাওয়া ছিল না ।মানুষের রোগ বালাই এত ছিল না । এই কথাগুলো বল ছিলো সমীর তার ছেলে মেয়েদের ।
বিজয় নদীর কাছাকাছি একটি গ্রামে বাস করতো। পড়ানোর পাশাপাশি সে গাছ লাগাত ছাত্রদের নিয়ে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে ।স্ত্রী রমা খুব কাজের মহিলা ছিলেন । কাজের ফাঁকে গাছ লাগাতেন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে । বিজয় গ্রামে গিয়ে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গাছ লাগাত ।আবার সময় পেলেই বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে অনেক অজানা তথ্য গ্রামবাসীদের শোনাত । একজন ছাত্র প্রশ্ন করল,
--- বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে কি বোঝায় গো বিজয় দা?একজন গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করলেন ।
বিজয় বলল,--আমাদের পৃথিবীর নানা দিকে বরফের পাহাড় আছে ।অতিরিক্ত গরমে এই বরফ গলে সমুদ্রের জল স্তর বাড়িয়ে দেবে ।ফলে সুনামী , বন্যায় পৃথিবীর সবকিছু সলিল সমাধি হয়ে যাবে ।
---তাহলে এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি?
-মানুষকে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে ।
গ্রামের একটা লোক বলল,--কি পদ্ধতি বলুন দাদা । কি করতে হবে আমাদের?
---এই যে পাখি ওপশুরা মল ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে তার সঙ্গে গাছের বীজ থাকে ।এই বীজ গুলি থেকে বিভিন্ন গাছের চারা বেরোয় । বাবলা,গুয়ে বাবলা,নিম, বট,প্রভৃতি চারা প্রকৃতির বুকে অযাচিত ভাবেই বেড়ে ওঠে ।শিমূল গাছের বীজের থেকে তুলো একটি ছোট বীজসহ উড়ে চলে আসে । একে আমরা বুড়ির সুতো বলি । তারপর বর্ষাকালে জল পেয়ে বেড়ে ওঠে ।
---তাহলে আমাদের কাজ কি?
---আমাদের কাজ হলও ওই চারা গুলি বড় করা ।তার জন্য আমাদের বাঁশের খাঁচা বানিয়ে ঢাকা দিতে হবে । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ যদি এই নিয়মে মেনে গাছ লাগায় তবেই একমাত্র বিশ্ব উষ্ণায়নের কোপ থেকে রক্ষা পাবে ।
কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষের চেতনা এখনও হয়নি । গাছ কাটা এখনও অব্যাহত আছে ।তাইতো এত গরম ।বৃষ্টির দেখা নেই ।বিজয় খুবই চিন্তার মধ্যে আছে । রাতে তার ঘুম হয়না । বর্ষাকাল চলছে ।সমুদ্র ফুলে উঠেছে আক্রোশে ।কি হয় ,কি হয় ।খুব ভয় ।বিজয় ভাবে,মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বেইমানি করেছে । এর প্রতিশোধ প্রকৃতি নেবেই । তারপর অন্য কথা ।একদিন বর্ষাকালে রাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে কিন্তু জেগে আছে সমীর আর বন্যার জলের বিষাক্ত ফণা । মাঝ রাতে বন্যার একটা বড় ঢেউ এসে সমীর ও তার গ্রামের সবাই কে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ধ্বংসের পথে । এখন সেই গ্রাম শ্মশানের মত ফাঁকা ।প্রকৃতি এখনও সুযোগ দিয়ে চলেছে বারে বারে । সাবধান হলে বাঁচবে । পৃথিবীকে সবুজের ঘেরাটোপে সাজাতে হবে। বাঁচার একমাত্র পথ গাছ, শুধু গাছ। বন্যা কমে গেলে নদীর পাড়ে ভাঙা বাঁধটা দশ গ্রামের লোক এসে একত্রে বাঁধলো মাটি আর বাঁশ দিয়ে শক্ত করে। বিজয় বলে সকল গ্রামবাসীকে , আমাদের গ্রামটা সবুজ গাছ করে দাও সবাই একত্রে গাছ রোপণ করে।তাহলে আমদের গ্রাম বাঁচবে।...
একদল বলাকার দল উড়ে এল রিমির মনমেঘে।তখন সে সাদাশাড়িতে সতের।দেহের সাগর ঘিরে উথালপাথাল ঢেউ।ঠিক সেই সময়ে নোঙর করে তার মনের তীরে পূর্ব প্রেমিক সমীরণের ছোঁয়ায় তার শিরশিরে পানসি নৌকার অনুভব।ধীরে ধীরে পালতোলা জাহাজের মত দুজনের প্রেম তরতরিয়ে এগিয়ে চলে।শত ঝিনুকের মুক্তোর সোহাগে দুজনেই রঙীন হয়ে উঠত।
চিন্তার রেশ কাটতেই বিপিন বলে উঠল,রিমি তুমি এত কী চিন্তা করছ?
- কিছু না।এমনি করেই কাটুক সময়।
- আমাদের বিয়ের পাঁচ বছরে একটা অনুষ্ঠান করলে হয় না?
- থাক ওসবে আর কী হবে? এই বেশ বসে আছি নদীর তীরে।
- তোমার অতীতের কথা বলো। আমি শুনব।
- কেন তোমার অতীত নেই
- আমার অতীত বর্তমান হয়ে রাজুর বউ হয়ে বসে আছে।
- ও, রাজুর বউ তোমার পূর্ব প্রেমিকা ছিল?
- হ্যাঁ ছিল একদিন। গ্রামের মন্ডপতলায় গেলেই মনে পড়ে বাল্যপ্রেম।কাঁসর ঘন্টা বাজত আরতির সময়।আমি ভালো কাঁসর বাজাতাম।আর তাছাড়া ওর মুখ দেখার লোভে ছুটে চলে যেতাম পুজোমন্ডপে। আরতির ফাঁকে দেখে নিত ওর চোখ আমাকে।তার চোখের নজর আমার দিকেই থাকত। সারাদিন তাকিয়ে থাকতাম ওদের বাড়ির দিকে।যদি একবারও দেখা যায় ওর মুখ। অসীম খিদে চোখে কেটে গেছে আমার রোদবেলা।
- আমারও অতীতের ভালোবাসা সমীরণ, ভেসে গেছে অজানা স্রোতে।এসো আজ আমরা আবার নতুন মনে এক হই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ চেয়ে।
- হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি। পুরোনো ব্যাথায় মলম লাগাব দুজনে দুজনকে।চলো আজ নৌকাবিহারে আমাদের বিবাহবার্ষিকী পালন করি।
- চলো। নব উদ্যমে এগিয়ে যাই আমরা নবসূর্যের আহ্বানে।
রিমি লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর ভক্ত।বিপিন পুণ্যদাস বাউলের গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।কিন্তু দুজনে দুজনের পছন্দকে শ্রদ্ধা করে।
রিমি বিপিনকে বলে তার প্রিয় লেখিকার কর্মজীবনের কথা,সাহিত্যের কথা।রিমি বলে, পুরুলিয়া,বাঁকুড়া,পশ্চিম মেদিনীপুরের শবর জনজাতির সঙ্গে মহাশ্বেতা জড়িয়ে ছিলেন আজীবন । তাকে মা হিসেবে মেনে নিয়েছিল শবরাও । পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর ব্লকে লােধা শবর , বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ , রাইপুর এবং পুরুলিয়ার তেরােটি ব্লকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী খেড়িয়া শবরদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষে কাজ করেছেন তিনি । এদের উন্নয়নে মহাশ্বেতারকর্মসূচি ছিল শিশুশিক্ষা , বয়স্কশিক্ষা , নারীশিক্ষা , শবরদের মদ্যপানের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি , তাদের হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করা এবং ব্রিটিশ যুগ থেকে শবরদের গায়ে লেগে থাকা ‘ অপরাধপ্রবণ জনজাতি’রতকমা থেকে তাদের মুক্ত করা।
বিপিন বলে,আমি পড়েছি,এজন্য আইনি লড়াইয়েও পিছপা হননি তিনি । ২০০৩ সালে এই শবরমাতা ম্যাগসাইসাই ’ পুরস্কারের ভূষিত হন । পুরস্কার মূল্যের দশ লক্ষ টাকা পুরােটাই তিনি দিয়েছেন এদের উন্নয়নার্থে । গ্রামে কোন সমস্যা হলেই তিনি সেইসব গ্রামে সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটে গেছেন ।
রিমি আবার বলে, মহাশ্বেতার সাহিত্যিক জীবন অবশ্য শুরু হয়েছিল আরাে অনেক বছর আগে । ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় পদ্মিনী ও যশোবন্তি গল্পদুটি লেখেন মহাশ্বেতা দেবী । পঞ্চাশের দশকের গােড়ায় মহাশ্বেতা দেবী গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে ।১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস ঝাঁসির রাণী, এইমধ্যপ্রদেশের লােককথা ও ইতিহাসের মিশেলে তৈরি । ষাট দশকের গােড়ায় অবিভক্ত বিহারে পালামৌ , হাজারিবাগ , সিংভূমের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে সেখানকার বেগার শ্রমিক প্রথা এবং জনজাতিদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে লেখেন ‘ অপারেশন বসাই টুডু, অরণ্যের অধিকার এবং ‘ চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর ‘ । ১৯৭৪ সালে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা ‘ হাজার চুরাশির মা ‘ বাংলা সাহিত্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল । পরবর্তীতে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের বিভিন্ন বাংলা পাঠ্যপুস্তকও সম্পাদনা করেন মহাশ্বেতা । ১৯৭৯ সালে বাবা মণীশ ঘটকের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ‘ বর্তিকা’র দায়িত্ব নেন । ১৯৮৩ সালে পুরুলিয়ার অবহেলিত জনজাতিদের উন্নতির জন্য গড়ে তােলেন পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি । তিনি তার বহু পুরস্কারের অর্থ দান । করেন এইসমিতিকে ।
রিমির পাশের বাড়িতে রাজু আর রাজুর বউ প্রজ্ঞা থাকে।রিমি না থাকলেই বিপিন প্রজ্ঞার কাছে যায়,কথা বলে।বিপিন গান করে,"গোলেমালে, গোলেমালে পিরীত কোরো না"। প্রজ্ঞা বলে,খুব তো সাহস দেখাও।বিয়ের আগে তো কিছু বলতে পারো নি। এখন তো আমি পরের বউ গো।বিপিন বলে,অপরজনা এখন আমার আপনজন হয়ে বসে আছে।বিপিন অতীতের কথা বলে প্রজ্ঞাকে,যখন মামার বাড়ি যেতাম মায়ের সঙ্গে তখন দাদু আমাদের দেখেই মামিমাকে মাছ,ডিম,মাংস রান্না করতে বলতেন। কখনও সখনও দেখেছি মামিমা নিজে ডেঙা পাড়া,সাঁওতাল পাড়া থেকে হাঁসের ডিম জোগাড় করে নিয়ে আসতেন। তখন এখনকার মতো ব্রয়লার মুরগি ছিলো না। দেশি মুরগির বদলে চাল,ডাল,মুড়ি নিয়ে যেতো মুরগির মালিক। নগদ টাকর টানাটানি ছিলো। চাষের জমি থেকে চাল,ডাল,গুড় পাওয়া যেতো। মুড়ি নিজেই ভেজে নিতেন মামিমা। আবার কি চাই। সামনেই শালগোরে। সেখানে দাদু নিজেই জাল ফেলে তুলে ফেলতেন বড়ো বড়ো রুই, কাতলা,মৃগেল। তারপর বিরাট গোয়ালে কুড়িটি গাইগরু। গল্প মনে হচ্ছে। মোটেও না। ১৯৮০ সালের কথা এগুলি।এখনও আমার সঙ্গে গেলে প্রমাণ হিসাবে পুকুর,গোয়াল সব দেখাতে পারি। আহমদপুর স্টেশনে নেমে জুঁইতা গ্রাম। লাল মাটি। উঁচু উঁচু ঢিবি। আমি পূর্ব বর্ধমানের ছেলে। সমতলের বাসিন্দা। আর বীরভূমে লাল উঁচু নিচু ঢিবি দেখে ভালো লাগতো।আমাদের মাটি লাল নয়। কি বৈচিত্র্য। ভূগোল জানতাম না। জানতাম শুধু মামার বাড়ি। মজার সারি। দুপুর বেলা ঘুম বাদ দিয় শুধু খেলা। আর ওই সময়ে দাদু শুয়ে থাকতেন। ডিসটার্ব হতো।
বিপিন বলে,এবার আসি কবিতার কথায়। নব্বই দশকের বাংলা কবিতার যে প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ছান্দিক কাঠামোর মধ্যে থেকে বিষয় ভিত্তিক কবিতা লেখা, বা বলা যায় ভাবপ্রধান বাংলা কবিতার এক প্রবর্ধন, তা শূন্য দশকে এসে বেশ খানিকটা বদলে যায়। আমরা লক্ষ্য করি লিরিক প্রধান বাংলা কবিতার শরীরে কোথাও একটা অস্বস্তি সূচিত হয়েছে। হয়ত নব্বই দশকের লেখা থেকে নিজেদের আলাদা করার তাগিদ থেকেই এই উত্তর। হয়ত সত্তর দশকের ছায়ায় লালিত বাংলা কবিতার পাঠাভ্যাস থেকে নিজেদের আলাদা করার এক সচেতন প্রচেষ্টা। যেখানে নব্বই দশকের সংকলন করতে গিয়ে সম্পাদক সে দশকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেন প্রেম এর সঙ্গে এটিএম এর অন্ত্যমিল, সেখানে শূন্য দশকের সম্পাদককে ঘাঁটতে হবে নির্মাণের ইতিহাস। যেখানে নব্বই দশকের কবি খুঁজে বেড়িয়েছেন গল্প বলার ছান্দিক দক্ষতা, সেখানে শূন্য দশকের কবি খুঁজেছেন ভাষা প্রকরণ। হয়ত এর পিছনে কাজ করেছে এক গভীর সত্য যে কবিতা আর জনপ্রিয় হয় না। কবি আর চটুল মনোরঞ্জন করবেন না। আর এই কাজে শূন্য দশক অনেকাংশই তাদের শিকড় পেয়েছে আশির দশকের নতুন কবিতা আন্দোলনে।
এছাড়া বাঙালীর দুর্গাপুজে এক ভালোলাগার দলিল।ঘুরে ঘুরে সারারাত কলকাতার ঠাকুর দেখা আর খাওয়াদাওয়া, ধুনুচি নাচের স্মৃতি জড়িয়ে বেঁচে থাকুক অমলিন স্মৃতি।কুমোরপাড়ার খ্যাতি ছিল হাঁড়ি কলসি ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য বাসনপত্র তৈরির জন্যই। এখানকার পুরনো অধিবাসীদের কথায় জানা যায়, বিশ শতকের গোড়ার দিকেও নাকি এখানে কিছু মাটির হাঁড়ি-কলসি নির্মাতার দেখা পাওয়া যেত। প্রথমে হাঁড়ি-কলসি, তার পরে ঘর সাজাবার পুতুল এবং একটা সময়ের পরে, যখন দুর্গাপুজো ক্রমে আমজনতার উৎসবে পরিণত হল, তখন থেকে ছোট্ট সেই কুমোর পাড়া রূপান্তরিত হয়ে উঠতে লাগল প্রতিমা নির্মাণের প্রধানতম কেন্দ্র,কুমোরটুলিতে।
বাসস্টপেজেই অতনুর বাড়ি।সে বলে, রাত বাড়লে বাসস্ট্যান্ড একটা আমোদের জায়গা হয়ে যায়। অন্ধকারে শুয়ে থাকা কিশোরী থেকে বুড়ি ভিখারির পাশে শুয়ে পড়ে মাতালের দল। তারা তো জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খায় না। শুধু একগ্রাস ভাত জোগাড় করতেই তাদের দিন কেটে যায়। তারপর রাতচড়াদের বাজার। কেউ ওদের মালিক নয়। বাজারি মাল দরিয়া মে ঢাল। ঠিক এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর আলো দেখেছিল অতনু। কে তার বাপ সে জানে না। আর জন্মদাত্রী ফেলে দিয়েছিল বাসের ছাদে। সেখানে শকুনের মত ওৎ পেতে থাকে হায়েনার মত ভয়ংকর অমানুষের দল। তারা অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড় করে। বড় হলে চুরি বা ভিক্ষা করে তারা যে টাকা আয় করে তার বৃহৎ অংশ নিয়ে নেয় হায়েনার দল। না খেতে পাওয়ার প্রবাহ চলতেই থাকে। এর থেকে মুক্তি পায় না অনাথ শিশুরা।
অতনু এখন বেশ স্মার্ট, বুদ্ধিমান। সে নিজের চেষ্টায় মেকানিকের কাজ শিখে নিয়েছে। মাথা উঁচু করে চলা ছেলেদের সকলেই সমীহ করে।
অতনু চুরি করে না, ভিক্ষাও করে না। সে বলে, হাত পা আছে। খেটে খাব। আর তোদের যা পাওনা মিটিয়ে দেব। সে বলে হায়েনার দলকে, বেশি ঘাঁটালে আমাকে, দেব শালা খালাস করে। আমার বাঁধন শক্ত বে। ওসব মাস্তানী তোর পকেটে রেখে দে।
যতই হোক শয়তানদের সাহস কিন্তু বেশি হয় না। অতনু একটা দল করেছে ছেলে মেয়েদের। সে বলে, শালা, কোন শালা রাতে খারাপ কাজ করতে এলে একসঙ্গে আ্যটাক করব। ওদের দৌড় বেশিদূর নয়। অতনু থাকতে আর অনাথের দল বাড়াতে দেব না বাসস্টপে। এই এলাকা এখন নতুন প্রজন্মের। ওরা আমাদের বড় করেছে তাই ওদের পাওনাটুকু দেব।
হায়েনার দল সাবধান হয়ে গেছে। এখন আর অনাথ বাচ্চা কম পায় এইস্থানে। অতনুর বিরুদ্ধে কাজ করে ওরা অনেকবার ঠকেছে।অতনুর দলবল দেখে ওরা অন্য জায়গায় ডেরা বাঁধে।
অতনু সকলকে নিজের পরিবারের সদস্যের মত দেখে।
এই পরিবারের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সুনীতা। সে পাশের পাড়ায় থাকে। অতনু তার আদর্শ। কিন্তু অতনুর বংশ পরিচয় নেই। তা না থাক তবু সে সমাজসেবী।
অতনু দেখেছে মারামারি বা লড়াই করে জেতার থেকে ভালবাসার জোর বেশি। ভালোবেসে কথা বললে শয়তানও বশ হয়ে যায়। এখন সে একদম আনন্দে থাকে। এলাকার লোকজন তাকে ভালবাসে।
সুনীতা ভাবে, অতনুদা এত বড় মন পেল কোথা থেকে।
সকলের উপকারে ছুটে যায় অতনু। হাসপাতাল,শ্মশান যেখানে যার প্রয়োজন প্রথমেই ডাকে তাকে। সুনীতা ভাবে, সে কি অতনুর প্রেমে পড়েছে। সবসময় অতনুকে দেখতে পায় খাতায়, জলে, দেওয়ালে, আয়নায়। তবু অতনুকে বলতে সাহস হয় না। যদি রেগে যায়। যা ব্যক্তিত্ব ছেলেটার, শ্রদ্ধা হয়। সুনীতা সবসময় এখন এইসব ভাবে।
অতনু বলে তার বন্ধুকে, আমি তো অনাথ, বেজন্মা। ভদ্র সমাজে আমার স্থান হবে না। আমি কি চিরদিন এই বাসস্টপেজেই থেকে যাব?
আজ সুনীতা গ্রামের বাড়ি যাবে। সে পরিবারের সঙ্গে বাসস্টপে এসেছে ব্যাগপত্তর নিয়ে। সুনীতাকে দেখে অতনু কাছে এল। অতনুর মা বললেন, সুনীতার মুখে তোমার কথা শুনেছি। আজকে তোমাকে ছাড়ছি না। আমাদের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি পুজো দেখতে চল। অতনু বলল,আমি অনাথ পুজোবাড়িতে আমার স্থান হবে? সুনীতার মা বললেন, কে বললো তুমি অনাথ। তুমি আমাদের পরিবারের একজন হলে। আমরা আছি, চল। অতনু তার সঙ্গিদের বললো, আমি পুজোয় গ্রামে যাচ্ছি। তোরা সাবধানে থাকিস।
গ্রামের পুজোবাড়িতে আরতির বাজনা বাজছে। ধুনোর গন্ধে পুজোবাড়ি মাতোয়ারা। আর একটু পরেই ধুনুচি নাচ শুরু হবে।
সুনীতা ধুনুচি নাচ নাচছে। ধুনোর গন্ধে অতনু খুশি। একটা শিহরণ তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। সুনীতার চোখ তার দিকে। সুনীতার মা অতনুকে হাত নেড়ে হাসিমুখে ডাকছেন। সুনীতার মায়ের মুখটা ঠিক দুর্গা প্রতিমার মত। তার চোখের দিকে তাকিয়ে অতনু এই প্রথম বলে উঠলো, মা, মা গো...।
রাজুকে বিপিন তার বাড়ি নিয়ে আসে,গল্পগুজব করে।সে বলে,তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমার বাড়ি আসবে। এবার পুজোয় আমরা আবাডাঙা যাব।বিপিন বলে,শুনেছি ওখানে পটের ঠাকুর পূজিত হন।রাজু বলে,হ্যাঁ।দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল।রাজু বিপিনকে নিয়ে এল আবাডাঙা।সে বলল,বীরভূমের আবাডাঙা গ্রামে বাড়ুজ্জে পরিবারের পটের পুজো বিখ্যাত। পটের দুর্গা,পটের লক্ষী,পটের কার্তিক নানা জায়গায় পূজিত হন। পাটের থিম "পট ও পুতুল এর মাঝে এস ই ও " মূলত প্রতিটি জেলার হস্তশিল্পের তাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ।থিমটি প্রথমবারের মতো বাংলার ২৩টি জেলার প্রতিটি হস্তশিল্পের সারমর্ম। সমৃদ্ধসাংস্কৃতিক এই ঐতিহ্যকেই মূলত তুলে ধরতেই চেয়েছে এসইও।এসইও র এই উদযাপন শুধু বাসিন্দাদের জন্যই নয়।ঘরের মেয়ের এই আগমন উৎসব সমস্ত দর্শকদের উপভোগের জন্যও সমান খোলা থাকে। ভাস্করশিল্পী প্রদীপ রুদ্র পালের হাতে এবার তৈরি হচ্ছে তাদের মাতৃমূর্তি।দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসে সিলভার ওকের এমন নির্মল ও কল্যাণময় মাতৃমূর্তি দেখতে। সারল্যই এই মূর্তির বৈশিষ্ট। মা পরে থাকেন সুতির শাড়ী। সহজ সরল গ্রাম্য মেয়ের সাজে সেজে ওঠেন ওখানে মা। সঞ্জায় দাসের সৃজনশীল নির্দেশনায় এবার সেজে উঠছে সিলভার ওকের মন্ডল। আলোকসজ্জ করছেন এবারে বিশ্বজিৎ সরকার। প্যান্ডেল ডিসাইনের দায়িত্বে আছেন সুরজিৎ সেন।
পূজার সময় একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবার। তাদের মধ্যে
প্রথম হলো আনন্দমেলা উৎসব এই উৎসবে বাড়ির শেফরা তাদের রান্নার দক্ষতা প্রদর্শন করবেন ।
দ্বিতীয়ত আবাসিকদের জন্য থাকছে ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, যেখানে নাটক, আবৃত্তি, নাচ, গান প্রভৃতি পরিবেশন করতে পারবেন ৮ থেকে ৮০ সকলে
তৃতীয়ত স্বনামধন্য গায়ক অনীক ধর ও উর্মি চৌধুরী আসছেন এই পুজোয় গান গাইতে।
চতুর্থত থাকছে মহাভোজ। এই চারদিন আবাসিকরা মণ্ডপেই পুজোর ভোগ খাবেন। আর খাওয়া দেওয়ার সাথেই চলতে থাকবে আড্ডা।
ভগ্নপ্রায় মন্দিরেই পুজো পান দেবী পটেশ্বরী। বর্ধমান রাজবাড়িতে যখন রাজা রাজত্ব করতেন তখন সাড়ম্বরে পূজা পেতেন দেবেন পটেশ্বরী। কিন্তু এখন সেই পুজোর জৌলুস খানিকটা মলিন হয়েছে। অতীতে বহু মানুষ এই পুজো দেখতে ভিড় জমাতেন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসত এই বাড়ির পুজো দেখতে। বর্ধমান রাজার তৈরি লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুরের বাড়িতে পুজো হতো।
এই পুজোতে বাড়ির মহিলারা কখনই সবার সামনে আসতেন না। গোপন রাস্তা দিতে তাঁরা মন্দিরে আসতেন এবং সেখানকার দ্বিতলে বসে পুজো দেখতে। পুজোটা আজও হয়। কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দির প্রায় ভেঙে গিয়েছে। গত দুই বছর করোনার কারণে জনসাধারণ এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি।
রাজবাড়ি তার জৌলুস হারালেও পুজোর রীতি নীতি, জৌলুস কোনওটাই কমেনি আজও। অতীতের নিয়ম মেনেই পূজিত হন দেবী পটেশ্বরী। প্রতিপদ থেকে এই পুজো শুরু হয়ে যায়। এই পুজো নাকি বর্ধমানের রাজা মহাতাব চাঁদ শুরু করেছিলেন। কাঠের পটের উপর নানান রঙ দিয়ে আঁকা হতো দশভূজাকে। এখানে কেবল গণেশের দুটি চোখ দেখা যায়। বাকি সকলেরই দেখা যায় একটি করে চোখ। এমন ভাবেই আঁকা হয় এই পট। এই বাড়িতে আজও আছে বলি প্রথা। তবে পাঁঠা নয়, বলি হয় মিষ্টির। আগে অবশ্য কুমড়ো বলি হতো। নবকুমারীর পুজোও হয় এই বাড়িতে অষ্টমীর দিন।সমীরণ বলে,বীরভূমের পট নিয়ে প্রচুর কিছু লেখা না হলেও কিছু মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। যাদু পটুয়াদের কথা লিখেছেন ও’ম্যালি, গৌরীহর মিত্র প্রমুখ। এই পটুয়াদের সঙ্গে হাট সেরান্দির পটশিল্পীদের পার্থক্য রয়েছে।এখানকার পটশিল্পীরা সূত্রধর সম্প্রদায়ের। পটের সঙ্গে গান এঁরা করেন না। কেবলমাত্র দুর্গার পট আঁকা/লেখা ছাড়া অন্য পটও করেন না। সে দিক থেকে অন্যান্য পটুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই পটশিল্পীদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, এমনটা বলা যায় না। কিন্তু শোনা যায়, হাট সেরান্দির সূত্রধর শিল্পীদের পূর্বপুরুষ রাজারাম এসেছিলেন অজয়পাড়ের ভেদিয়া থেকে। তিনিও পটের শিল্পী ছিলেন। ভেদিয়া নামটির উৎস কেউ কেউ‘বেদিয়া’ বলে গণ্য করা হয়। বেদিয়াদের মধ্যে পটশিল্পীদের গোষ্ঠী রয়েছে। আসলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে কোথাও না কোথাও জুড়ে রয়েছে। এই যোগসূত্রগুলি খুঁজে দেখা দরকার। যাই হোক, বর্তমানে আমরা সূত্রধর শিল্পীদের মধ্যে পট আঁকার প্রায় দুশো বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাচ্ছি। রামকৃষ্ণ সূত্রধরের পিতা আদরগোপাল, তাঁর পিতা কালীপদ, কালীপদের পিতা শিবরাম, শিবরামের পূর্বে দ্বারিকানাথ, তদূর্ধ্ব রাজারাম। এ ভাবেই পারিবারিক ইতিহাস বাহিত হয়েছে। সূত্রধরদের মধ্যে প্রবীণ মানিকচাঁদ গুণী শিল্পী। এই সম্প্রদায়ের বাইরে রয়েছেন রত্নাকর মেটে। পটশিল্পের ইতিহাস নিয়ে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। আমার উদ্দেশ্য বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা।
সমীরণ নিজের আশ্রমে বেশিদিন তাকে না।এবার রিমি ও বিপিনকে নিয়ে চলে এলো কালনা ঘুরতে।সমীরণ বলে,পূর্ব বর্ধমান জেলার উল্লেখযোগ্য শহর অম্বিকা কালনা।ছোটথেকেই শুনে আসছি কালনা শহরের ঐতিহাসিক সৌন্দর্যের কথা।দেখার সৌভাগ্য হল ডি এল এড পড়ার সুবাদে।কালনা নবকৈলাস মন্দিরের ১০৯টি মন্দিরের মধ্যে ১০৮টি মন্দির জ্যামিতিক বৃত্তে বিন্যস্ত। দুটি বৃত্তে বিন্যস্ত এই মন্দিরগুলির বাইরের বৃত্তে ৭৮টি এবং ভেতরের বৃত্তে মোট ৩৪টি অবস্থিত। বৃত্তের বহির্দেশে, পশ্চিমদিকে ১০৯ সংখ্যক মন্দিরটি অবস্থিত। বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত ১০৮টি মন্দির আটচালার আকৃতিতে নির্মিত। ভিতরের বৃত্তের পরিধি প্রায় ৩৩৬ ফুট এবং বাইরের বৃত্তের পরিধি ৭১০ ফুট। এই মন্দিরগুলি স্বল্প উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এবং মন্দিরগুলি পরস্পর সংলগ্ন। মন্দিরগুলির উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট এবং প্রস্থ ৯.৫ ফুট। এই মন্দিরের দেয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের পর্ব এবং শিকারের বহু দৃশ্যও চিত্রিত রয়েছে। ১০৯ সংখ্যক মন্দিরটি আটটি সিঁড়িবিশিস্ট বারান্দার উপর অবস্থিত । এর মন্দিরটি ৬ ফুট উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর অবস্থিত, যার আয়তন ১৩ ফুট X ১৩ ফুট এবং উচ্চতা ৩৫ ফুট। এই মন্দিরটির বর্তমান নাম জলেশ্বর।বৃত্তদুটির কেন্দ্রে একটি বাধানো ইঁদারা আছে যা মন্দিরের পূজার কাজে ব্যবহৃত জলের চাহিদা মেটায়। তবে অনেকে মনে করেন এটি শূণ্য অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ শিবের প্রতীক।
বর্ধমান রাজপরিবারে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলিত ছিল। গঙ্গার অবস্থিতি এবং বৈষ্ণব পাট হিসেবে পরিচিত হওয়ায় বর্ধমান রাজপরিবার কালনাতেও আবাসস্থল এবং বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মন্দির স্থাপন করে। রাজপরিবারের সদস্যরা কালনায় গঙ্গাস্নানে যেতেন। এই উদ্দেশ্যে বর্ধমান এবং কালনার মধ্যে ১৮৩১ সাধারণাব্দে রাজপথ নির্মাণ করান তেজচন্দ্। এই সঙ্গে নির্মিত হয় প্রতি আট মাইল অন্তর জলাশয়, বাংলো, আস্তাবল ইত্যাদি। ভোলানাথ চন্দ্র প্রণীত 'ট্রাভেলস অব আ হিন্দু' (লন্ডন, ১৮৬৯) এবং ডব্লু ডব্লু হান্টারের 'আ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' (১৮৭৬) উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, গঙ্গার ধারে ছিমছাম সুন্দর শহরের রূপকার বর্ধমান রাজপরিবার। কালনা ছিল বর্ধমান জেলার একমাত্র বন্দর এবং মূল বাণিজ্যকেন্দ্র। জেলার বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানি হত কালনা বন্দরের মাধ্যমে। কালনা পুরসভার অস্তিত্ব পাওয়া যায় ১৮৭১ সাধারণাব্দে। ১৮৭২-য় কালনার জনসংখ্যা ছিল ২৭,৩৩৬। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় রেভারেন্ড জেমস্ লং-এর রচনা থেকে জানা যায় যে, কালনা বাজারে ইটের তৈরি এক হাজার দোকান ছিল। রংপুর, দেওয়ানগঞ্জ এবং জাফরগঞ্জ থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল কিনে মজুত করা হত কালনায়। খাদ্যশস্য, সিল্ক, তুলো ইত্যাদি ছিল প্রধান পণ্যদ্রব্য।
এ হেন কালনা রাজবাড়ি চত্বরের সবচেয়ে পুরোনো পঁচিশচূড়া মন্দিরটি হল লালজি মন্দির। ১৭৩৯ সাধারণাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করান বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্-জননী ব্রজকিশোরী দেবী। মন্দিরের প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি। 'লালজি'-র নামকরণের পিছনে তেমনই একটি কিংবদন্তি আছে।
কালনা ভ্রমণ শুরু করলাম চকবাজার এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত নবকৈলাস দর্শনের মধ্যে দিয়ে যা ১০৮ শিবমন্দির বলে পরিচিত। অম্বিকা কালনা ষ্টেশন থেকে টোটো করে চলে এলাম শহরের প্রানকেন্দ্রে ১৮০৯ সালে বর্ধমানের রাজা তেজ বাহাদুর কতৃক প্রতিষ্ঠিত অপরূপ শিল্পের এই একচালা মন্দির প্রাঙ্গণে। দুটি বৃত্তের মধ্যে ৪টি প্রবেশদ্বার নিয়ে ৭৪টি মন্দির বাইরে ও ভিতরে ৩৪টি মন্দির রয়েছে। বাইরের ৭৪টি মন্দিরে একটি সাদা শিবলিঙ্গ ও পাশেরটি কালো শিবলিঙ্গ এবং ভিতরের ৩৪টি মন্দিরে সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরের প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গ উওরমুখী এবং শিবলিঙ্গগুলোর অবস্থান ও কিছুটা ভিন্ন। মন্দির প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে লোহার জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত এক জলাধার রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে ৩৪টি শিবলিঙ্গ একসাথে দেখা যায়। অদ্ভূত এক চিন্তা চেতনা ও ভাবনার নিদর্শন হচ্ছে এই নবকৈলাস বা ১০৮ শিবমন্দির।প্রখর বুদ্ধিমতী ব্রজকিশোরী তাঁর রাধিকা মূর্তির সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এক সন্ন্যাসীর কাছে থাকা শ্যামরায়-এর এবং রাজ-জামাতা 'লালজি'-র আবাসস্থল হিসেবে অনন্য শৈলীর দেবালয়টি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন।
লালজি মন্দির চত্বরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। লম্বা-চওড়ায় ৫৪ ফুট বর্গাকার মন্দিরটি প্রায় চার ফুট বেদির ওপর অবস্থিত। মন্দিরের সামনে আছে চারচালা নাটমন্দির। চত্বরে প্রবেশপথের উপরে আছে নহবতখানা। বাঁ-দিকে রয়েছে পর্বত আকৃতির গিরিগোবর্ধন। মূল মন্দিরের চারদিকে চারচালা ছাদযুক্ত দীর্ঘ এবং ত্রিখিলান বারান্দা আছে। প্রথম তলের ছাদের চার কোণে সৃষ্ট খাঁজে তিনটি করে---দুটি চূড়া সমউচ্চতায় এবং মাঝেরটি একটু পেছোনো অবস্থায় সমতল করে বসানো আছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখভাগে আছে ত্রিখিলান প্রবেশদ্বার। মন্দিরের সম্মুখভাগ টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ। রামায়ণ, নানা পৌরাণিক কাহিনির ফলকের পাশাপাশি নামের সঙ্গে সাজুয্য রেখে মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণের অনেকটা অংশ জুড়েই আছে কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনির প্রতিফলন।
লালজি মন্দিরের বর্তমান বয়স ২৮০ বছর। ১৯৫৪ সালে জমিদারি উচ্ছেদের পর রাজবাড়িচত্বর প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তার অন্তত ৪৫ বছর পর সমগ্র চত্বরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মণ্ডল অধিগ্রহণ করে। চত্বরের সৌন্দর্যায়নের কাজটি চমৎকারভাবে হলেও স্থাপত্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন সাধারণ মানুষ।
রিমির মনটা আনবাড়ির আঙিনার ধুলোয় বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে মনটা।সকালে উঠে সমীরণের উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে।তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়।বিপিন ও সমীরণ হরিনাম করে।রিমি খোল বাজায়।
পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত এই সতীপীঠ আমার জন্মস্থান বড়পুরুলিয়া গ্রামের কাছাকাছি। তাই বারবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সতীপীঠে।
সত্য যুগে দক্ষ যজ্ঞে সতী শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দেন। এর পর মহাদেব কালভৈরবকে পাঠান দক্ষকে বধ করতে। সতীর দেহ নিয়ে তিনি শুরু করেন তাণ্ডবনৃত্য। ফলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ বিভিন্ন ভাগে খণ্ডিত করেন। এই অংশ গুলো যেখানে পরেছে সেখানে মন্দির তৈরি হয়েছে। এগুলোকে সতীপীঠ বা শক্তিপীঠ বলে। এগুলি তীর্থে পরিণত হয়েছে। পীঠনির্ণয়তন্ত্র তন্ত্র মতে দেবীর বাম বাহু পড়েছিল বহুলায়। পরে রাজা চন্দ্রকেতুর নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় কেতুগ্রাম ।
পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মাতা সতী নিজের বাপের বাড়িতে বাবার কাছে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সেখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। মাতা সতীর দেহত্যাগের খবর মহাদেবের কাছে পৌছতেই মহাদেব সেখানে উপস্থিত হন।সতীর মৃতদেহ দেখে ক্রোধে উন্মত্ত মহাদেব এই দেহ কাঁধে নিয়ে তান্ডব নৃত্য চালু করেন। মহাদেবের তান্ডব নৃত্যে পৃথিবী ধ্বংসের আশঙ্কায় শ্রীবিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দ্বারা মাতা সতীর দেহ একান্নটি খন্ডে খণ্ডিত করেন। সেই দেহ খন্ড গুলোই যে যে স্থানে পড়েছিল সেখানে একটি করে সতীপীঠ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই রকমই একটি সতীপীঠ হলো “বেহুলা” বা “বহুলা” সতীপীঠ।অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে এটিকে আবার “বাহুলা” পীঠ বলে উল্লেখ করা আছে এবং এখানের অধিষ্ঠিত দেবীকে “বাহুলা চন্ডিকা” বলা হয়েছে। আবার “শিবচরিত গ্রন্থ” অনুযায়ী কেতুগ্রামেরই ‘রণখন্ড’ নামে একটি জায়গায় সতীর ‘ডান কনুই’ পড়েছে। এখানে অধিষ্ঠিত দেবীর নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরব মহাকাল।
বর্ধমানের কাটোয়া থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে কেতুগ্রামে বহুলা সতীপীঠ অবস্থিত। অনেক বছর আগে এই গ্রামে তিলি বংশজাত ভূপাল নামক এক রাজা বাস করতেন। সেই রাজার একটি ছেলে ছিল, তার নাম চন্দ্রকেতু। মনে করা হয় চন্দ্রকেতুর নামেই এই গ্রামের নাম হয়েছে কেতুগ্রাম। প্রাচীনত্ত্বের বিচারে এই কেতুগ্রামের বয়স অনেক। অনেকের মতে এই কেতুগ্রামেই জন্মেছিলেন নানুরের বিশালাক্ষী-বাশুলি দেবীর উপাসক চন্ডীদাস। এই গ্রামে ছিল তার আদি বাসস্থান। এই কেতুগ্রামের উত্তরদিকের একটি জায়গাকে স্থানীয় মানুষজন চন্ডীভিটা বলে সম্বোধন করে থাকে। গ্রামেই অবস্থান বহুলা মায়ের মন্দিরের। রাও পদবিধারী জমিদারেরা বহুলা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। বর্তমানে মন্দিরের যে সেবাইতরা রয়েছেন তারা এই রাও জমিদারদের বংশধর। এই কেতুগ্রামে “মরাঘাট মহাতীর্থ” বলে একটি জায়গা রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে শিবচরিত গ্রন্থে রণখন্ড বলে যে জায়গার উল্লেখ করা আছে সেটি আসলে কেতুগ্রামের মরাঘাট মহাতীর্থ নামক জায়গাটি। এখানেই দেবীর দেহখন্ড পড়েছিল। এই মরাঘাটের পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে গেছে। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে মরাঘাট মহাতীর্থ অনেক বছর আগে শশ্মান ছিল। শশ্মানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর তীরে মৃত শিশুদের দেহ পোঁতা হতো। এখানে অনেক সাধক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখানেই রয়েছে দেবীর ভৈরব ভীরুক। তবে এটা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকের মতে কেতুগ্রামে বহুলা দেবীর সাথেই ভৈরব ভীরুকের অবস্থান। আবার অনেকের মতে কেতুগ্রাম থেকে একটু দূর “শ্রীখন্ডে” আছে মায়ের আসল ভৈরব ভীরুকের লিঙ্গ ও মন্দির।
সমীরণ বলে,গ্রামে মায়ের যে মন্দির আছে, সেটিকে নতুন ভাবে সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরে দেবীর মূর্তিটিকে একটি কালো পাথরের উপর স্থাপন করা হয়েছে। দেবীর মুখ বাদে সারা শরীর সুন্দর বস্ত্র দ্বারা আবরণ করা থাকে। মায়ের মূর্তির চারটি হাত। মায়ের পাশেই রয়েছে অষ্টভুজ গণেশের মূর্তি। গণেশের এই মূর্তিটি অনেক পুরানো। মা এখানে স্বামী পুত্র নিয়ে একসাথে বাস করেন। এখানে দেবীর নিত্য পুজো করা হয়। মাকে রোজ অন্নভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরের পাশে একটি পুকুর আছে, অনেকের বিশ্বাস এই পুকুরে অবগাহন করলে রোগ ভালো হয়ে যায়।
আজ সমীরণ সকালে বলল,আজ আমরা অট্টহাসতলা যাব।তৈরি হয়ে সকলে বেরিয়ে পড়ল।সমীরন বলে,কলকাতা থেকে ধর্মতলা থেকে নিরোলের সরকারি বাস (SBSTC) পাবেন। তবে বাসে সময়টা একটু বেশিই লাগে। বাস ছাড়ার সময় হল বিকেলে তিনটে। ওই বাস বাসটি নিরোল পৌঁছায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। নিরোলে নেমেই টোটো রিক্সা করে পৌঁছে যান অট্টহাস সতীপীঠে। আপনি চাইলে মন্দিরে আগে থেকে ফোন করেও আসতে পারেন। তাতে আপনারই সুবিধা। অতিথিতের থাকার জন্য জায়গা আছে। ভক্তদের থাকা, খাওয়া মন্দির থেকেই পরিচালিত হয়।
এছাড়াও কাটোয়ার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মস্থান। যেমন, চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাড়ি ঝামতপুর নামের এক গ্রামে। বাংলায় মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের বাড়ি কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। ফলে অট্টহাসে এলে আপনি এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মস্থানেও আসতে পারবেন ঘুরতে। অন্যদিকে কাটোয়া থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেই জগদানন্দপুর গ্রাম। সেখানেই রয়েছে রাধাগোবিন্দ জিউয়ের মন্দির। যদি আপনার পুরাতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহ থাকে, তাহলে এই মন্দিরের গঠনশৈলি আপনাকে অবাক করবেই।মন্দিরের পূর্বপাশে সাধক ভোলাবাবার মন্দির ৷ পঞ্চমুন্ডির আসন ৷ রটন্তী কালিকা মন্দির ৷এই কালীর কাছে ডাকাতরা পুজো করত ৷ আগে অট্টহাসে পূজার পর শিবাভোগের( শিয়ালকে খাওয়ানো ) ব্যবস্থা ছিল ৷ ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় শৃগালকূল ধ্বংস হওয়ায় ৷ এখন ওই প্রথা উঠে গেছে ৷ শাক্তদেবী হলেও এখানে বাৎসরিক পুজো হয় বৈষ্ণবীয় উৎসবের সময় দোল বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ৷ এখানে ধূমধাম সহকারে ওই উৎসবের প্রচলন করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা কাটোয়ার বিখ্যাত দুলাল সাধু ৷
যদিও বীরভূমেও অট্টহাস সতীপীঠ আছে ৷যা লাভপুরের কাছে ৷ সেখানেও গিয়েছি ৷ আগে বলেছি সেই সাধনপীঠ তথা সতীপীঠের কাহিনী ৷
এই সতীপীঠে দেবীর পাথরের প্রতিমা উপর মহিষমর্দ্দিনীর পাথর মূর্তি রেখে নিত্যসেবা করা হয় ৷মহাভোগ যোগে কালীমন্ত্রে দেবী পূজিতা হন ৷এখানে মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী দন্তরা চামুন্ডা ৷ ভূগর্ভের কয়েক হাত নিচে রয়েছে সতীর মূল শিলা বা পাথর ৷হাজারেরও বেশি বছর আগের একটা নথি পাওয়া গেছে একটা স্কেচ তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ "অট্টহাসে চ চামুন্ডা তন্ত্রে শ্রী গৌতমেশ্বরী "৷ তাই , অনেকে বলেন এখানে
প্রাচীন বৌদ্ধ দেবীর হিন্দুআয়ন হয়েছে ৷ তাই , মনে হয় হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক , বজ্রযানী ও সিদ্ধাচার্যগণ এখানে সাধনা করেছেন ৷
মায়ের কাছেই ছোট মন্দিরে বিল্লেশ থাকলেও মূল
বিল্লেশ মন্দির বিল্লেশ্বর গ্রামে ৷সেখানে শিব লিঙ্গ মাটিতে বসা ৷ কষ্ঠি পাথরের শিববাহন ষাঁড়ের মূর্তি ৷ মহাপীঠ নিরূপম
গ্রন্থে এই পীঠের কথা বলা হয়েছে ৷ এই পীঠে একসময় ভয়ানক রঘু ডাকাত পুজো করে ডাকাতি করতে যেত ৷ সে নরবলি দিত বলে জনশ্রুতি আছে ৷আবার যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বাংলার ডাকাত " বইয়ে বলেছেন এখানে বেহারী বাগদী নামে এক ডাকাত পুজো করে নরবলি দিত ৷ ত্রিশ একর জঙ্গলে ঘেরা এই মন্দিরে আজও গা ছমছমে পরিবেশ ৷
মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ঈশাণী নদী। কাছেই রয়েছে শ্মশান। এই এলাকাটি আগে এত বেশি জঙ্গলে ভরা ছিল যে, দিনের বেলায়ও যেতে সাহস পেতেন না অনেকে। তবে এখন খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে মন্দিরটিকে। রাতে ঘুমানোর সময় কানে আসবে শিয়ালের ও প্যাঁচার ডাক, সকালে উঠবেন পাখির ডাকে। শান্ত পরিবেশে ভক্তি ভরে পুজো দিতে পারবেন আপনি। কথিত আছে একমনে মাকে ডাকলে সতীমায়ের উপস্থিতি অনুভব করা যায় আজও।
সত্য যুগে দক্ষ যজ্ঞে সতী শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। এর পর মহাদেব বীরভদ্রকে পাঠান দক্ষকে বধ করতে।সতীর দেহ নিয়ে তিনি শুরু করেন তাণ্ডবনৃত্য ।ফলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ বিভিন্ন ভাগে খণ্ডিত করেন। এই অংশ গুলো যেখানে পরেছে সেখানে শক্তিপীঠ স্থাপিত হয়েছে ।এগুলোকে সতীপীঠ বলে । এগুলি তীর্থে পরিণত হয়েছে। এখানে দেবীর অধর / নিচের ঠোঁট, পতিত হয়।
এরপর অনেক বছর কেটে যায়।এই স্থান জঙ্গল হয়ে ওঠে।তখন এ স্থানের নাম ছিল খুলারামপুর বা তুলারামপুর।পরবর্তীতে এই গ্রামের নাম দক্ষিণ ডিহি হয়।এই গ্রামে কিছু কৃষক বাস করত।তারা মাঠে চাষবাদ করত। ঈশানি নদীর ধারে অবস্থিত এ স্থান ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। দিনের বেলাতেও ওখানে কেউ যেত না। একদিন কৃষকরা চাষ করতে গিয়ে এক সাধুবাবাকে জঙ্গলে ধ্যানমগ্ন দেখতে পায়।তাড়া কৌতূহলী হয়ে দলবদ্ধভাবে তার কাছে যায় ও তাকে প্রণাম করেন।সাধুবাবা এখানে যজ্ঞ করেন।যজ্ঞ শেষে তিনি যজ্ঞস্থানে একটি ত্রিশূল পুঁতে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।চলে যাবার আগে বলেন, এটি একটি সতীপীঠ।
এখানে দেবী ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ ।এখানে দেবীর দন্তুরা চামুণ্ডা মূর্তি ।এখানে দেবীকে অধরেশ্বরী নামে পূজা করা হয়।এখানে আছে এক প্রাচীন শিলামূর্তি।মন্দিরের অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে।
সারা বছর এখানে ভক্তরা আসে।তবে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস এ পাঁচ মাস এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।বহু ভক্তের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে এখানে পূজা দিয়ে ।দোলের সময় এখানে বিশাল মেলা বসে। এখানে থাকার জন্য অতিথি নিবাস আছে।মন্দির থেকে ভক্তদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
আজ সমীরণ ক্ষীরগ্রাম যাওয়া ঠিক করল।সমীরণ বলল, জনশ্রুতি অনুসারে এই জলাশয়ের দক্ষিণ দিকে দেবী সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছে। দেবী যোগাদ্যা মায়ের স্থায়ী বাসস্থান এই জলাশয়ের নীচে। একমাত্র বৈশাখ সংক্রান্তিতে দেবীকে জল থেকে তুলে মূল মন্দিরে ভক্তদের সামনে রাখা হয়। এই দিন সবার অধিকার থাকে দেবীকে স্পর্শ করার পুজো দেবার। এই সংক্রান্তিতে সারাদিন ধরে মায়ের পুজো হয় ও গ্রামে মেলা বসে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এই দীঘির ঘাটে মা যুবতীর বেশ ধরে শাঁখা পড়েছিলেন। সেই উপলক্ষে বৈশাখ মাসের উৎসবে মাকে শাঁখা পড়ানো হয় এবং গ্রামের বধূরাও ওই দিন শাঁখা পরে। পুজো শেষ হলে ভোরবেলা দেবীকে আবার ক্ষীরদীঘিতে রেখে আসা হয়। এছাড়াও বছরের অন্যান্য বিশেষ সময়ে দেবীকে জল থেকে তুলে মন্দিরে এনে পুজো করা হলেও ভক্তরা দেবীর দর্শন পান না। একমাত্র বৈশাখ সংক্রান্তির দিনই দেবীর দর্শন করা যায়।
পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেবী যোগাদ্যাকে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং রাম। লংকায় রাম রাবণের যুদ্ধ চলাকালীন রাবণের ছেলে মহীরাবণ রাম ও লক্ষণকে মায়াজালে আবদ্ধ করে পাতালে নিয়ে আসে বলি দেবার জন্য।এই পাতালে মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী ছিলেন ভদ্রকালি তথা দেবী যোগাদ্যা ।প্রতিদিন দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হতো। কিন্তু মহীরাবণের সেই উদ্দশ্য সফল হয় নি। হনুমান মহীরাবণকে পরাজিত করে রাম ও লক্ষণ কে উদ্ধার করেন। মা যোগাদ্যা রামের কাছে থাকতে এবং তার হাতে পুজো নেবার ইচ্ছে জানালে রাম দেবীকে পাতালপুরী থেকে পৃথিবীতে এনে এই ক্ষীর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বর্ণনা কবি কৃত্তিবাসের রচনায় পাওয়া গেছে। যারা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মতে এই ক্ষীরগ্রাম থেকে বহু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার হয়েছে যেখানে যোগাদ্যা বন্দনার প্রায় ৪০টি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।
দেবী মূর্তিটি কালো কষ্টি পাথরের। দেবীর রূপ দশভূজা ও দেবী মহিষমর্দিনী। বলা হয় প্রাচীন মূর্তি চুরি যাওয়ায় বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ দাইহাটের নবীনচন্দ্র ভাস্করকে দিয়ে দশভূজা মহিষমর্দিনীর একটি প্রস্তর প্রতিমা তৈরি করিয়েছিলেন। এই প্রতিমাটিই ক্ষীরদীঘির জলের নীচে রাখা থাকে। তবে মূল মন্দিরে কোনো প্রতিমা নেই। গর্ভগৃহে বেদী রাখা আছে এই বেদীতেই মায়ের নিত্য পুজো করা হয়। মাকে আমিষ ভোগ প্রদান করা হয়। এই মন্দিরের একটু দূরে রয়েছে ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠের শিব মন্দির। একসময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, হারিয়ে যাওয়া মূর্তিটি নিয়ে। ক্ষীরদীঘি সংস্কারের সময় নতুন মূর্তির সাথে খোঁজ মেলে হারিয়ে যাওয়া মূর্তির। পুরনো মূর্তি ফিরে পাবার আনন্দে গ্রামবাসীরা আরও একটি মন্দির গড়ে তোলেন। এই মন্দিরেই রাখা থাকে পুরনো যোগাদ্যা মূর্তিটি। ফলত এখন গ্রামে গেলে সারাবছরই মায়ের দর্শন পাওয়া যায়। এবং বৈশাখ সংক্রান্তির সময় গ্রামের দুই মন্দিরেই সমান আরাধনা চলে।
ক্ষীরগ্রাম দেবী সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এখানে সতীর আঙুলসহ ডান পায়ের পাতা পড়েছিল। দেবীকে এখানে যোগাদ্যা রুপে পূজা করা হয়।
জানা যায়, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তি চন্দ এই গ্রামে যোগাদ্যার একটি মন্দির তৈরি করান। কিন্তু এরপর কোনও ভাবে হারিয়ে যায় প্রাচীন যোগাদ্যা মূর্তিটি। এরপরই সম্ভবত মহারাজার আদেশেই হারিয়ে যাওয়া মূর্তিটির অনুকরণে একটি দশভূজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি তৈরি করা হয়। তবে, পরবর্তী সময়েও নতুন তৈরি হওয়া মূর্তিটিও কিন্তু অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়ে ডুবিয়ে রাখা হত ক্ষীরদীঘির জলেই বলে জানা যায়। কেবল ৩১ বৈশাখ দেবীকে জল থেকে তুলে এনে সর্বসমক্ষে রাখা হত।
এর মধ্যে হঠাৎই ঘটে যায় এক অলৌকিক কাণ্ড। ক্ষীরদীঘি সংস্কারের সময় হঠাৎই নতুন মূর্তির সঙ্গেই উঠে আসে ‘হারিয়ে যাওয়া’ পুরনো যোগাদ্যা মূর্তিটিও। এরপর, মূর্তি ফেরত পাওয়ার আনন্দে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের সাহায্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটি মন্দির গড়ে তোলেন গ্রামের মানুষরা। সেই নতুন মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হন ফিরে পাওয়া দেবী মূর্তিটি। তাই এখন গ্রামে গেলেই দেবীরদর্শন পান বহিরাগতরা। পাশাপশি সংক্রান্তিতে দুই মন্দিরেই চলে দেবীর আরাধনা।
জানা যায়, এই ক্ষীরগ্রামে একটা সময় বেশ কিছু চতুষ্পাঠী ছিল। সেই সময়ের সাক্ষী বহু প্রাচীন পুঁথি। স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক জন পণ্ডিত এই গ্রামে বিদ্যাচর্চা করতেন। অন্তত ৪০টি যোগাদ্যা বন্দনা পুঁথি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়। তবে জানা যায়, সবথেকে আগে যোগাদ্যা বন্দনা লিখেছিলেন কবি কৃত্তিবাস। কবির মতে, রামায়ণের কালে মহীরাবণ বধের পরে তাঁরই পূজিতা ভদ্রকালী বা যোগাদ্যাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেন রামচন্দ্র।
মন্দির থেকে অদূরে একটি টিলার উপর দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ শিবের মন্দির। তাই এই গাঁয়ের নাম ক্ষীরগ্রাম, আদরের ক্ষীরগাঁ। মন্দির আর ক্ষীরদীঘি থেকে খানিকটা দূরে গ্রামের এক প্রান্তে ধামাসদীঘি। কথিত আছে, মহীরাবণকে কৌশলে বধ করে লক্ষ্মণ যখন পাতাল ত্যাগ করতে উদ্যাত হন, তখন রাবণের আরাধ্যা দেবী মহাকাল প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হনুমানের কাঁধে চেপে মহাকাল এসে ওঠেন মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামে। পুরাণ মতে, সেই সময় থেকেই দেবী মহামায়া বা মহাকালী কিংবা ভদ্রকালী যোগাদ্যা হয়ে রাঢ় বঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির হাতে পূজিতা হতে শুরু করেন। শাক্ত মতে এটি সতীপীঠ। দেবীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল এখানে। এখানে আলাদা কোনও কালী মূর্তি নেই । দেবীর রত্নবেদীতে কালীমন্ত্রে পুজো করা হয় দেবী যোগাদ্যাকে।
সমীরণ, বিপিন ও রিমি আজ ঠিক করল,উজানি হয়ে কাটোয়ার বাসায় ফিরবে ওরা।সমীরণ বলল,তুমি তো জানো বিপিন,অজয় নদের পাড়ে এই মন্দির অবস্থিত। মূল মন্দিরটিতে প্রথমে একটি বারান্দা আছে। তার ভিতরে আয়তাকার গর্ভগৃহ। এই গর্ভগৃহের মধ্যে মা মঙ্গলচণ্ডীর ছোটো কালো পাথরের দশভূজা মূর্তি রয়েছে। প্রাচীন মূর্তিটি নব্বইয়ের দশকে চুরি হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালে মল্লিক উপাধিধারী গ্রামের এক ধনী পরিবার বর্তমানের কষ্টিপাথরের দশভুজা মূর্তিটি নির্মাণ করে দেন। সেই থেকে এই কষ্টিপাথরের মূর্তিটির পূজা হচ্ছে। ২০০৬ সালে মন্দিরটি সারানো এবং বাড়ানো হয়েছে। মূল মন্দিরের সামনে একটি ছোট নাটমন্দির যোগ করা হয়েছে।
প্রত্যেকটি সতীপীঠ বা শক্তিপীঠে দেবী এবং ভৈরব অধিষ্ঠিত থাকে। দেবী হলেন সতীর রূপ। ভৈরব হলেন দেবীর স্বামী। উজানি সতীপীঠে দেবীর নাম মঙ্গলচন্ডী। উঁচু কালো রঙের পাথরের একটি শিবলিঙ্গ হল দেবীর ভৈরব । ভৈরবের নাম কপিলাম্বর। অনেকে কপিলেশ্বর বলেও উল্লেখ করেন। শিবলিঙ্গের সামনে নন্দীর কালো পাথরের একটি ছোট মূর্তি আছে। শুধু তাই নয়, ভৈরবের বাঁদিকে একটি বজ্রাসন বুদ্ধমূর্তিও আছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই মূর্তিটি পাল যুগের।কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত ভ্রমরার দহ, মাড়গড়া, শ্রীমন্তের ডাঙা প্রভৃতি স্থানগুলি উজানিতেই। বর্তমানে সেই স্থানগুলির হদিশ পাওয়া যায় না। কথিত আছে সপত্নীপীড়িতা খুল্লনা উজানির কাছে ছাগল চরাতেন। যে স্থানে ভাত রান্না করে মাড় গালতেন সেই স্থানটি মাড়গড়া নামে পরিচিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি দত্ত এই ভ্রমরার দহ থেকেই ডিঙায় চেপে সিংহলে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। আবার তাঁর পুত্র শ্রীমন্তও মঙ্গলচণ্ডীর চরণে পুজো দিয়ে সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে যেতে ভ্রমরার দহ থেকেই সাত খানি ডিঙা ভাসিয়েছিলেন। যে স্থানে দাঁড়িয়ে সাতখানি ডিঙা দেখেছিলেন সেই স্থানটি শ্রীমন্তর ডাঙা নামে পরিচিত ছিল। সেগুলির সন্ধান বর্তমানে না পাওয়া গেলেও উজানির সতীপীঠ-কপিলাম্বর রয়েছেন স্বমহিমায়। দেবীর মূল পুজো হয় শারদীয়া দুর্গাপুজোর সময়। পুজো চলে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। এটি সতীপীঠ হওয়ার কারণে পুজোয় আলাদা করে মূর্তি আসে না এবং নবপত্রিকা আনা হয় না। শুধু ঘট বারি আনা হয়। বছরে তিনবার ঘট বদল হয়। প্রথম ঘট আসে বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার এবং বাৎসরিক পুজো হয়। এরপর ঘট আসে জিতাষ্টমীর পরদিন, যাকে বোধনের ঘট বলা হয়। তারপর ঘট আসে দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন। এছাড়াও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো হয়। এখানে বলিপ্রথা চালু আছে। দুর্গাপুজোর সপ্তমী এবং অষ্টমীতে চালকুমড়ো, নবমীতে চালকুমড়ো, কলা, আখ এবং ছাগ বলি হয়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ। লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে কালে কালে যুক্ত থাকে পরিপুষ্ট গভীর আবেগ, ভক্তির উচ্ছ্বাস, অন্ধবিশ্বাসের ঐকান্তিকতা। শ্রীমন্ত এই স্থান থেকে সিংহলে যাত্রা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই উজানি শক্তিপীঠের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস আজও অমলিন।
পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এখানে সতীর বাঁ হাতের কনুই পড়েছিল। এখানে অধিষ্ঠিত দেবী মঙ্গলচন্ডী এবং ভৈরব হলেন কপিলাম্বর বা কপিলেশ্বর। পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছে কোগ্রামে অবস্থিত এই সতীপীঠ।
পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মাতা সতী নিজের বাপের বাড়িতে বাবার কাছে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সেখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। মাতা সতীর দেহত্যাগের খবর মহাদেবের কাছে পৌঁছতেই মহাদেব সেখানে উপস্থিত হন। সতীর মৃতদেহ দেখে ক্রোধে উন্মত্ত মহাদেব সেই দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য চালু করেন। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী ধ্বংসের আশঙ্কায় শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা মাতা সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে খণ্ডিত করেন। সেই দেহখন্ডগুলোই যে যে স্থানে পড়েছিল সেখানে একটি করে সতীপীঠ প্রতিষ্ঠা হয়। বলা হয় কোগ্রামের সতীপীঠ উজানিতে মাতা সতীর বাঁ হাতের কনুই পড়েছিল।যার সাধনায় অনেক অসাধ্যকে সাধ্য হতে দেখেছেন ভারতবাসী। এদেশের প্রতিটি ঘরে রয়েছে ঈশ্বর আরাধনার বাতাবরণ। রয়েছে সেই মহাশক্তির ছায়া। বাকি ভারতের সঙ্গে তুলনা টানলে দেখা যাবে যে এই বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনকী এখানে নাস্তিকতার আড়ালেও চলে দৈব সাধনা, পুজো-অর্চ্চনা, জপ-তপ। চলে তন্ত্রচর্চাও। যার সাহায্যে জীবনের অনেক কঠিন পরিস্থিতিকে সহজে সামলে নেন ভক্তরা।
এই বাংলার আরও বড় সুবিধা যে এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি শক্তিপীঠ। বেশ কয়েকটি সিদ্ধপীঠ। এই বাংলায় জন্ম নিয়েছেন একের পর এক মহাপুরুষ। এমনই এক শক্তিপীঠ হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কোগ্রামের উজানি। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী যেখানে দেবী সতীর বাম হাতের কনুই পড়েছিল। এখানে দেবী মণ্ডলচণ্ডী। আর ভৈরব কপিলাম্বর বা কপিলেশ্বর।
রিমি বলল,এছাড়া পূর্ব বর্ধমান জেলায়,ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মা,কেতুগ্রামের বাহুলক্ষীতলা ও অট্টহাস সতীপীঠ উল্লেখযোগ্য সতীপীঠ বলে পরিচিত। সমীরণদা আজকের রাতটা আমাদের বাসায় থাক।সমীরণ বলল,নিশ্চয়ই।
তারপর রাত হলে বিপিন সমীরণকে পাঁচলাখ টাকার চেক দিয়ে বলল,তুমি তোমার আশ্রমের উন্নতি করো।আমি ও রিমি বয়স হলে তোমার সঙ্গি হব।
সমীরণ বলল,টাকায় আমার কাজ নেই।তবু আশ্রমের সেবার কাজে লাগে ভক্তদের সাহায্য। আমার আশ্রমের প্রবেশদুয়ার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে চিরকাল।সমীরণ সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ল অজানার টানে।
...(সমাপ্ত)...
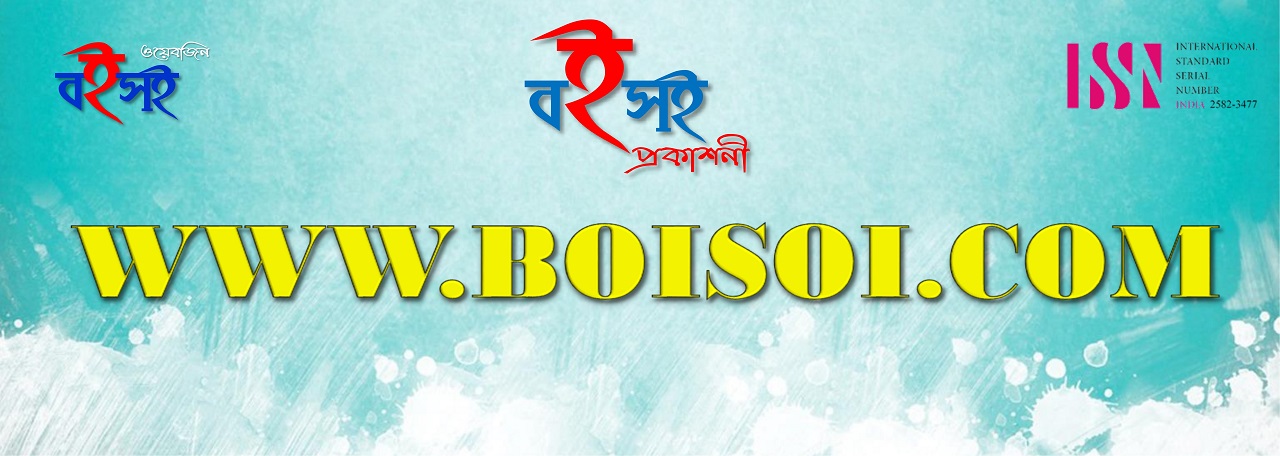







No comments:
Post a Comment