 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান —উপেক্ষিতা মধুমতীদের কাব্য
বৈশাখের পড়ন্ত বিকেলে রোদ একটু নরম হলে মধুমতী বাগানের মাঝখানে ঘন গাছঢাকা অঞ্চলটাতে গিয়ে দাঁড়াতে ভালোবাসে। মহাকাব্যে তার নামের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু নাম তো একটা থাকতেই হবে, না থাকলে কেমন যেন মৃতপ্রায় বৃক্ষের মতো মনে হয়, তাই তাকে সরস সতেজ করে পরিবেশন করবার অভিপ্রায়ে নামকরণ করা হল মধুমতী। এই গাছঢাকা অঞ্চলে এসে যেন নিজের প্রকৃতিকে অনুভব করবার অবকাশ পায় মধুমতী। এই নিরালা বিকেলটুকুই তার একান্ত নিজের। বাগানে অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই মধুমতীর অনুমতি ছাড়া। গৃহে যাঁরা তার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন তাঁদের সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ে আসতে হয়। অভিজাত লোকমনোরঞ্জনকারিণী হিসেবে মধুমতীর রাজ্যজোড়া খ্যাতি। নগরীর তথা রাজ্যের কূটনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে অনেকসময় মধুমতীকে পুরোভাগে আসতে হয়েছে এবং যথোচিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। বহু দেশীয় বিদেশীয় অভিজাত মধুমতীর সঙ্গ যাচনা করেন। এতে অন্য অন্য মনোরঞ্জনকারিণীদের ঈর্ষা হলেও মধুমতীর কিছু এসে যায় না।
বাগানের মাঝখানে একটি স্বচ্ছ জলের কূপ। এই স্ফটিক সদৃশ জলেই মধুমতী নিজেকে আপন করে দেখতে পায়। অট্টালিকার মহার্ঘ দর্পণে সে তো অন্যের রূপমোহিনী, সেখানে ছলাকলা বিলোল কটাক্ষের মায়াময় জগৎ। সেখানে নিজের সম্বন্ধে ভাবার নিজেকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবার অবকাশ কোথায়!বাহ্যিক বসনভূষণ থেকে মুক্ত হয়ে মধুমতী আরামের এই অবসরটুকুকেই পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে। মিশে যায় আদিম প্রকৃতির সঙ্গে। কাচের মতো স্বচ্ছ শীতল জল কূপ থেকে তুলে স্নান করে, অঙ্গমার্জনা করে দীর্ঘ সময় ধরে। ভেষজ সুগন্ধী জলে পুনরায় গাত্রধৌতি পর্ব সমাধা করে। সমস্ত দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তির অবসান হয়। নিজের সুরভিত দেহের সুঘ্রাণে আপ্লুত মধুমতীকে সন্ধ্যার মুখে প্রস্তুত হতে হয় অভিজাত সঙ্গলিপ্সুদের আপ্যায়নের জন্য।
কিন্তু আজ তার দিনলিপি একটু অন্যরকম। আজ সে কোনো অতিথির আপ্যায়ন করবে না। তার প্রধানা পরিচারিকা অট্টালিকার মূল দ্বারে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেক অভিজাত অতিথিকে বিনীতভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে। অট্টালিকার প্রতিটি কক্ষ দীপালোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কূপের সুশীতল সুগন্ধীযুক্ত জলে স্নান করে, সারা দেহে সুগন্ধী ফুলের নির্যাস মেখে সালংকারা সুসজ্জিতা মধুমতী প্রস্তুত হয়ে আছে রাজদর্শনের জন্য। মধুমতী আজ উত্তেজিত এবং বিস্মিতও বটে। এই অঙ্গদেশের রাজা দশরথসখা লোমপাদ। রাজা লোমপাদ বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তান্বিত। মধুমতী এ-সংবাদ জেনেছে গোপনে তার চৌষট্টিকলার প্রয়োগনৈপুণ্যের জোরে। রাজার ঘনিষ্ঠ কোনো এক বন্ধু এ-সংবাদ দিয়ে ফেলেছেন অনবধানবশত। কিন্তু কারণটা পরিষ্কার করে জানায়নি। তবে মধুমতীর কাছে এটুকু সংবাদ যথেষ্ট। সে ঠিকই অনুসন্ধান করে নিতে পারবে রাজার মাথাব্যথার কারণ। পেরেছেও।
২
রাজা লোমপাদ এক অভিজাত নাগরিকের ছদ্মবেশে এলেন। মধুমতী পাদ্য-অর্ঘ্য সহকারে তাঁর যথাবিধি আপ্যায়ন করলে রাজা তুষ্ট হয়ে বললেন, ‘কামিনী, তুমি আশাকরি কিঞ্চিৎ অবহিত রাজ্যের দুরবস্থা সম্পর্কে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা আমার প্রতি রুষ্ট। জানি না কোন অপরাধে তাঁরা আমাকে অপরাধী করলেন। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যে বারিবর্ষণে বিরত হয়েছেন। তীব্র জলাভাব দেখা দেবে অচীরেই। ধনেপ্রাণে মরতে হবে সকলকেই। ধরিত্রীর বুকের রস ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন ইতোমধ্যেই কানে এসেছে আমার। অনাবৃষ্টির করাল গ্রাস থেকে তুমি আমি সাধারণ মানুষ কেউই নিস্তার পাব না। তবে একটা উপায় দেখতে পেয়েছি কিন্তু তার উপযুক্ত প্রয়োগ নির্ভর করছে তোমার কর্মকুশলতার ওপর।’
মধুমতী কিঞ্চিৎ বিস্মিত। সে ঘাড়খানা ঈষৎ হেলিয়ে সরাসরি চেয়ে থাকে রাজার দিকে। রাজা বললেন, ‘এক মহাত্মা মুনি এই আসন্ন বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরামর্শই আমি উপযুক্ত বলে মনে করছি। তিনি বলেছেন কৌশিকী নদীর তীরে বিভাণ্ডক নামে এক মুনি সপুত্র বাস করেন। তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে এরাজ্যে আনতে পারলেই ইন্দ্র অনাবৃষ্টির কালে জলবর্ষণ করবেন।’
মধুমতী বলে, ‘কাউকে পাঠিয়ে মুনিপুত্রকে আমন্ত্রণ করুন’
রাজা ঈষৎ হেসে বললেন, ‘তা হলে তো ভাবনা ছিল না বা তোমার মহার্ঘ সময় নষ্ট করারও প্রশ্ন ছিল না। একাজ অন্য কারোকে দিয়ে হওয়ার নয়।’
মধুমতী ভ্রূ কুঞ্চন করে বলে, ‘কেন?’
রাজা এবার মধুমতীর দিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন তারপর বলেন, ‘শোনো, বিভাণ্ডক মুনি বহুকাল ধরে তপস্যা করে যখন পরিশ্রান্ত তখন শ্রান্তি নিবারণের জন্য তিনি একদিন বিশাল হ্রদে অবগাহন করে স্নান করছিলেন। এমন সময় অপ্সরা উর্বশীকে হ্রদ সন্নিহিত স্থানে দর্শন করে কামপ্রবাহে মুনিবর রোমাঞ্চিত হন। তাঁর রেতঃ স্খলিত হয়। কোনো এক তৃষিতা হরিণী জলপান করতে গিয়ে নিঃসৃত শুক্র জলের সঙ্গে পান করে। তারপর সেই হরিণী গর্ভিণী হলে সময়ান্তে একটি মানব সন্তান প্রসব করে, যার মস্তকে একটিমাত্র শৃঙ্গ বর্তমান। এই শিশুই বিভাণ্ডক মুনির ঔরসজাত সন্তান ঋষ্যশৃঙ্গ। এরপর মুনিবর তাঁর পুত্রকে নিয়ে ঋষভকূট পর্বত অতিক্রম করে কৌশিকী নদীর তীরে এক মনোরম স্থানে আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। বর্তমানে মুনিকুমারও কঠোর ব্রহ্মচর্য তপস্যায় নিমগ্ন। মুনিকুমার জন্মাবধি কোনো নারীর মুখদর্শন করেননি। পিতা ভিন্ন অন্য পুরুষও তিনি দেখেননি। লোকমোহিনী, ওই তেজস্বী মহাতাপস মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলে ও কৌশলে এ রাজ্যে আনতে হবে। বুঝতে পারছ তো তুমি ছাড়া একাজ অন্য কারোর পক্ষে করা একপ্রকার অসম্ভব।’
মধুমতী বিলোল কটাক্ষে রাজার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে রাজা কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, ‘কোনো চিন্তা কোরো না কামিনী রাজ-ঐশ্বর্যে মুড়ে দেব তোমাকে। শুধু কার্যোদ্ধার করে আমাকে চিন্তামুক্ত করো। আর একাজে তোমার যা যা আবশ্যক তার একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।’ নৃপতি লোমপাদ সম্বলহীন কপর্দকশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মধুমতীর সম্মতিলাভের অপেক্ষায়।
উন্মুক্ত বাতায়ন পথে মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস গৃহের অভ্যন্তরভাগকে মনোরম করে তুলেছে। বাগানের সুগন্ধী ফুলের সৌরভে গৃহ সুরভিত। মধুমতী একটু সময় নিয়ে ভাবল। তারপর রাজাকে বলল, ‘মহারাজ আপনি কীভাবে ঘোরতর সুনিশ্চিত যে কার্যোদ্ধার আমার দ্বারাই সম্ভব?’
রাজা মৃদু হেসে বললেন, ‘দেখ মধুমতী, তোমার তূল্য সুন্দরী ষোড়শকলাবিলাসিনী এবং প্রত্যুৎপন্নমতী নারী এরাজ্যে তো নেই-ই, আমার বিশ্বাস প্রতিবেশী বন্ধু-রাজ্যগুলোতেও নেই। সাধারণ বারনারীরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কোনো পুরুষের দ্বারা একাজ হওয়ার নয়, কেননা ওই মহাতেজা তপস্বীর সমীপে অকুতোভয় হয়ে কোনো পুরুষের বাক্যালাপ করা তো দূরস্থান, কয়েক পল স্থিতু হতে গেলেও মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়বে। আগেই বলেছি মুনিকুমার কঠোর তপস্বায় নিমগ্ন আর জন্মাবধি পিতা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখদর্শন করেননি, নারীর মুখ তো নয়ই । তাই তাঁর তপস্বা ভঙ্গ করে এবং পিতার দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে হলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে যা পুরুষের অসাধ্য, সাধারণ নারীরও সে সাধ্য নেই কেবল তুমিই সেই সুলক্ষণা যার ওপর নির্ভাবনায় নির্ভর করা যায়। আমার মন্ত্রি এবং আমাত্যগণ তোমাকে স্মরণ করায় তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তোমাকে কিছু বলে থাকবেন। তোমার জননী আমার পরিচিতা।’ শেষের কথাটি বলতে গিয়ে রাজা লোমপাদের কণ্ঠ ঈষৎ কম্পমান হয় আর রাজোচিত দৃপ্ত ভঙ্গীতেও কেমন জড়তা নেমে আসে। তা মধুমতীর দৃষ্টি এড়ায় না। মধুমতী মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায়।
বয়সকালে তার মাতাও অভিজাত মনোরঞ্জনকারিণী ছিলেন। রাজপুরুষরাই ছিলেন তাঁর অতিথি। একসময়ে তার মাতা এই রাজার বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। আজকের রাজা সেসময়ে সদ্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। যুবরাজ লোমপাদের ঔরসে তার জন্ম হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়। একথা সে মাতার কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে জেনেছে। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস! রাজপুত্রী হয়েও সে বেশ্যাকন্যা। আজ তার পরিচয় কেবল অভিজাত বারবধূ। তার প্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রাজার উচ্চবেতনভুক কর্মচারীর ক্ষমতা সে ভোগ করে। প্রশাসন তার নিরাপত্তার জন্য সবিশেষ তৎপর। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিলাসবৈভব রাজপুরীর চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। তবুও যেন কোথায় একটা কাঁটা আটকে যায় নিজের কাছে, সামাজিক সম্মান অর্জনে কেননা সে যে বহুগম্যা এই কালিমা তো জীবদ্দসায় মুছবে না। মৃদু হাস্য ক’রে মধুমতী রাজাকে প্রণাম করে । তারপর মাথা তুলে চোখে চোখ রেখে বলে, ‘রাজা পিতার সমান। মহারাজ আপনার আদেশ পিতৃ-আজ্ঞার মতোই অবশ্য পালনীয়। আমি যথোচিত কৌশল অবলম্বন ক’রে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আমাদের রাজ্যে আনবার চেষ্টা করব। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।’
রাজা লোমপাদ আশীর্বাদ করতে গিয়ে একটু হলেও শিহরিত হলেন। দক্ষিণ হস্ত কেঁপে উঠল। তারপর কোনোক্রমে মধুমতীর সুরম্য ভবন থেকে পলায়ন করলেন। অষ্টাদশী মধুমতীর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল রাজার মুখমণ্ডল বিষাদে ক্লিষ্ট। এ বিষাদ রাজ্যের বর্তমান সংকটের জন্য নয়, এ বিষাদ অব্যক্ত অপরাধবোধপ্রসূত।
৩
যাত্রার দিন সমাগত। রাজার কাছ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ধনরত্নাদি পেয়ে মধুমতীর মাতা এক বৃহদাকার নৌকোয় বৃক্ষলতা, পুষ্প, মৃগ ইত্যাদি শোভিত করে এক কৃত্রিম মায়াময় সুরম্য আশ্রম নির্মাণ করলেন। মধুমতী এবং তার মাতা ছাড়াও আরও কয়েকজন রূপযৌবনবতী তরুণীর কলকণ্ঠে মুখর মায়া-আশ্রম এক শুভক্ষণ দেখে প্রভাতকালে ভেসে পড়ল নদীতে। ঋষভকূট পর্বতকে বামপার্শ্বে রেখে পর্বতের অপর প্রান্তে বয়ে চলা কৌশিকী নদীর ওপর নৌকো এসে পড়ল। পুণ্যতোয়া স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জলরাশির ওপর মায়া-আশ্রম ভেসে চলেছে। কিছুদূরে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম। পশ্চিম আকাশে অস্তগত সূর্যের মায়াবী আলপনা মায়া-আশ্রমের শোভা দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মধুমতী নৌকোর একপাশে উচ্চ-আসনে উপবিষ্ট হয়ে জলের ওপর রক্তিম আলোর প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একান্তে ভাবতে থাকে, রাজকুমারী শান্তা তারই সমবয়সী অথচ দুজনের সামাজিক অবস্থার কত অসাম্য। হয়তো উভয়েরই পিতা একজনই তবু সে বেশ্যাকন্যা আর তিনি রাজপুত্রী। এ সবই মধুমতীর অনুমান।
বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমের অদূরেই নৌকো বাঁধা হল। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত মধুমতী ও অন্যান্য সকলের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে লাগল পরিচারকেরা। অনতি বিলম্বে পাচক নৈশ-আহারের প্রস্তুতি সমাধা ক’রে মধুমতী ও অন্যান্য সঙ্গিনীদের আহার পরিবেশন করে। নৈশ-আহার সম্পন্ন হলে সকলেই নিদ্রাভিভূত হল। মায়া-আশ্রম অন্ধকারের নিজস্ব আলোয় মুড়ে গেল। মায়া-আশ্রমের কয়েকটি কক্ষ আছে। নির্দিষ্ট করা আছে কোন কক্ষে কে থাকবে। একটি পাকশালা এবং তৎসন্নিহিত দুটি কক্ষ পাচক ও পরিচারকদের জন্য। মাঝিমাল্লারা খোলা অংশেই থাকবে এবং পাহারা দেবে। তবে আশ্রমে মধুমতী এবং অন্যান্য তরুণীরা ছাড়া কেউই বাইরের অংশে দৃশ্যমান হবে না। এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে আশ্রম-নৌকোখানা। আশ্রমের পুরোভাগে শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে, যা গাভি মৃগ ইত্যাদি পশুর চারণক্ষেত্র। একপাশে পুষ্পোদ্যান রকমারি পুষ্পরাজির শোভা ও সৌরভে আমোদিত। অন্য প্রান্তে ফলের বাগিচা, রসাল ফলভারে বৃক্ষাদি নমিত হয়ে আছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা মধুমতী তার মাতার সঙ্গে পরামর্শ ক’রে বাস্তবায়িত করেছে।
৪
কশ্যপ গোত্রজাত মহাত্মা বিভাণ্ডক প্রাতঃকালে ফলমূলাদি আহরণের নিমিত্ত কুটির থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ গভীর তপস্যায় মগ্ন। অতি প্রত্যূষে স্নান ও অঙ্গমার্জনা সেরে সুগন্ধী পুষ্পরাশি দুই বাহুমূলে পিষ্ট করে অনিন্দ্যসুন্দর বক্ষ চন্দনচর্চিত করে অতি সুরভিত তনু এবং প্রফুল্ল মন নিয়ে জটাজুটধারী মুনিকুমারের সামনে এসে দাঁড়াল মধুমতী। পরনে স্বচ্ছবসন। সুদীর্ঘ কেশ পরিপাটি করে সোনার সুতো দিয়ে বেণী আকারে বাঁধা। কোমরে সোনার মেখলা। হাতে কানে গলায় স্বর্ণালঙ্কারের শিঞ্জন। সুঠাম পদযুগলে সুবর্ণ নূপুরের নিক্কন। মহাতেজা ব্রহ্মচারীর সম্মুখে মধুমতীর আগমন আশ্রমের পরিবেশকে আরও মনোরম করে তুলল। আশ্রম পরিমল পবনে পরিপূর্ণ হল। কী এক অভূতপূর্ব পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠছে মুনিকুমারের মন। ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখলেন এক অপরিচিত ব্রহ্মচারীকে। মধুমতীর লোভনলীলাময় দেহলতা মুনিকুমারের মনে অপার বিস্ময় সৃষ্টি করল।
তিনি মনে মনে ভাবলেন—ইনি তো তাঁর বা পিতার মতো নন। এঁর চীরবসন তাঁর মতো নয়। পদ্মপলাশ তূল্য আয়ত নয়ন, নির্মল সুগন্ধযুক্ত সুদীর্ঘ জটা সুবর্ণসূত্রে গাঁথা, স্বচ্ছ চীরবসনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান বক্ষের দুটি মনোহর রোমহীন মাংসপিণ্ড—এ তো তাঁর বা পিতার সঙ্গে মেলে না! শুধু তা-ই নয় এঁর শ্মশ্রুগুম্ফহীন অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী মনে পুলক সৃষ্টি করে, এই ব্রহ্মচারীর সুবর্ণ মেখলাবেষ্টিত ক্ষীণ কটিদেশ এবং হাত ও পা-এ জপমালার মতো অত্যাশ্চর্য শব্দকারী মালা কেমন যেন রোমাঞ্চিত করে। ব্রহ্মচারীর মৃদু হাস্য দেহে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার করে—এমন ভাবনায় যখন মুনিকুমার বিভোর ঠিক তখনই মধুমতী লীলায়িত ছন্দে মুনিকুমারকে আলিঙ্গন ক’রে সুলোলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে মহাতেজা ব্রহ্মচারী! আশ্রমে আপনারা সকলে কুশল তো? ফুল, ফলমূলাদি ঠিক ঠিক পাচ্ছেন কি না তা দেখতে এসেছি।’
ঋষ্যশৃঙ্গ রোমাঞ্চিত ও আপ্লুত হয়ে বললেন, ‘হে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ব্রহ্মচারী আমার কুটিরে পক্ক ভল্লাতক, আমলক, ধন্বন, ইঙ্গুদ, প্রিয়লক ইত্যাদি ফল আছে এইসব দিয়ে আপনার পাদ্য-অর্ঘ্য সাজিয়ে যথাবিধি সৎকার করি।’
মধুমতী সুকৌশলে মুনিকুমারের অর্ঘ্য বর্জন করে মুনিকুমারকে দুগ্ধজাত প্রস্তুত উৎকৃষ্ট আহার্য, সুস্বাদু পানীয়(মদ্য বিশেষ), গন্ধমাল্য, বিচিত্র সৌখিন বসন ও নানাবিধ ক্রীড়াসামগ্রী দান করে হাস্য পরিহাসে রত হল। মধ্যে মধ্যে সুযোগমতো সে মুনিকুমারকে শরীর দিয়ে স্পর্শদান করতে থাকে। কখনও বা নৃত্যগীত প্রদর্শন করতে থাকে। আবার অবসর মতো তার উদ্ধত কোমল স্তনদ্বয় মুনিকুমারের বক্ষে চেপে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই শ্মশ্রুগুম্ফ সযত্নে সরিয়ে মুনিকুমারের ওষ্ঠে নিজের নরম রক্তাভ ঠোঁট চেপে ধরে গভীর চুম্বনে মুনিকুমারকে হর্ষোৎফুল্ল ক’রে তোলে। হর্ষে পুলকে উত্তেজনায় মুনিকুমার আসন ছেড়ে উঠে দণ্ডায়মান হলেন। তারপর মধুমতীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, ‘হে তাপস! আপনার আশ্রম কোথায়? কোন ব্রত আচরণ করেন আপনি? কী সুন্দর নমনীয় সুগন্ধিত দেহ আপনার মুনিবর! আমার দেহের প্রতিটি রোমকূপে কী এক তরঙ্গ লেগেছে। মুনিবর! আপনার আশ্রম দর্শনের নিমিত্ত আমি উদগ্রীব।’
মুনিকুমার প্রলোভনের বশবর্তী হয়েছেন বুঝতে পেরে মধুমতী হোম করবার ছলে আশ্রম থেকে লীলায়িত ছন্দে নিষ্ক্রান্ত হল। আবিষ্ট মুনিকুমার তড়িদাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রইলেন। স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করতে থাকেন মধুমতীকে যতক্ষণ না সে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। এরপর মুনিকুমার গভীর সংকটে পড়লেন। একাগ্রচিত্তে ধ্যানে বসতে পারছেন না, থেকে থেকেই অস্থির হয়ে উঠছেন। কেবলই মনে হচ্ছে এই মহাজগতে তিনি বা পিতা ছাড়াও এমন মানুষও বাস করেন! বিস্ময়ের অবধি নেই তাঁর। বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো ভাবনা সাময়িকভাবে মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করেছে। মহাত্মা বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে দেখেন পুত্র কাতর এবং অস্বাভাবিক হয়ে রয়েছেন। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। পিতা পুত্রের কাছে এই বিহ্বলতার কারণ জানতে চাইলে ঋষ্যশৃঙ্গ অকপটে প্রাতঃকালের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। শুধু তা-ই নয় তিনি যে সেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গলাভে অতিশয় প্রীত হয়েছেন এবং আবারও তাঁর সঙ্গলাভ করতে উৎসুক তাও পিতাকে জানাতে ভুললেন না।
আশ্রমের চারিদিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ক’রে এবং উপঢৌকনাদি অবলোকন ক’রে মহাত্মা বিভাণ্ডক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এটা কোনো নারীঘটিত ঘটনা। ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম থেকে কোনো নারীকে দেখেননি তাই তাঁর বিহ্বলতা উত্তেজনা মাত্রা ছাড়িয়েছে। প্রকাশভঙ্গিও অসংলগ্ন। নিশ্চয় অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো বারবণিতা পুত্রের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়েছে। তৎক্ষণাৎ অন্বেষণে বের হলেন মহাত্মা বিভাণ্ডক। সর্বত্র অন্বেষণ করেও মায়া-আশ্রমের কোনো সন্ধান করতে পারলেন না তিনি। তিনদিন পর ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ব্যর্থ মনোরথে শেষ রাতে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করলেন মুনিবর।
৫
এদিকে মধুমতী মায়া-আশ্রমে পদার্পণ করামাত্র তার মাতা অতি সচেতনভাবেই মায়াসৃষ্ট নৌকো-আশ্রম এমন স্থানে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যেখান থেকে সমস্ত কিছু দৃশ্যমান হলেও তাঁরা কারোর দৃষ্টিগোচর হবেন না। তিনদিন ধরে মায়া-আশ্রমে বসে মধুমতী ভেবে চলেছে অনেক কথা। মুনিকুমারের সঙ্গে এই কপট খেলা সে মন থেকে মানতে পারে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে মানুষের শক্তি-জ্ঞান-মেধাকে দেবতারা ভয় পান। তা না হলে কেন কপট ছলনার আশ্রয় নিয়ে বার বার মানুষের একাগ্রতা অর্থাৎ তপস্যাকে নষ্ট করতে তৎপর হন? ঋষ্যশৃঙ্গ মহান তেজস্বী ঋষি। জন্মাবধি পিতা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখেননি, নারীর মুখদর্শন তো দূরস্থান। এঁর কঠোর তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্যধর্ম চর্চায় দেবরাজ নিশ্চয়ই ভীত এবং ত্রস্ত, নইলে কেন তিনি অঙ্গরাজ লোমপাদকে বিপাকে ফেলে বাধ্য করবেন ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসবার জন্য? দোষে গুণে মেশানো মানবজগৎ। অঙ্গরাজ লোমপাদ হয়তো কোনো কারণবশত পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছিলেন, আর সেই ত্রুটিকেই সুযোগ মতো সদ্ব্যবহার করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আর দেবতাদের এই প্রিয় কাজকে বারংবার সফল করতে এগিয়ে আসতে হয়েছে তার মতোই কোনো না কোনো বহুভোগ্যা লাস্যময়ী সুন্দরী যুবতীদের। অথচ তারা চিরকালই সমাজের নীচের তলায় পাদপ্রদীপের অন্ধকারেই থেকে গেল ব্রাত্যজন হয়ে। স্বর্গের অপ্সরীই হোক আর মর্ত্যের রাজা বা রাজপুরুষদের লীলাসঙ্গিনীই হোক কাজ তো একই। হয় প্রভুর মনোরঞ্জন করা নয়তো প্রভুর হুকুমে অন্যের চিত্ততোষ ঘটিয়ে প্রভুর স্বার্থ রক্ষা করা। তারা তো ক্রীড়ার সামগ্রী। স্বার্থ আর ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে তারা তো ক্রীড়নক বই আর কিছুই নয়। ধন ঐশ্বর্যের প্রাচূর্যে সমাজের অভিজাতদের তুলনীয় হলেও নারীর প্রকৃত মর্যাদা বা সম্মানের কানাকড়িও কেউ দেয় না। অথচ তাদের কলানৈপুণ্য এবং বুদ্ধিমত্তায় রাজ্য পার পেয়ে যাচ্ছে বহু সংকট থেকে সে স্বর্গরাজ্যই হোক কিংবা মর্ত্যধাম। কিন্তু তাদের মতামত দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের মতপ্রকাশ তো অমার্জনীয় অপরাধ। তারা তো কেবল রাজপুরুষদের ক্রীড়ার সামগ্রী। তাদের সংসার থাকতে নেই, সন্তান থাকতে নেই, সুস্থভাবে স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার থাকতে নেই। বুকের অভ্যন্তরভাগে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত বাষ্প কণ্ঠাতে এসে আটকে থাকে মধুমতীর। কেমন ব্যথা লাগে গলায়। চোখ দুটো ভিজে ওঠে।
এই নিষ্পাপ অনুরক্ত ঋষিকুমারকে নিয়ে মধুমতীর ইচ্ছে করে পৃথিবীর কোনো নির্জন প্রদেশে গিয়ে সংসার পাতে। প্রথমে ঋষ্যশৃঙ্গের মস্তকোপরি শৃঙ্গ দেখে মধুমতীর মনে কিঞ্চিৎ বিরাগ জন্মেছিল। পরে রাজাজ্ঞার কথা স্মরণ করে নিজের কাজে মন দিয়েছিল। সে তো স্বেচ্ছায় আসেনি, রাজার আদেশে অর্থের বিনিময়ে সে এসেছে নির্দিষ্ট কাজে। এখানে বিরাগ অনুরাগ শোভা পায় না। আর তার পেশার ধর্মও তো তাই। কিন্তু ক্রমে যেন এই মহাতেজা তাপসের শিশুসুলভ সরলতা আর অদ্ভুত তেজস্বী অবয়বের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। নিজেও আনন্দে শিহরিত হত ওই নিষ্পাপ তপস্বীর দেহ স্পর্শ করে। বিরাগের ওপর অনুরাগের স্তর জমতে শুরু করল। নারীর স্পর্শে ঋষিকুমারে জাগ্রত পৌরুষকে সে নিজের মধ্যে ধারণ করতে চায়। জায়া ও জননী হয়ে সুখীগৃহকোণ রচনা করতে একান্তভাবে ইচ্ছুক মধুমতী। সে এটুকু বুঝতে পেরেছে ঋষিকুমার যে অপার্থিব আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন, তাতে তিনি তার দ্বারা পরিচালিত হবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা তো হওয়ার নয় কেননা, সে রাজার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার কাজ শুধুমাত্র অঙ্গদেশে নিয়ে আসা। যদিও সে অনুমানের ওপর নির্ভর করে উপলব্ধি করেছিল তারই সমবয়সী রাজকন্যা শান্তা মুনিকুমারের স্ত্রী হবেন। কিন্তু এখন কেবল অনুমান নয় এ তার স্থির বিশ্বাস কারণ যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করলে গণনা সেই অভিমুখই নির্দেশ করছে। সুচতুর দেবরাজ ইন্দ্র কেবল জলবর্ষণের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনয়ন করতে বাধ্য করছেন না, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্মচর্যব্রত থেকে ঋষিকুমারকে বিরত করা। আর সেই ব্রত যদি ভঙ্গই হল, তবে তো মুনিকুমারের স্ত্রীগমন অবশ্যাম্ভাবী। আর সেক্ষেত্রে রাজকুমারী শান্তাই তাঁর উপযুক্ত ভার্যা। তারই পেড়ে দেওয়া ফল ভোগ করবেন রাজপুত্রী শান্তা। রুক্ষ শুষ্ক অঙ্গদেশ তারই পরিশ্রমে হয়ে উঠবে আবার শস্যশ্যামল। অথচ সে কী পাবে গুটি কয়েক স্বর্ণভূষণ আর মুদ্রা!
এক তীব্র দোলাচলের মধ্যে মধুমতীর সময় কাটতে থাকে। সে অষ্টাদশ বর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী। জীবনের এই ঊন্মেষ পর্বে বহু দীপ্তমান, শৌর্যমান, বীর্যবান রাজপুরুষ তার শয্যায় ক্রীড়া করেছে। কিন্তু মুনিকুমারের তেজোদীপ্ত পৌরুষ স্পর্শে যেভাবে মথিত হয়েছে তার অন্তরের অনুভূতিসমূহ, তা আগে কখনও হয়নি। একবার ভাবে ঋষিকুমার তার। আবার পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় সে রাজার অনুমোদিত ও প্রেরিত গণিকামাত্র। তার ক্লেদাক্ত জীবনের অবসান মৃত্যুতে। তার তো কোনো ধর্ম থাকতে নেই, ব্যক্তিগত সখ-আহ্লাদ থাকতে নেই, সংসার থাকতে নেই, এমনকি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভালোবাসাও থাকতে নেই—সে বহুভোগ্যা ও বিনোদনের সামগ্রীমাত্র।
৬
শেষরাতে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করে মুনিবর বিভাণ্ডক ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে নিদ্রাভিভূত হলেন। কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়। নিত্যদিনের মতো প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃকালীন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জপ-স্তব সমাধা করেন। তারপর অভ্যাসবশত ফলমূল আহরণের জন্য আশ্রমের বাইরে গমন করলেন। ঠিক এই সুযোগে মধুমতী আগের দিনের মতো সুগন্ধিত দেহে স্বচ্ছবসনে লীলায়িত ছন্দে মুনিকুমারের সামনে উপস্থিত হল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে প্রত্যক্ষ করে আপ্লুত হয়ে সবলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বললেন, ‘তপোধন, এই তিনদিবস আপনার অদর্শন আমাকে ব্যাথিত করেছে। যদিও পিতা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন। আপনার আগমন পিতার মনঃপূত নয়। কিন্তু আপনার দর্শন স্পর্শ আমাকে অপার আনন্দদান করে। এখানে পিতা ভিন্ন অন্য কোনো মনুষ্যের মুখ আমি কদাপি দর্শন করিনি। আপনি একমাত্র সুহৃদ যিনি আমাকে এত আনন্দ দিয়েছেন। চলুন আপনার আশ্রমে যাই। আপনার ব্রতচর্চা দেখে আসি। পিতার প্রত্যাগমনের পূর্বেই আমাকে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’
মধুমতীর অন্তর প্রদীপ্ত শিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে মুনিকুমারকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে তুলল। মধুমতীর প্রশ্রয়ে তার মনোহর সুগন্ধিত নরম স্তনদ্বয় নিয়ে মেতে ওঠেন মুনিকুমার। ক্রমে মধুমতী অনুভব করে ঋষ্যশৃঙ্গের পৌরুষ দীপ্ত হচ্ছে। আবিষ্ট মুনিকুমারকে সে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে তাদের মায়া-আশ্রমের নৌকোয়। নৌকো নোঙর তুলে দেয়। ভেসে চলে অঙ্গরাজ্যের অভিমুখে। কৌশিকী নদীর সুশীতল বাতাসে মুনিকুমার শান্তিলাভ করেন। অপার বিস্ময়ে মায়া-আশ্রম নিরীক্ষণ করেন ঋষ্যশৃঙ্গ। মধুমতীর হস্তধারণ করে বলেন, ‘হে তাপস, কী অপূর্ব আপনার আশ্রমস্থান। পুষ্পসৌরভে আমোদিত চারপাশ। মনে হয় আপনার আশ্রমেই বাস করি কিছুকাল।’ শিশুসুলভ চপলতায় মধুমতীর শরীরের সুঘ্রাণ নিতে থাকেন মুনিকুমার। মধুমতী বুঝতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গের আবেশ এখনও দূরীভূত হয়নি। মায়া-আশ্রমের একটি বিশেষ কুটিরে মুনিকুমারের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। সুকোমল শয্যায় গভীর নিদ্রাভিভূত হন মুনিকুমার। তাঁর নিদ্রাভভূত দেহ থেকে উন্মাদনা ক্রমশ দূরীভূত হতে থাকে। মধুমতী নৌকোর খোলা স্থানে এসে বসে।
৭
প্রাতঃকালের রূপময় প্রকৃতি যেন চঞ্চলা তরুণী। কৌশিকী নদীর তরঙ্গমালায় স্বর্ণাভ রৌদ্রকিরণ আপতিত হয়ে আগ্নেয় মেখলার রূপ পরিগ্রহ করেছে। মধুমতী বৈশাখের খর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই দিকে। তার একটাই সান্ত্বনা সে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের মতো বা তাঁদের প্রেরিত অপ্সরাদের মতো কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রতারণা করেনি। মুনিকুমারের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ভঙ্গ করেছে ঠিকই, সেইসঙ্গে গার্হস্থাশ্রমের বাসনাও জাগ্রত করে তুলেছে তাঁর মনে। পূর্বেও এধরনের কাজে খ্যাতনামা অপ্সরাগণও দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেবল প্রভুর আজ্ঞায় স্বার্থের বশেই একাজ করেছেন। মধুমতী ঋষ্যশৃঙ্গকে ভালোবেসেছে। সে তাঁর জন্য নিজের বৃত্তি ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। রাজপুত্রী শান্তার আগে মুনিকুমারকে অধিকার করে নিজের দেহকে ধন্য করে নিয়েছে মধুমতী। এই সৌভাগ্য নিয়েই বাকি জীবন তাকে কাটাতে হবে। এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি নেমে আসে ওর চোখেমুখে। মধুমতীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে।
মাথার ওপর কারোর হাতের স্নেহের পরশ অনুভব করে ঘুরে তাকাতেই দেখে মা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি। মাথাটা মায়ের গায়ে এলিয়ে দেয় সে। কন্যার মনের কথা মাতা পড়তে পারেন। সব মায়েরই এটা সহজাত প্রবৃত্তি। কন্যার কপোলোপরি অবিন্যস্ত কেশদাম সাজিয়ে দিতে দিতে বললেন, ‘জীবন যেমন চলছে তেমনই চলতে দাও মা। সবকিছু সবার জন্য নয়। বৃথা স্বপ্ন দেখে মনের উদ্বেগ বাড়িয়ো না। সংসার আমাদের জন্য নয়। আমরা বিলাসবৈভব ভোগ করতে পারি। হয়তো অর্থের বলে সম্মানও আদায় করতে পারি কিন্তু সামাজিকভাবে সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন আমাদের জন্য নয়।’ মধুমতী সম্মুখের সুবিশাল জলরাশির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক’রে মাতার মতামতকে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায়। মনে ভাবে তারা সত্যিই রাষ্ট্রনীতির সমাজনীতির এবং ক্ষমতা অধিকারের স্বার্থের নির্মম শিকার।
ঋষ্যশৃঙ্গ আর কয়েক প্রহর পর অঙ্গরাজ্যে পৌঁছবেন বেশ্যাকন্যার হাত ধরে। এরপর যা হওয়ার ছিল তা-ই হবে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বস্তিতে নিদ্রা যাবেন। অঙ্গরাজ্য বারিবর্ষণে সজল-শ্যামল হবে। তৃষ্ণার্ত জীবকূল অঞ্জলি ভরে জল পান করবে। রাজা লোমপাদ মধুমতীর গৃহ এবং অঙ্গ ভরিয়ে দেবেন বিপুল ঐশ্বর্যে। রাজ্যজুড়ে মদ্য ও বারাঙ্গনাদের স্রোত বইবে। রাজ্যে উৎসবের রেশ চলবে পক্ষকালব্যাপী। এসব ছাপিয়েও যা হবে তা হল রাজপ্রাসাদ সেজে উঠবে আলোকমালায় রাজকন্যা শান্তা আর ঋষ্যশৃঙ্গের মহামিলন শুভবিবাহ উপলক্ষে। মুনিবর মহাত্মা বিভাণ্ডকও প্রসন্নচিত্তে মেনে নেবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান উৎপাদন করবেন। এইরকমই স্থির আছে, অন্তত ভারত কাব্যে তা-ই বলা আছে। কিন্তু কাব্যে যা অনুক্ত অথচ শাশ্বত তা মধুমতীর একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ এই সংবাদ কোনোদিনই পাবেন না— মহাকাব্যে মধুমতীরা চিরদিনই নামহীন, গোত্রহীন, সংসারহীন, সামাজিক অধিকার বর্জিত নর্মসহচরীমাত্র।
...(সমাপ্ত)...
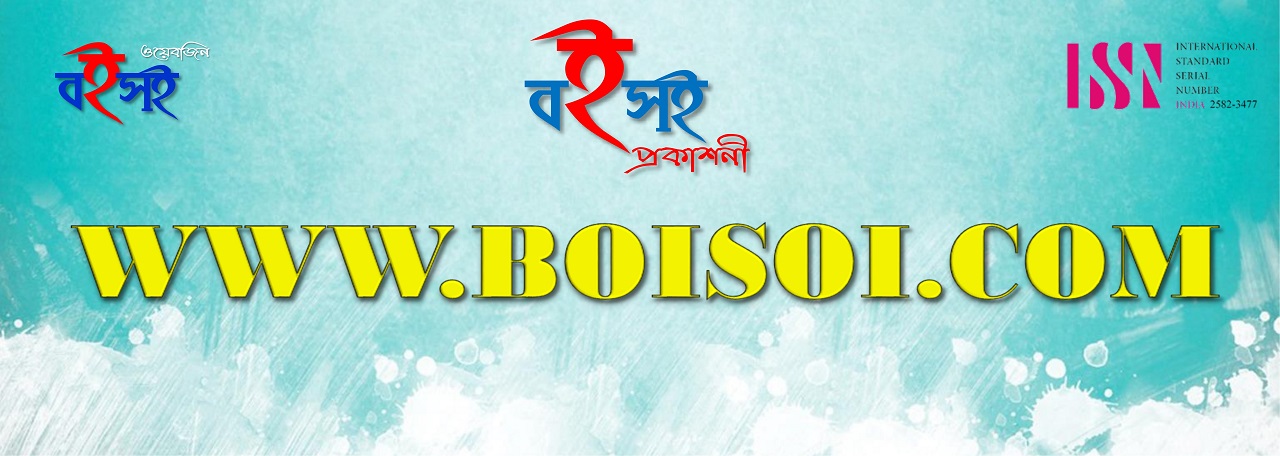







No comments:
Post a Comment