 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেপে ওঠে বন্ধ এ ঘর
ঊর্বী দ ত্ত
শৈশবটাকে
ফিরে পাওয়ার ধান্দায় মাঝে মাঝেই আমি অনেক পাগলামো করি। আমার ঘরের একটা কোনায়
প্রচুর পুতুল আছে। ওগুলোর দিকে তাকালেই আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়। বয়সটা কমে
না তো, তাই নিজেকে অনেকটা বেমানান লাগে। যখন স্কুলে যাই, দরজাগুলো রঙিন কাগজ দিয়ে
সাজানো, আমার ভারী চমৎকার লাগে। মনে হয় সত্যিকারে যদি জীবনটা এত রঙিন হতো, এসবের
কোন প্রয়োজনই পড়তো না।
জন্মানোর
পর থেকেই বোধহয় মানুষের জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়। তা না হলে ওইটুকুনি শিশুদের
জন্যও এত বাড়াবাড়ি করবার কি কোন দরকার পড়তো? নাকি মনুষ্যত্ব মাত্রই একঘেয়েমি।
সকালে দাঁতে মাজন ঘষা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সবটাই নিয়মমাফিক।
অনেকটা কবিগুরুর তাসের দেশের মতো।
আচ্ছা,এই
নিয়মমাফিক একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই কি বিনোদন। নাকি বিনোদন
চালিয়েদেরও একঘেয়ে লাগার অধিকার আছে?
তাই
কি মাঝে মাঝে ছবি ঘরে গিয়েও অভিনয়টাকে অভিনয় মনে হয়?
জীবন
বৈচিত্রপূর্ণ হতে পারে, মনুষ্যত্ব নয়। মানুষ হওয়ার দায় থাকে যে। জীবজন্তুদের তো
আর মানুষ হওয়ার দায়টা থাকে না। সমাজের মনবাঞ্ছা পূর্ণ না হলে প্রশ্নের
মুখেও পড়তে হয় না।
এইসবই
কি আমার নিছক পাগলামি নাকি সত্যিই জীবনকে চিনেছি? কে জানে!
একটা
বয়সের পর নিজের চেতনার রঙে পান্না সবুজ আর চুনি রাঙ্গা হয়ে ওঠে না। ঠিক সেই
মুহূর্তেই দরকার পড়ে 'এক্সট্রিনসিক মোটিভেসন' এর।
দৈনন্দিন
ও গতানুগতিক ধারাবাহিকতা জীবনকে করে তোলে একঘেয়ে।
কিন্তু
মানব জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে এই একঘেয়েমীর কাছে হার মানবে কেন,ধরা দেবে কেন?
কিন্তু
যতই সে বার বার মনকে প্রমোদে টইটম্বুর করে রাখার চেষ্টা করে ততই মন বাধ সাধে,বলে
"আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে"।
ঠিক
সেই সময় গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে "আমরা অদ্ভুত,আমরা চঞ্চল,আমরা নূতন যৌবনেরই
দূত", "আমরা ঠেকবো না তো কোন শেষে,ফুরোয় না পথ কোন দেশে" আর হঠাৎ
যেন বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাই সাড়া,লাগে চমক।
এই
চমকটা বুকে লাগাবার জন্যই কাউকে শুনতে হয় রবীন্দ্র সংগীত, কারোর লাগে নেটফ্লিক্স
আর কফি, কারোর বা লাগে কাফকার 'মেটামরফোসিস'।
এই
মেটামরফোসিসের জন্য মানুষ এক জীবন অপেক্ষা করতে পারে।
মেটামরফোসিস ঘটে, কিন্তু আড়ালে থাকে, সহজে দেখা
দেয় না। সেটাকে খুঁজে বার করাটাই তো
জীবন।
তাই
হঠাৎ প্রাণ গেয়ে ওঠে
"আজ
নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে"।
লাতিন
আমেরিকান লেখক জর্জ লুই বোর্হেস তাঁর একটি ছোট গল্প 'বোরহেস্ অ্যান্ড আই' তে
শিল্পী এবং সত্তার কথা বলেছেন।
তিনি
বলেন যে শিল্পী বোরহেস্ এবং সত্তা বোরহেসের মধ্যে তিনি এক পার্থক্য খুঁজে পান।
সেটা
কি শুধুমাত্র সৃষ্টির দায়ে?
এক্ষেত্রে
অবশ্য শিল্পী এবং স্রষ্টা একই ব্যক্তি।
কিন্তু
যে অর্থে শিল্পও সৃষ্টির কথা বলে, সে অর্থে কি স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করা
হয়?
ইম্পোজিশন্
না ইমপ্রোভাইসেশন্ - শিল্পে কোনটার প্রাধান্য বেশি?
এখানে
রোলা বার্থ এর 'ডেথ অফ দি অথর' বিষয়টিও প্রাধান্য পায়।
অর্থাৎ সংগীত রচনা এবং সংগীত পরিবেশন, দুটির দায় কি স্রষ্টার উপরেই বর্তায়?
সৃষ্টির
ক্ষেত্রে কি স্রষ্টা দাবি করতে পারেন যে,"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে
করেছি রচনা"?
সে
ক্ষেত্রে বোধহয় সব শিল্পীকেই তাহলে স্রষ্টা হতে হতো।
কিন্তু
তা বলে কি নিজের সৃষ্টি এভাবে বিকিয়ে দেওয়া যায়?
"আর
আছে? আর নেই! দিয়েছি ভরে।"
এখানেই
বাণিজ্যের প্রসঙ্গটা আসছে।
একজন
শিল্পী হিসেবে আমি স্রষ্টার সৃষ্টিকে নকল করব না ইমপ্রোভাইস করব,সেটা কি আমার
সিদ্ধান্ত?
দর্শক
বা শ্রোতারও কি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে?
স্রষ্টা,সৃষ্টি,শিল্প
ও শিল্পী - সমার্থক হওয়া সম্ভব?
...(সমাপ্ত)...
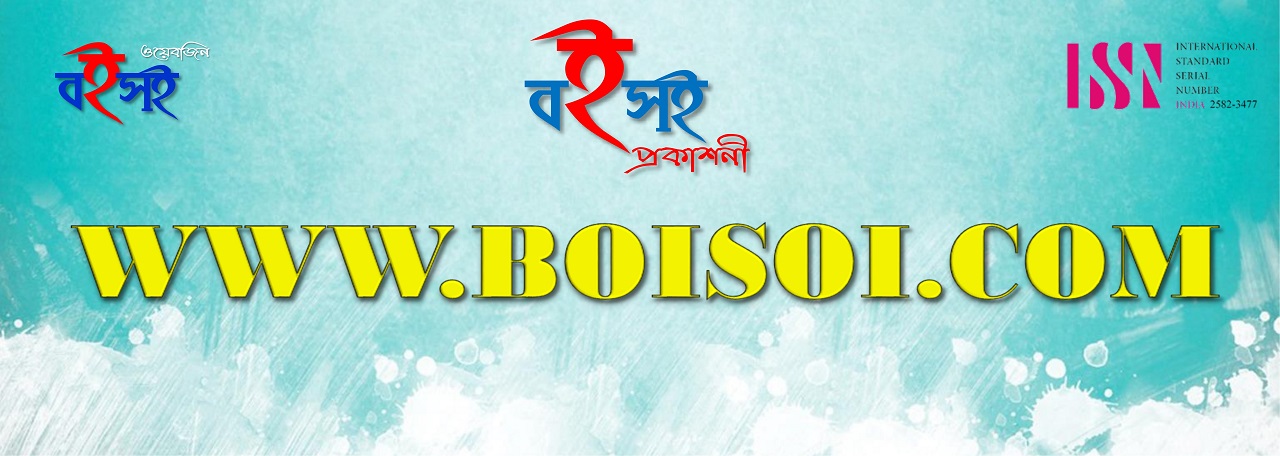








No comments:
Post a Comment