 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
দুর্গাপূজা: এক সাংস্কৃতিক-দার্শনিক পরিভ্রমণ
কৃশানু ব্যানার্জী
দুর্গাপূজা, বাঙালির জীবনে এক অপার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, এক সাংস্কৃতিক পরম্পরার ধারাবাহিক বহিঃপ্রকাশ, যা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ইতিহাস, কাব্য, শিল্প এবং দর্শনের সম্মিলিত অনুরণন। এই পূজা কেবলমাত্র দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে নিহিত আছে নারীশক্তির বিজয়, অসুরবিনাশের প্রতীকী দ্যোতনা এবং মানবচেতনার জাগরণ।
ভারতীয় উপমহাদেশে মাতৃতত্ত্বের ধারণা আদিকাল থেকেই বিদ্যমান। আদ্যাশক্তি, মহামায়া, যোগমায়া—এই সমস্ত নামেই দেবীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুর্গা যেন এই ত্রিবিধ রূপের সম্মিলনে এক সর্বময় মহাশক্তির প্রতিরূপ, যিনি সৃষ্টিকে রক্ষা, পালন ও ধ্বংসের মাধ্যমে সাম্য ও ভারসাম্য রক্ষা করেন। দুর্গাপূজার আচার, বেদমন্ত্র ও পুরাণকথার মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর দার্শনিক তাৎপর্য।
পুরাণ অনুযায়ী, মহিষাসুর নামক এক অসুর দীর্ঘ তপস্যার মাধ্যমে প্রায় অমরত্বের বরলাভ করেছিল, যার পরিণামে সে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ অধিকার করে নেয়। তখন সমস্ত দেবতার সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্টি হয় দেবী দুর্গা, যিনি দশ হাতে অস্ত্রধারণ করে অসুরদের বিনাশ করেন। এই কাহিনির ভিতরে লুকিয়ে আছে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য—অহংকার, কামনা ও মায়ার অসুররূপী রূপ যখন চেতনার স্বর্গরাজ্য অধিকার করে, তখন আত্মার শক্তিই সেই অন্ধকারকে পরাভূত করে।
দুর্গাপূজার প্রধান অনুষঙ্গ হল 'অশুভের বিনাশ' ও 'শুভের প্রতিষ্ঠা'। এই ধারণা শুধুমাত্র পৌরাণিক নয়, বরং মানবজীবনের অন্তরসত্যের প্রতীক। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই বাস করে অসুররূপী প্রবৃত্তি, যা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যরূপে আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দুর্গাপূজা সেই অন্তরাত্মার যুদ্ধেরই প্রতীক, যেখানে চৈতন্য ও শক্তি মিলিত হয়ে অজ্ঞতার পর্দা ছিন্ন করে।
ঋগ্বেদ, উপনিষদ এবং তন্ত্রসাহিত্যে ‘শক্তি’ ধারণাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ‘দেবীসূক্ত’ বর্ণনা করে দেবীকে সর্বভূতের চেতনাত্মা হিসেবে। এই ভাবনা থেকেই দুর্গাকে কেবল মূর্তি বা রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি সর্বত্র, সর্বদা, সর্বাবস্থায় বিরাজমান। এই দার্শনিক উপলব্ধি দুর্গাপূজার রূপকার্যে যেমন প্রতিফলিত, তেমনি তাতে নিহিত আছে অদ্বৈত বোধের ছায়া।
বাঙালি সংস্কৃতিতে দুর্গাপূজার স্থান শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নয়; এটি এক সামগ্রিক সামাজিক সংস্কৃতির উৎসব। গ্রাম থেকে শহর, দরিদ্র থেকে বিত্তবান, হিন্দু থেকে অন্য সম্প্রদায়—সবাই এই পূজার আনন্দে মিলিত হন। এই মিলনবোধই দুর্গাপূজাকে এক সার্বজনীন উৎসবে রূপ দিয়েছে, যা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়সের সীমারেখা ছিন্ন করে মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে।
দুর্গাপূজার সবচেয়ে দার্শনিক দিক হচ্ছে ‘অস্থায়িত্বের মধ্যে স্থায়িত্বের সন্ধান’। চার দিনের এই উৎসবের রূপজগৎ যেন এক নাট্যমঞ্চ, যেখানে আনন্দ, শোক, উত্তরণ ও বিচ্ছেদ—সব অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটে। দেবী আসেন, থাকেন, এবং আবার ফিরে যান—এই আগমন-প্রস্থান যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে সমস্ত সম্পর্ক, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষণস্থায়ী অথচ গভীর।
পূজার রীতিনীতি—চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মহাস্নান, অঞ্জলি, কুমারীপূজা, সন্ধিপূজা ইত্যাদি—প্রতিটি আচারবিধির মধ্যেই এক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা কাজ করে। চক্ষুদান শুধু মূর্তির নয়, বরং দর্শকেরও চেতনায় আলোর সঞ্চার। কুমারীপূজা নারীশক্তির প্রতি সমাজের সম্মান, এবং সন্ধিপূজা, অন্ধকার ও আলোর সন্ধিক্ষণে আত্মসমর্পণের অভিজ্ঞতা।
দুর্গাপূজা একদিকে যেমন তন্ত্রসাধনার মূল আধার, তেমনি বৈদিক ও পৌরাণিক দর্শনের সমন্বিত রূপ। তন্ত্রে দেবীকে ‘শক্তি’ হিসেবে পূজিত করা হয়—যিনি জ্ঞান, কর্ম, ইচ্ছার উৎস। আবার উপনিষদে বলা হয়, ‘যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা’। অর্থাৎ দুর্গা কেবল যুদ্ধরতা দেবী নন, তিনিই মানববুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, মননের উৎস।
শিল্প ও সাহিত্যে দুর্গার চিত্রায়ণ বহুবিধ। অষ্টভুজা দেবীর রূপ যেমন চিত্রকলায় এসেছে, তেমনি তার অসুরবিনাশী শক্তির রূপ এসেছে কবিতায়—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখ কবিদের রচনায় দুর্গা এক প্রতীকী চরিত্র, যিনি বাঙালির চেতনার অভ্যন্তরে বিদ্যমান।
আধুনিক সমাজে দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় বা আচারিক নয়, এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। থিমপ্যান্ডেল, সমাজসেবা, নারী-সমাজের জাগরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার—সবই দুর্গাপূজাকে এক বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। তবে এই আধুনিকীকরণের মধ্যেও দর্শনের গভীরতা যেন হারিয়ে না যায়, সেটাই আজকের মূল চ্যালেঞ্জ।
দুর্গাপূজার একটি গভীর দর্শন হলো চক্রবৎ পরিবর্তনের বোধ। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষ পর্যন্ত এই উৎসবের সময়কাল ঋতু-পরিবর্তনের সংকেত দেয়। ঠিক যেমন প্রকৃতিতে আলো ও অন্ধকারের চক্র চলে, তেমনি মানুষের মনেও চলমান থাকে শক্তি ও ক্লান্তির দ্বন্দ্ব। পূজার মাধ্যমে সেই ক্লান্ত আত্মা পুনরায় শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়।
দর্শন বলে, 'অসতোমা সদগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়'—এই চেতনা দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত প্রেরণা। দেবী দুর্গা যেন সেই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রার পথপ্রদর্শক। তিনি কেবল একজন দেবী নন, বরং এক আত্মিক পথের দিশারী।
দুর্গাপূজার সময় যে সমবেততা দেখা যায়—বিশেষত শিল্পীদের, পুরোহিতদের, প্যান্ডেল নির্মাতাদের, শিশু-কিশোরদের ও সাধারণ মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ—তা মানবসমাজের এক গভীর আন্তঃসম্পর্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অন্তর্মিলনই দুর্গাকে করে তোলে ‘সার্বজনীন’।
প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে নিহিত আছে দর্শনের আরেকটি দিক—‘মাটি থেকে মাটি’। আমরা সবাই ধূলিকণা, আবার ধূলিতে বিলীন হব। দেবীর প্রতিমা যখন জলে মেশে, তখন আত্মজিজ্ঞাসার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়—এই ধ্বংস মধ্যেই নিহিত সৃষ্টির বীজ।
দুর্গাপূজা ও নারীতত্ত্ব একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দেবী কেবল মাতৃত্বের প্রতীক নন, তিনি সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রেম, জ্ঞান ও করুণার সমন্বিত রূপ। এই দর্শন নারীকে কেবল ভক্তির নয়, বরং সম্মানের আসনে স্থাপন করে।
সাম্প্রতিক সময়ে দুর্গাপূজার বানিজ্যিকীকরণ, রাজনীতি ও প্রতিযোগিতা পূজার প্রকৃত দর্শনের ওপর ছায়া ফেলছে। কিন্তু তবু, এই পূজার অন্তঃস্থলে যে আত্মিক আগুন জ্বলছে, তা নিভে যায়নি। প্রতিটি ঢাকের আওয়াজে, অঞ্জলির প্রণতিতে, ও বিসর্জনের কান্নায় সেই অন্তর্জাগতিক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়।
শেষ
কথা, দুর্গাপূজা একটি রূপক—যেখানে চিরন্তন শক্তি ও মানবিক দুর্বলতা, অন্ধকার ও আলো,
দুঃখ ও আনন্দ একত্রে মিলে যায়। এই মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের গভীরতর সত্য—‘শক্তিই
জীবনের মূল, প্রেমই তার চালিকা, এবং জ্ঞানই তার গন্তব্য’।
...(সমাপ্ত)...
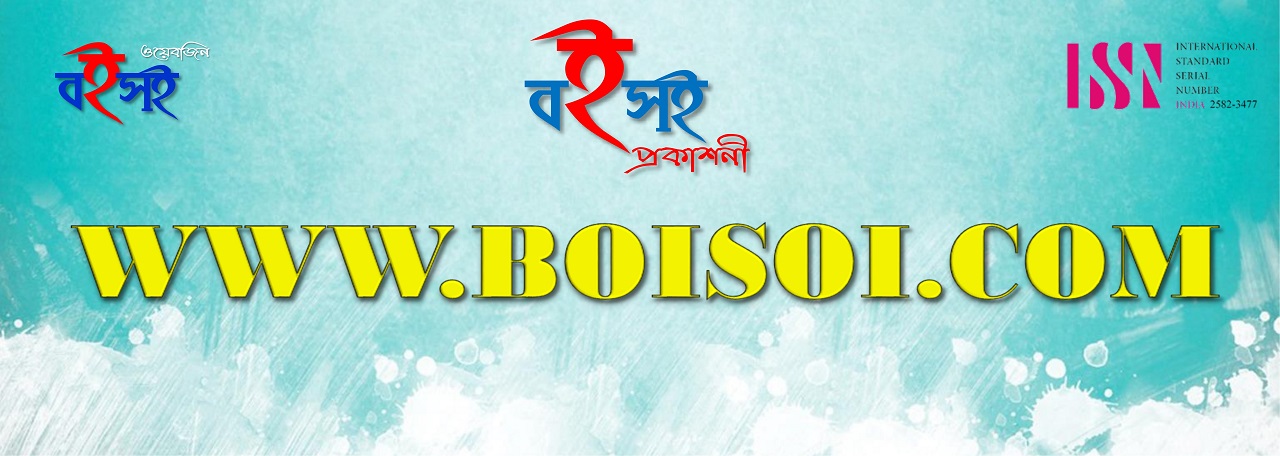








No comments:
Post a Comment