 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
সভ্যতার শুরু থেকে অনার্য লোকেরা তাদের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাসনা
করত। তারা বিশ্বাস করতো যে মানবের পাপ দেবতাকে রাগান্বিত
করে। তাই তাদের তুষ্ট করার জন্য অনাহূত ক্ষতির সম্ভাবনার থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেবদেবীর
পূজো, আচার, ব্রত ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছে। ব্রত পালন এই জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বলেছেন, ‘কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে
চলে তাকেই বলা হয় ব্রত’। তিনি ব্রত গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন-১)
শাস্ত্রীয় ব্রত, যা হিন্দু ধর্মের সংগে
এদেশে প্রচার পেয়েছে, আর ২) মেয়েলী ব্রত, যার অনুষ্ঠানগুলিকে পুরাণের আদিপর্ব বলে
মনে হলেও এর মধ্যে হিন্দু-পূর্ব ও হিন্দু
ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতার কোন চিহ্ন
তার মধ্যে অমিল।
ঠিক এমনই সর্বাধিক প্রচলিত নারীদের একটি ব্রতের নাম ষষ্ঠী ব্রত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি পুরাণ মতে ষষ্ঠী পূজো বারো ধরণের ছিল। যদিও কালের সঙ্গে বেশীর ভাগেরই
স্বাতন্ত্রতা হারিয়ে গিয়েছে। গ্রাম বাংলায় রয়ে গেছে ছয়টি ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান। সেগুলি হলো- অরণ্য, লোটন, গেতু, শীতল, অশোক ও নীল।
তবে এদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৬ তারিখে অরণ্য ষষ্ঠীর প্রচলন সবচেয়ে বেশী। এই
অরণ্য ষষ্ঠীর আর এক নাম জামাই-ষষ্ঠী। আম এই পূজোর প্রধান
উপকরণ বলে বাংলার অনেক স্থানে এর আরেক নাম আমষষ্ঠী, বিশেষত পূর্ব-বাংলার পাবনা ও
বগুরা জেলায়।
কুসংস্কারচ্ছন্ন বাংলার প্রাচীন সমাজে শিশুমৃত্যুর হার থেকে
রক্ষা পেতে অজ্ঞ এবং অসহায় সমাজ যে সব দেবতাদের শরণাপন্ন হয়েছিল, ষষ্ঠী তাদেরই
অন্যতম। অনেকযুগ ধরেই শিশু জন্মের পরে প্রসুতি গৃহে ষষ্ঠ দিনে এই
দেবীর পূজোর প্রচলন হয়ে আসছে। এরপর
সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও সুখের জন্য প্রতি বছরে নারীরা এর
উপাসনা করে। ষষ্ঠী শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাংলাতে 'ষষ্ঠ', এই কারণেই ষষ্ঠী-ব্রত মাসের ষষ্ঠ দিনে
পালন করা হয়। বাংলা ছাড়াও ভারতের
উড়িষ্যা সহ উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই একই রীতি অনুসরণ করা হয়। বিহারে, ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠানটিকে
ছঠী (ষষ্ঠ) বলা হয় এবং ষষ্ঠীকে
‘ছঠী মাতা’।
এই দেবীর পূজো কতটা প্রাচীন বা ঠিক কোন সময় থেকে এর প্রচলন, তা অজানা এখনও। কারণ, প্রাচীন কোন হিন্দুধর্মগ্রন্থে বা বেদ-এ ষষ্ঠীর কোন
নামোল্লেখ নেই। যদিও পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত বায়ু পুরাণে ৪৯ টি দেবদেবীর তালিকায়
ষষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মনে করা হয়, মনসা ও মঙ্গল চন্ডীর মতো এই দেবীকেও
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পুরাণে স্থান দেওয়া হয়েছে। ষোলশ শতকে বৃন্দাবন
দাসের চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে চৈতন্যের জন্মের ষষ্ঠ দিনে দেবী ষষ্ঠীর পূজোর
কথা। যদিও তার অনেক আগে থেকেই বাংলায় এই
পূজোর প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ দেবী-ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। দেবি-ভাগবতে ষষ্ঠীকে বলা হয়েছে দেবী-কাত্যায়নী
(দুর্গার আর এক নাম)। আবার, আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক, আর্নেস্ট ম্যাকে প্রাক-ঐতিহাসিক হরপ্পার খনকার্যের থেকে কিছু পোড়ামাটির এক দেবীর মূর্তি দেখে জানান যে, এর উৎসের
বিষয়টি সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্যের থেকে এসেছে। অন্যদিকে, বাংলায় সবচেয়ে প্রাচীন লোকসাহিত্য ষষ্ঠীমঙ্গল হলো
ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রচলিত বিখ্যাত গ্রন্থ, যা সতের শতকের শেষার্ধে লেখা হয়।
কিন্তু এখন
প্রশ্ন হচ্ছে জামাইদের সঙ্গে এই আচারের কি সম্পর্ক? বাংলার লোক ঐতিহ্যে, দেবী ষষ্ঠীকে নারীদের
উর্বরতার দেবী হিসাবে দেখা হয়। হিন্দু
শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বা গ্রাম বাংলায় এখনো আছে, যে
কন্যার বিয়ের পর যতক্ষন না পর্যন্ত সন্তান হচ্ছে, কন্যার বাবা-মা তার
বাড়িতে পরিদর্শন বা অন্ন গ্রহণ করবে না।
দক্ষিণ এশিয়ায়, তাই আজও অনেক যুবতী স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার
জন্য এবং সর্বোপরি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তীব্র পারিবারিক চাপের
মুখোমুখি হন। ঋকবেদে বলা আছে, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও পুত্রসন্তান জন্মের উদ্দেশ্যে একজন পুরুষকে সক্ষম করে তোলা। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের লেখকরাও একই ধারণা পোষণ করতো। তাই বন্ধ্যাত্বকে কেবল ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, ধার্মিক হিন্দুরা মনে করেন যে পুত্রহীন
স্বামীদের মৃত্যুর পরে স্বর্গে স্থান পাবার সুযোগ খুবই সামান্য। এমনকি পূর্ব-পুরুষদের পিন্ড দানের অধিকারও দেওয়া আছে পুত্রদের। মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনও পুণ্যবান ব্যক্তি কোনও পুত্রহীন ব্যক্তিকে দেখতে পান তবে তার বহুজন্মের
অর্জিত পুণ্য আর কার্যকর হবে না। তাই, এই উর্বরতা সমীকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
হিসেবে মা-ষষ্ঠীর ঐশ্বরিক আর্শিবাদের পরিবেষ্টনের
আওতায় আনা হয় জামাইদের। এইজন্যে
অরণ্য-ষষ্ঠীর আর এক নাম 'জামাই-ষষ্ঠী'। এই
দিনে বাঙ্গালি শাশুড়িরা তাদের কন্যা ও জামাইকে আমন্ত্রণ জানায়। জামাইকে ছয়টি
ফলযুক্ত একটি প্লেট এবং হাতে হলুদ সুতো বেঁধে পাখার হাওয়া দেয়। তারপর, বিভিন্ন
স্বাদের রান্না করে জামাইকে আদর যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ন করে। শাশুড়ির
মনে আশা থাকে যে তাঁর মেয়ের বংশের মাধ্যমে মাতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
যদিও, এই নিয়ে নানা
বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সমাজতত্ববিদদের মধ্যে। অনেক গবেষক বলেছেন, কেন হিন্দুমহিলারা বিনাপ্রশ্নে এখনও শত শত নারী বিরোধী অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে, লীলা দুবে, একজন
নৃতত্ববিদ, একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতিগুলির প্রভাবে নারীরা
আরো বেশী মাত্রায় তাদের স্বামী এবং অন্যান্য
পিতৃস্থানীয় আত্মীয়দের অধীনস্থ হয়। বলা যায়, ব্রত পালনের
মাধ্যমে নারীরা একজন আদর্শ বধূর তকমা অর্জন করে, যা সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত। আবার সুসান ওয়াডলি বলেন, মনস্তাত্ত্বিক অনুভব নারীদের এই আচারগুলিতে
অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী করে। একই যুক্তি জেমস
ফ্রিম্যানও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের
আনুষ্ঠানিক আচারে অংশগ্রহন তাদের একটি মানসিক আরাম এনে দেয়। অনেকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের
সুযোগ হিসাবেও বিবেচনা করে, যা আগের জন্মের কর্ম দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। শৈশবকাল থেকেই নারীদের
প্ররোচিত করা হয় এই ধরণের রীতিতে অভ্যস্ত হতে এবং বিবাহের পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি
নিতে ।তাদের প্রশিক্ষণের একটি আকর্ষণীয় অংশ হল ব্রতগুলি পর্যবেক্ষণ করা, যা ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্য দ্বারা নির্ধারিত দেশীয় বিন্যাস হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে।
অ্যানি
ম্যাকেনজি পিয়ারসন অবশ্য ১৯৯৬ সালে অন্যরকম যুক্তি দেখান। তিনি বলেন, ব্রত রীতি অনুশীলনের মাধ্যমে মহিলারা ক্ষমতায়িত হতে পারেন, যার জেরে স্ব-নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন
করে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাঁর লিখিত
গ্রন্থ ‘গিভস মি পিস অফ মাইন্ড’-এ বলেছেন, এর ফলে নারীদের
মনের প্রশান্তির সুশৃঙ্খল প্রসার ঘটে,
যা বর্ণনায় 'সৌভাগ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সমাজতত্ববিদরা অরণ্যষষ্ঠীর আচার অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন, এটি মানব উর্বরতার রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘জামাই-ষষ্ঠী’ নামটি তাদের এই সিদ্ধান্তকে
সমর্থন করে। আধুনিকীকরণ এবং দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, ব্রত একটি লিঙ্গভিত্তিক
অনুষ্ঠান হিসেবে ভীষনভাবে প্রচলিত, কারণ পুরুষতান্তিক পারিবারিক সমাজে এই ধরণের নারীবাদী ভূমিকা
এখনও প্রত্যাশিত এবং প্রশংসিত। সুতরাং, সবশেষে
বলা যেতে পারে, এই ব্রতপালন মাতৃত্বের ধর্মের থেকেও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বর্তমানেও বেশী
গ্রহনযোগ্য।
২. আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রতকথা
৩. James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajput State Of India.
৪. Leela Dube, On the Construction of Gender: Hindu Girls in Patrilineal India.
৫. Susan Wadley, Brothers, Husbands and Sometimes Sons: Kinsmen in North Indian Ritual. Eastern Anthropologist.
৬. শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত

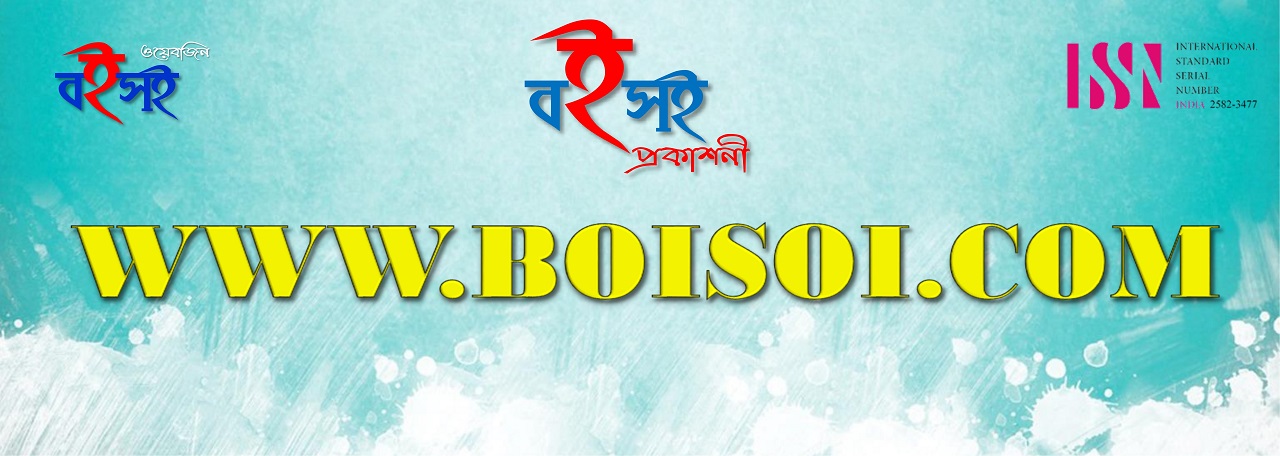






No comments:
Post a Comment