 |
| ছবি : ইন্টারনেট |
ড: সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণান ও বর্তমান দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা
অভিজিৎ দত্ত
ড:সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণান (১৮৮৮-১৯৭৫) ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, দার্শনিক, মানবপ্রেমিক এবং বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক।তিনি দীর্ঘ পনের বছর ধরে, উপরাষ্ট্রপতি (১৯৫২-১৯৬২) এবং রাষ্ট্রপতি (১৯৬২-১৯৬৭)পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে দায়িত্ব পেয়েছেন তাইই নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন।
রাধাকৃষ্ণানের জন্ম তামিলনাড়ুর ছোট্ট শহর তিরুতানিতে।পিতা সর্বেপল্লী বীরস্বামী ছিলেন একজন সামান্য তহশীলদার।মাতা সীতাম্মা।জন্মসূত্রে রাধাকৃষ্ণান ছিলেন নিন্মবিত্ত এক তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না বললেই চলে কিন্ত বংশ পরম্পরায় এই পরিবারের সকলেই ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। মানুষের সেবা করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যার প্রভাব পড়েছিল বালক রাধাকৃষ্ণানের উপর। ছোটবেলা থেকেই রাধাকৃষ্ণান ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। সবসময় বই এর মধ্যেই ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন।তিরুতানি শহরেই তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়।এরপরের শিক্ষা লুথেরান মিশন হাইস্কুলে।১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণান প্রবেশ করেন ভেলোর কলেজে।১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সাল পড়াশোনা করেন মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে।।১৯০৮ সালে ভর্তি হন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।এখানেই তিনি দর্শনে এম,এ ডিগ্রি লাভ করেন। এখান থেকেই তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ পায়-'Ethics of the vedanta and its metaphysical Analysis.এই প্রবন্ধটি পড়েছিল হক সাহেব মুগ্ধ হন ও ভবিষ্যতবাণী করেন রাধাকৃষ্ণান ভবিষ্যতে একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হবে।১৯০৯ সালে রাধাকৃষ্ণান খুব কম বয়সে(একুশ বছর) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন।অল্প দিনের মধ্যেই একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে সকলের নিকট পরিচিত হন।এরপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে যোগ দেন। এখানেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের মন জয় করেছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজের আহ্বানে সেখানে অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন তার একাধিক বক্তৃতার সংকলন নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়-My search of truth. ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণানকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে মনোনীত করা হয়।উপাচার্য থাকাকালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথ ও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও সেখানে বক্তৃতা দেন।১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোর চেয়ারম্যান হন।১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণান রাশিয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি (১৯৫২-১৯৬২)হিসাবে দশ বছর দায়িত্ব সামলান।পরর্বতীতে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি (১৯৬২-১৯৬৭) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। রাধাকৃষ্ণান তার কর্মদক্ষতার জন্য অনেক পুরস্কার পান।তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিখ্যাত হল The Religion we need,kolki or The Future of civilization, Religion and society, Religion in a changing world philosophy of Rabindranath Tagore, প্রভৃতি।১৯৫২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি-লিট।১৯৫৪ সালে ভারতরত্ন।১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক টেম্পলটন পুরস্কার লাভ করেন।উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান১৯৬০ সালের১৪ই সেপ্টেম্বরএকদিনেরজন্যমুর্শিদাবাদ জেলারবহরমপুরেএসেছিলেন কৃষ্ণনাথকলেজের পদার্বিদ্যার গবেষণাগারের নতুন ভবনের উদ্বোধন করতে।।এই অনুষ্ঠানে এসে তিনি এই শহরের দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম উল্লেখ করেন ও তাঁর অর্থ সংকটের সময় দাতার অর্থ সাহায্যের কথা বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন (৫ই সেপ্টেম্বর) কীভাবে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল? এই সম্পর্কে যেটা জানা যায় তা হল রাধাকৃষ্ণান রাষ্ট্রপতি (১৯৬২) হওয়ার পর ছাত্ররা তার জন্মদিন পালন করতে গেলে তিনি বলেন শিক্ষকরাই যেহেতু সমাজের মেরুদন্ড তাই তার জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করলে তিনি খুশি হবেন। এইভাবে সেই বছর থেকে শিক্ষক দিবস পালন শুরু হল।রাধাকৃষ্ণান সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন ও নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তিনি তার একমাত্র পুত্র সর্বেপল্লী গোপালকে লিখেছিলেন গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস ও জীবে করুণা এই দুটি ব্যাপার সবসময় লক্ষ্য রেখে চলো।আমিও ঐ নীতি মেনে চলি।এই মহান ব্যক্তিত্বের মহাপ্রয়াণ হয় ১৯৭৫ সালের ১৬ই এপ্রিল।
রাধাকৃষ্ণান ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, বিখ্যাত দার্শনিক ,যোগ্য প্রশাসক ও একজন মানবপ্রেমী ব্যক্তি।রাধাকৃষ্ণান যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা হলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও রাজযোগ তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমনটি করেছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও song offerings বই দুটি।রাধাকৃষ্ণানের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রতিষ্টা,যার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি এবং প্রথম অধিবেশনে সভাপতিহয়য়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথঠাকুর।রাধাকৃষ্ণান ছিলেন মুক্ত মনা ও স্বাধীন চিন্তার সমর্থক। তাই অন্যায় দেখলেই গর্জে উঠেছেন, কোন কিছুর পরোয়া করেন নি।বিবেকানন্দ প্রকৃত ধর্ম বলতে মানবসেবা বুঝিয়েছেন যেটা রাধাকৃষ্ণান হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তো তিনি যখন রাষ্ট্রপতি হন তার মাইনে ছিল দশ হাজার টাকা।তিনি দুহাজার টাকা নিজের খরচের জন্য রেখে বাকী আট হাজার টাকা দেশের কাজে ব্যয় করতেন। আজকের ভোগ সর্বস্ব যুগে এটা কেউ ভাবতে পারবে?মানুষ অমরত্ব অর্জন করে তার সৃষ্টি ও কীর্তির মধ্য দিয়ে।রাধাকৃষ্ণান সেই অর্থে একজন যুগনায়ক আবার একজন মনীষী, যিনি আজীবন মানুষের উন্নতি সাধন ও কল্যাণের জন্য যেমন বহু বই রচনা করেছেন, দেশ-বিদেশে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন আবার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাধাকৃষ্ণানের এইসকল কাজের উৎস ছিল মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম। রাধাকৃষ্ণানের মতে ধর্ম হল কতকগুলো আচার ও অনুষ্ঠান পালন নয়।ধর্ম আসলে অন্তরের উদ্বোধন। মানুষ সাধারণত বর্হিমুখি।অন্তরের দিকে দৃষ্টি নাই। ধর্মের মূল কথা অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করা।-যে অন্তরে বাস করেন আমাদের অন্তর্যামী তাকে জাগানো।শিক্ষক হিসাবে তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি জানতেন এইগুলি ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।শিক্ষাক্ষেত্রেও তার অসামান্য অবদান।তিনিই প্রথম স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে কমিশন (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণান কমিশন-১৯৪৮)গঠন করা হয় তা তার নেতৃত্বে সুন্দর কাজ করে এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতির জন্য নানা সুপারিশ প্রদান করে।তিনিই প্রথম ভারতীয় দর্শনকে চিত্তাকর্ষক ভাবে প্রকাশ করেন। ভারতীয় দর্শন যে পাশ্চাত্য দর্শন থেকে অনেক উন্নত তা তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।ধর্মের মূল কথা যে মানব কল্যাণ তা তার রচনাবলী পড়লেই বোঝা যায়।তিনি এমন এক মঙ্গলময় পৃথিবীর কথা চিন্তা করেছিলেন যার মূলে থাকবে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবতাবোধ।তিনি জানতেন মানুষের আত্মজ্ঞান ও চেতনাবোধের উন্মেষ ছাড়া কিছুতেই সুন্দর দেশ বা পৃথিবী গড়া সম্ভব নয়।আজকের ভোগবাদী, আত্মসর্বস্ব মানুষ রাধাকৃষ্ণানের কর্ম ও বাণীকে কবে উপলদ্ধি করবে?সুন্দর দেশ ও পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন কী সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে?না কী সত্য, শিব,সুন্দরের আর্দশে মানুষ আবার জেগে উঠবে? সময় সবকিছুর উত্তর দেবে।
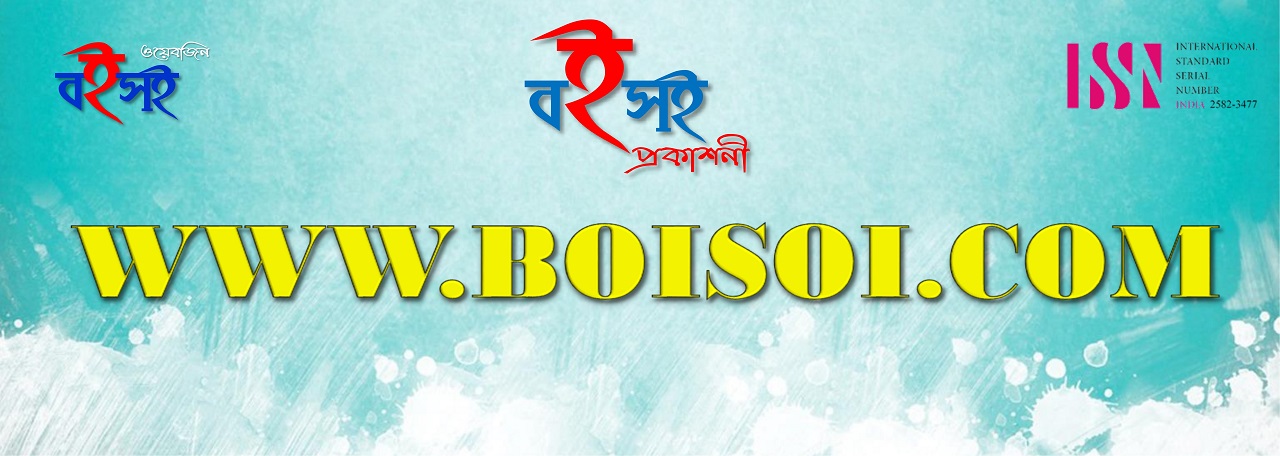







No comments:
Post a Comment